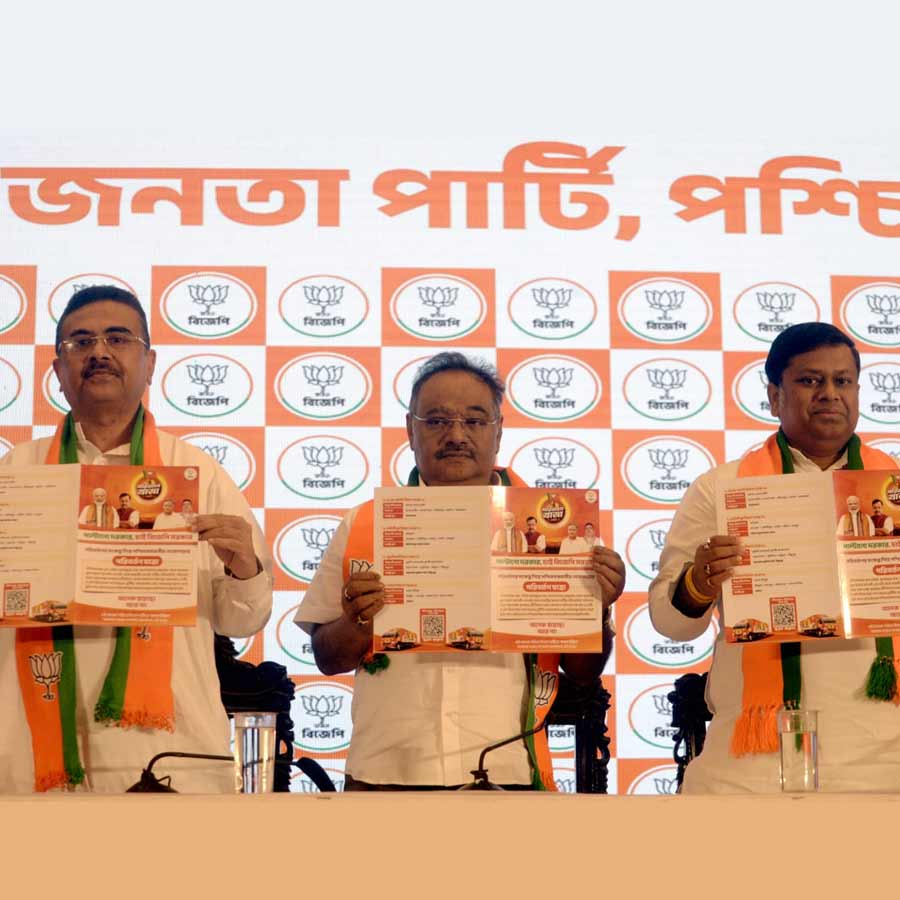পরিবেশের ইতিহাসের আলোচনায় শুধু মানুষের জীবন-মৃত্যুর আন্তঃসম্পর্কে পরিবেশের ঐতিহাসিক অভিঘাত নিয়েই আলোচনা থাকে তা নয়, বরং সমাজ ও জীবজগৎ উভয়েরই পারস্পরিক সম্পর্ক কী ভাবে গড়ে ওঠে চার পাশের প্রাকৃতিক ও জৈবিক জগতের সঙ্গে, এটি তারও আখ্যান। ১৯৬০-এর দশকে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ভাবনাচিন্তার যে ঢেউ ওঠে, তারই প্রেক্ষাপটে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে এই শাখাটির উৎপত্তি। ভারতে কৃষি ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে জঙ্গল এলাকা ও জঙ্গল-নিবাসীদের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসে রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিল পরিবেশের ইতিহাসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন ১৯৮০-র দশকে।
গুহ ও গ্যাডগিল দাবি করলেন, উপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রধানত পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। নানা আইনকানুনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কারণে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। গুহ লিখলেন, ব্রিটিশরা বিজ্ঞানসম্মত বন সংরক্ষণ নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করেছিল। এটি ছিল একেবারেই বাণিজ্যিক। রাজস্ব বাড়ানোই ছিল এর লক্ষ্য। গুহ উপনিবেশিক জ্ঞানকে দেখেছেন অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে ওঠা এক নির্মিতি। কিন্তু গ্রোভ উপনিবেশিক জ্ঞান ও স্বদেশজাত জ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট অমিল খুঁজে পেলেন না। এই দুই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কথা বললেন। গুহের ব্যাখ্যানের সূত্র ধরে বসন্ত সাবেরওয়াল, মোনিতি চক্রবর্তী কউল, মহেশ রঙ্গরাজন, নন্দিনী সুন্দর, শিবরামকৃষ্ণন লিখলেন ব্রিটিশ আমলের জঙ্গলের ইতিহাস। সাংস্কৃতিক ও প্রকৃতির বিচিত্র জগৎ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নানা বৈচিত্রপূর্ণ পরিসর উঠে এল এ সব গবেষণায়।
সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও কৃষক প্রতিরোধের ‘ন্যারেটিভ’ প্রথম দিকের চর্চায় গুরুত্ব পেলেও, পরবর্তী কালে সমাজবিদ্যার ‘ডিসকোর্স অ্যানালিসিস’ গুরুত্ব পায়। মার্ক্স ও গ্রামশি থেকে সরে এসে ফুকোর প্রভাব শক্তিশালী হয়। বিনয় গিদওয়ানি কৃষি ও পরিবেশের ইতিহাসের ভেদাভেদ দূর করে এই দুই ইতিহাসকে এক জায়গায় নিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে কল্যাণকৃষ্ণ শিবরামকৃষ্ণন, গুনেল সেডেরফ, নীলাদ্রি ভট্টাচার্য প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। নদীবাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে ১৯৮০-র দশকে শুরু হয় সামাজিক আন্দোলন। অমিতা বাওয়িস্কর, ডেভিড গিলমার্টিন ও রোহন ডি’সুজ়ার গবেষণায় জল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জল ও জঙ্গলকে নিয়ে সমসাময়িক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা এগিয়ে চলে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। মহেশ রঙ্গরাজন, দিব্যভানু সিংহ, মাইকেল লুইস, রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ বন্যপ্রাণীকে নিয়ে এলেন পরিবেশবিদ্যা-চর্চার বিষয় হিসেবে। এই ভাবে ধারণা ও পদ্ধতিগত দিক থেকে পরিবেশের ইতিহাস অন্যান্য বিষয়, যেমন সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছে এক অনন্য মিশ্রণ।
রঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত এই গ্রন্থটি পদ্ধতিগত দিকটির আলোচনা করে সেই লক্ষ্যেই অভিনিবেশ করেছে। আর চেষ্টা করা হয়েছে জলবায়ুর ইতিহাস ও পরিবেশবাদের সীমারেখা উন্মোচনের। তাঁর প্রাক্কথন ও ভূমিকায় লিখেছেন পরিবেশের ইতিহাসে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল কথা গভীর ভাবে সংযুক্ত, যা সাম্প্রতিক কালের উত্তর-আধুনিকতাবাদের নানা জটিলতা থেকেও মুক্ত। এই ইতিহাস প্রথম দিকের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত, আর রাজনৈতিক আলোচনাও এখানে তুলনামূলক ভাবে কম।
প্রবন্ধগুলোকে ‘হিস্টোরিয়োগ্রাফি অব এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি’; ‘এনভায়রনমেন্টালিজ়ম অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়্যারনেস’; ‘নেচার, ওয়াইল্ডলাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুড’ আর ‘এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দ্য সায়েন্সেস’— এই চার ভাগে সাজিয়ে উপস্থাপনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রিচার্ড গ্রোভ ও বিনীতা দামোদরন একটি সচেতন জ্ঞানান্বেষণের উৎস হিসেবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও প্রশাসকের লেখাপত্রে এর অস্তিত্ব খুঁজে পান। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সম্পদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিচিত পরিবেশেরও প্রভূত ক্ষতি করেছে। আর্নল্ড টয়েনবির তত্ত্বের সমালোচনা করে ব্রদেল ভূমধ্যসাগরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখিয়েছেন, মানুষের আচরণ ও ইতিহাসকে জলবায়ু কতটা প্রভাবিত করে। ১৯৫০-এর দশকে বিভিন্ন দেশে এই চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা নতুন ভাবে চর্চা হতে থাকে। গ্রোভ ও দামোদরন বিশ্ব পরিবেশের ইতিহাসের উৎস ও বিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েক শতাব্দী জুড়ে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ভাবনাচিন্তা ও ধারণার বিবর্তন বোঝার চেষ্টা করেছেন।
ডাজ় এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি ম্যাটার?: শিকার, সাবসিসস্টেন্স, সাস্টেনেন্স অ্যান্ড সায়েন্সেস
সম্পা: রঞ্জন চক্রবর্তী
১৪৯৫.০০
প্রাইমাস বুকস
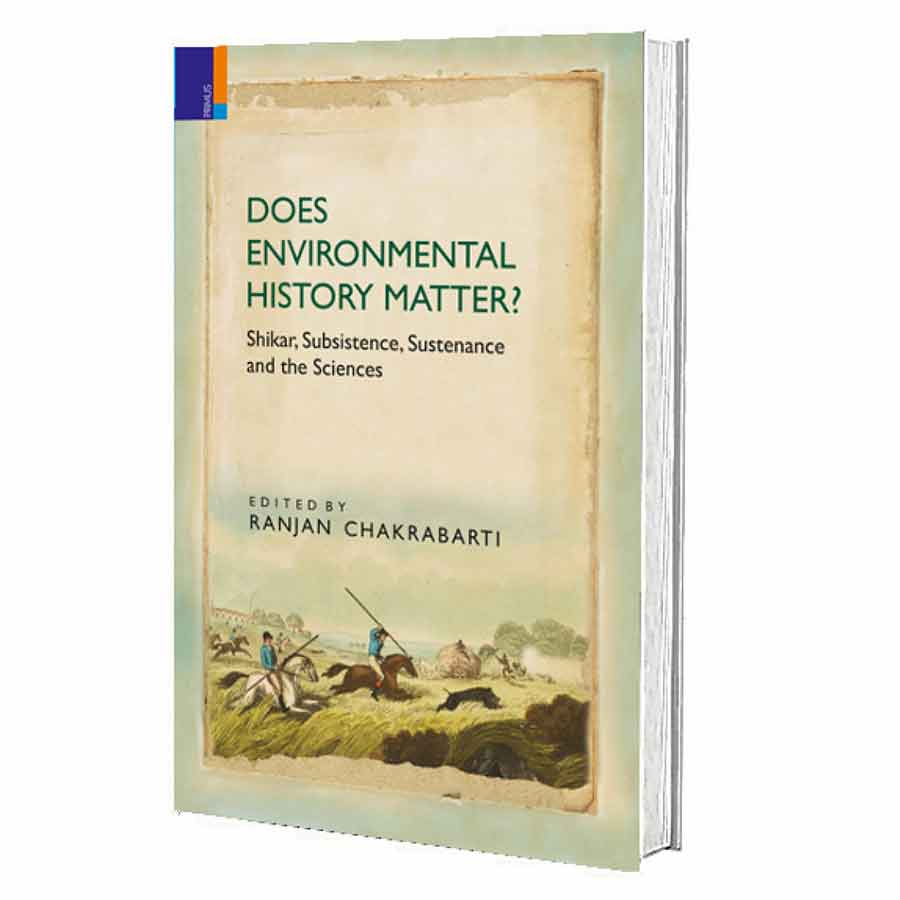

সংস্কৃত সাহিত্যকে ব্যবহার করে সি রাজেন্দ্রন গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের পরিবেশ-সচেতনতার অনুসন্ধান করেছেন। হিস্টোরিক্যাল জিয়োগ্রাফির ভূমিরূপ পরিবর্তনের ধারণাকে ব্যবহার করে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় কলকাতার ভূমিরূপের পরিবর্তনকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে। রঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর চতুর্থ অধ্যায়ে উপনিবেশিক শাসকদের পশুশিকারের আখ্যান লিখতে গিয়ে দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক জ্ঞান নির্মিত হয়েছিল দেশীয় জ্ঞানের সঙ্গে আপস ও কথোপকথনের মাধ্যমে। পঞ্চম অধ্যায়ে কৌশিক চক্রবর্তী ভারতের, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে, ব্রিটিশ ও স্বাধীন ভারতের বন-নীতি জনজাতিগুলির উপরে কী ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতে ও প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে জনজাতিগুলি প্রথাগত জঙ্গলের অধিকার ভোগ করত। শুচিব্রত সেন মৌখিক ইতিহাসের পদ্ধতি ব্যবহার করে জঙ্গল নিধন ও পরিবেশের অবক্ষয়ের ফলে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির কী সমস্যা হচ্ছে আর এ থেকে উত্তরণের পথ কী, আলোচনা করেছেন।
এই ইতিহাস আঞ্চলিক হলেও তাঁর প্রেক্ষিত বৃহত্তর। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের অবক্ষয়ের সমাধান নিয়ে উদ্বিগ্ন বৈজ্ঞানিক মহল এই জটিল বিষয়কে শুধু বিজ্ঞানের মূল শাখার মধ্যে সমাধান করতে পারছেন না। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, এমনকি সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গেও শুরু হল কথোপকথন। এই কথোপকথন থেকেই আন্তঃবিষয়ক চর্চা জোরালো হল, আর জন্ম হল ‘আর্থ সিস্টেম সায়েন্স’ শাখার। সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, এই শাখাটির উন্মেষ ভারতে কী ভাবে হয়েছিল। ভূমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল এবং জীবজগতের মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক নিয়ে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। জলবায়ু-ইতিহাসে তাই এই গ্রহজাগতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্ব পাচ্ছে।
অষ্টম অধ্যায়ে মিলি ঘোষ আবহাওয়া-বিজ্ঞানী হেনরি পিডিংটনের জলবায়ু-বিজ্ঞান বিষয়ে অবদান, বিশেষত ঘূর্ণিঝড় বিষয়ে তাঁর অসামান্য গবেষণার কথা লিখেছেন। ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আমাদের ধারণা গড়ে তুলতে পিডিংটন অশেষ সাহায্য করেছেন। তিনি লর্ড ডালহৌসিকে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা ক্যানিংয়ে বন্দর নির্মাণ না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করার ফলে বন্দরটি ১৮৬৭ সালে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বর্তমান গ্রন্থটি পরিবেশের ইতিহাসে যে সব বিতর্ক রয়েছে সেগুলোকে স্পষ্ট করেছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন উপস্থাপনা করে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছেন সম্পাদক। জলবায়ুর ইতিহাস ‘গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রি’র অন্যতম অংশ হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রিতে স্থানীয় ও বিশ্ব সমস্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বইটি এই প্রেক্ষাপটেই রচিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাস বিষয়ে ২০০৪ থেকে গবেষণাকর্ম চালিয়েছিল, এই গ্রন্থটি তারই ফসল। আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের জন্য গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য হবে, এই আশা।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)