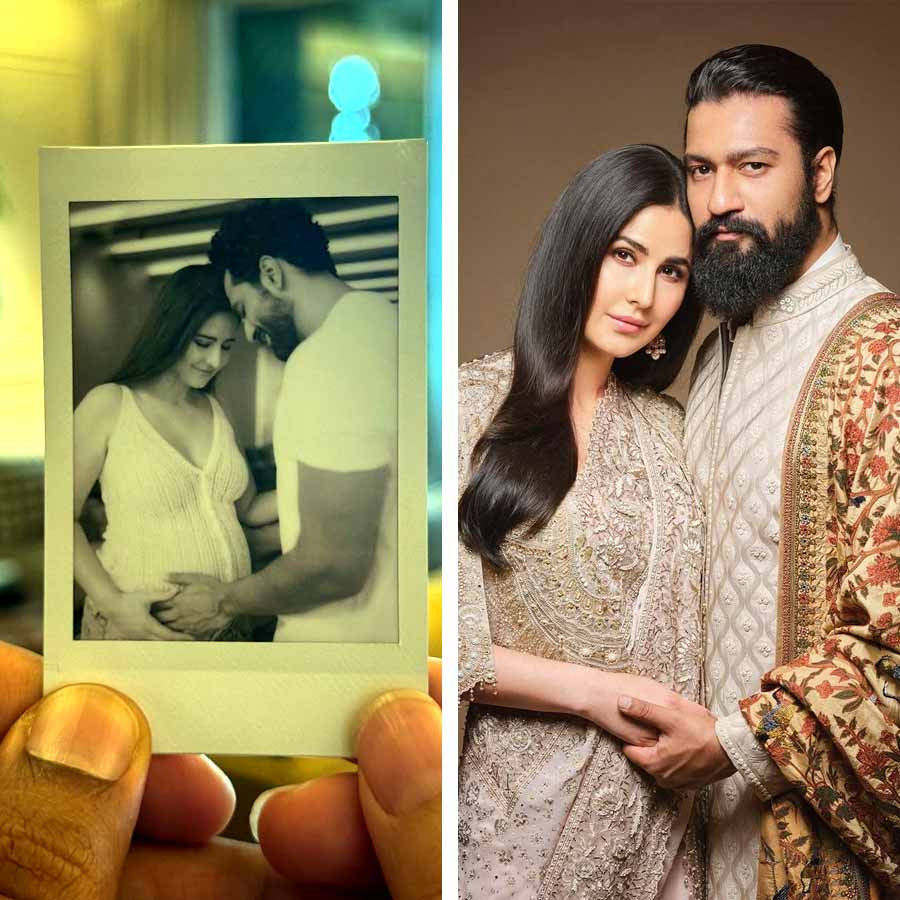ইতিহাস কী ভাবে লেখা উচিত, এ প্রশ্নের উত্তরে জওহরলাল নেহরুর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল। তিনি মনে করতেন, শুধুমাত্র সতীর্থ ইতিহাসবিদদের জন্য ‘তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল’ বিচার নয়, অন্তত কিছু লেখা এমন হওয়া উচিত, যা শ্রমিক কৃষকদের মতো বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে না থাকা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছতে পারে। ভারতীয় ইতিহাসচর্চার অন্তত একটি ধারার মধ্যে এই আদর্শগত অবস্থানটির প্রতিফলন ঘটেছিল। আদিত্য মুখোপাধ্যায় সেই ধারার ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রতিনিধি। তাঁর আলোচ্য বইটি এই গোত্রের ইতিহাসচর্চার উজ্জ্বল উদাহরণ। পেশাদার ইতিহাসবিদদের সম্মেলনে ভাষণ হিসাবে পঠিত হয়েছিল বটে মূল লেখাটি, কিন্তু তার অভিমুখ স্পষ্টতই সাধারণ মানুষের দিকে— জওহরলাল নেহরু, এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাঁর অবদান বিষয়ে যাঁদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়; ওয়টস্যাপ ইউনিভার্সিটির ফরওয়ার্ড যাঁদের মনে নেহরুর একটি বিরূপ ছবি তৈরি করে দিয়েছে, বিশেষত তাঁদের দিকে।
ফলে, বইটির একেবারে প্রথম পাতা থেকে তার দ্বিমুখী উদ্দেশ্য স্পষ্ট— এক, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, এমন ভঙ্গিতে মূলত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরুর বিভিন্ন অবস্থানের কথা বলা; এবং দুই, বারে বারেই দক্ষিণপন্থী অপপ্রচারের অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট করে দেওয়া। ঠিক এই কারণেই বইটির গুরুত্ব। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলটি নেহরুকে ভারতের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। সেই অসহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে নেহরুকে শুধু নেহরুবাদী পণ্ডিতদের চৌহদ্দিতে আটকে রাখা চলে না— তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে।
বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বজায় রেখেও যে লেখাটিকে প্রশস্তি করে না তুলে নির্মোহ ভাবে তাঁকে দেখা যায়, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তা হাতে-কলমে দেখিয়েছেন। এই বইয়ের দীর্ঘতম অধ্যায়টি নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে। ১৯২০-৩০’এর দশকগুলিতে নেহরু সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে দেখেছিলেন ধ্রুপদী মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে— তিনি মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ প্রকৃত সমস্যা নয়; আসল সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক শোষণ। সেই শোষণ থেকে মানুষের নজর সরিয়ে রাখার জন্যই সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সব মানুষের কাছে সেই উন্নতির সুফল পৌঁছলে আপনা থেকেই ধর্মীয় বিবাদের সমস্যা দূর হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরু এই অবস্থানটি থেকে সরে আসেন। বলেন, উন্নয়নের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে আগে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটির সমাধান করা দরকার। এই যে অবস্থানগত পরিবর্তন, আদিত্য মুখোপাধ্যায় সে কথা স্পষ্ট লিখেছেন। কিন্তু, এই পরিবর্তন যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি, বিশেষত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে নেহরুর আন্তরিক দায়বদ্ধতায় কোনও চ্যুতি ঘটায়নি, সে কথাটিও একই রকম স্পষ্ট। তিনি ১৯৪৬-এর বিহার দাঙ্গা থামাতে নেহরুর ভূমিকার কথা লিখেছেন। উল্লেখ করেছেন যে, দেশভাগ-পরবর্তী যন্ত্রণাদীর্ণ সময়ে মুসলমানদের প্রতি কোনও অন্যায় হলে রাষ্ট্র তার পূর্ণশক্তি দিয়ে সেই অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবে। মনে করিয়ে দেওয়া যায়, এই একই সময়ে ‘শত্রু সম্পত্তি’ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রের কাছে শুধু ন্যায্য আচরণই প্রত্যাশিত নয়; ন্যায় যে হচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে যেন তা স্পষ্ট হয়। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে শাসকের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত, নেহরুকে যদি তার মান্য মাপকাঠি ধরা হয়, তবে সেই নিরিখে আজকের শাসকদের এক বার যাচাই করে নেওয়া ভাল।
নেহরু’জ় ইন্ডিয়া: পাস্ট, প্রেজ়েন্ট অ্যান্ড ফিউচার
আদিত্য মুখোপাধ্যায়
৪৯৯.০০
পেঙ্গুইন
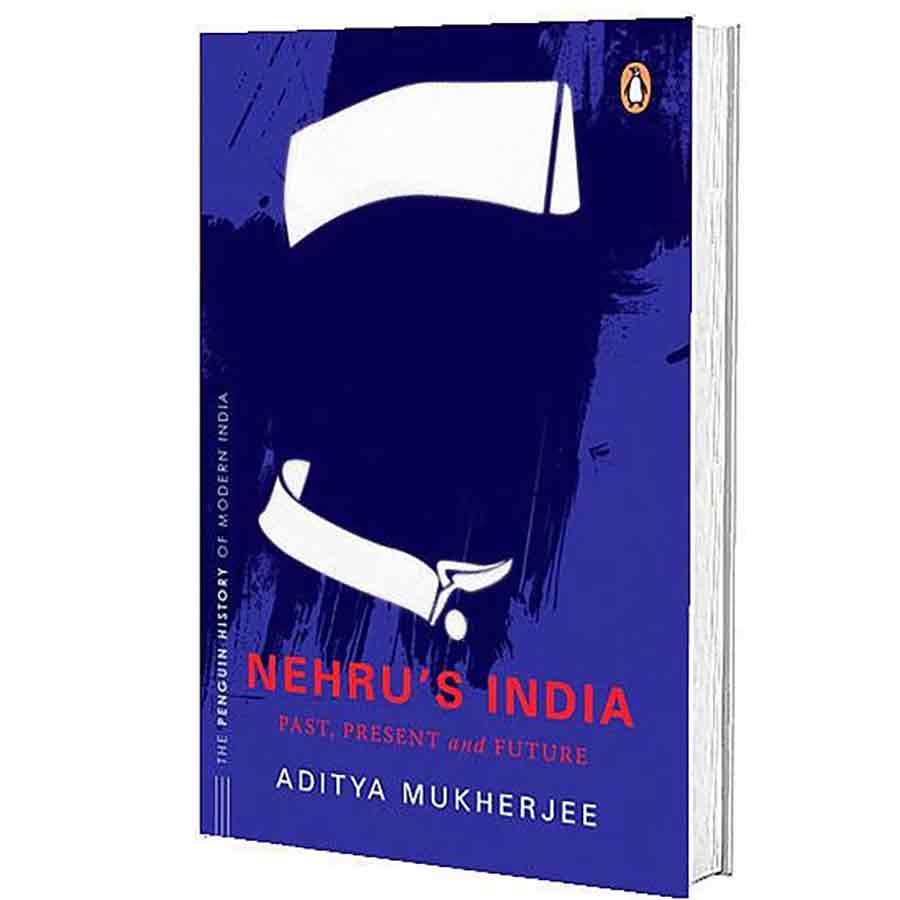
নেহরুর বিশ্বাস ছিল, দ্রুত এবং ব্যাপক শিল্পায়নের পথেই ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্ভব। বিশ শতকের মধ্যভাগে এই বিশ্বাসটি ছিল কার্যত বিশ্বজনীন। ১৯৩০-এর দশক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্যোগ— এই দেড় দশকে ভারতেও যত আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র দু’টি বাদ দিলে বাকি সবেতেই সর্বব্যাপী শিল্পায়নের কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু, কার্যত গোটা দুনিয়া শিল্পায়নের অভিমুখে যে পথে হেঁটেছে, নেহরু সে পথ পরিহার করেছিলেন সচেতন ভাবে। তিনি নিজেকে বেঁধেছিলেন কয়েকটি মৌলিক ধর্মের গণ্ডিতে। গণতন্ত্র ও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি তাঁর অনড় বিশ্বাস যেমন ছিল, তেমনই ছিল গান্ধীর অহিংসার আদর্শ। অন্য দিকে, শিল্পের জন্য মূলধনি পণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরতাও ছিল পরিহার্য। সব সময় সচেতন থাকতে হয়েছিল বণ্টনের ন্যায্যতা বিষয়েও। ফলে, যে দেশের সিংহভাগ মানুষ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন, দু’শো বছরের বিদেশি শাসনের ফলে যে দেশের অর্থব্যবস্থা ছিল বিধ্বস্ত, সে দেশকে শিল্পের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণতন্ত্রের, অহিংসার, ব্যক্তিস্বাধীনতার শর্তগুলিকে শিরোধার্য করে নেহরুকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। নেহরু-চর্চাকারীদের কাছে এ কথাগুলো নতুন নয়— কিন্তু, সাধারণ পাঠকের জন্য এই গোটা ছবিটা ফুটিয়ে তোলার অতি জরুরি কাজটি করেছেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়।
উন্নয়নের কাজটিও যে মানুষের সম্মতি ব্যতীত করা চলে না, এই বোধে উপনীত হওয়া নেহরুর রাজনৈতিক দর্শনের একটি দিকচিহ্ন। একের পর এক জনসভায় তিনি বলে গিয়েছেন উন্নয়নের গুরুত্বের কথা, এবং সেই মহাযজ্ঞে সাধারণ মানুষের যোগদানের তাৎপর্যের কথা। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া একটি দেশে যখন ভাষার ভিত্তিতে খণ্ড জাতীয়তাবাদী প্রবণতাগুলি প্রকট হয়ে উঠছে, তখন নেহরু উন্নয়নকে দেখতে চেয়েছিলেন ভারতীয় জাতির ঐকিক পরিচিতি হিসাবে— কেউ হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-শিখ নয়, কেউ বাঙালি-মরাঠি-তামিলও নয়, প্রত্যেকের প্রথম এবং প্রধানতম পরিচয়, তাঁরা ভারতীয়; ভারতের উন্নয়নে তাঁরা সমান ভাগীদার। ভারত ভবিষ্যতের পথে ধাবিত হবে যেমন উন্নয়নের রথে চড়ে, তেমনই সেই ভারতের পরিচয়ও তৈরি হবে উন্নয়নের পরিচিতিতেই। নেহরুর এই আদর্শবাদ, এই আশাবাদ শেষ অবধি বাস্তবায়িত হতে পারল না কেন, তা ভিন্ন প্রশ্ন— গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই, কিন্তু সেই ব্যর্থতা কোনও ভাবেই নেহরুর দর্শনের মহিমাকে খর্ব করে না।
আদিত্য মুখোপাধ্যায় এই বইয়ে নেহরুর ইতিহাসচেতনার কথা আলোচনা করেছেন একটি পৃথক অধ্যায়ে। এই বিষয়টির যতখানি গুরুত্ব প্রাপ্য, নেহরু-চর্চার পরিসরে তা সেই গুরুত্ব পায়নি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে দু’টি বিশেষ দিক উঠে আসে। প্রথমটি হল, আজকের দক্ষিণপন্থী রাজনীতি যে ভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করে মুসলমানদের শত্রুরূপে প্রতিষ্ঠা করে, নেহরু আগাগোড়া সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইসলামি শাসকের হাতে হিন্দু মন্দির ধ্বংস হলেই যে তাকে মৌলবাদী বৈরর উদাহরণ হিসাবে দেখা চলে না, এই সত্যটি তাঁর ইতিহাসবোধে ধরা পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসকে দেখার বিরোধিতা করার পাশাপাশি তিনি সংশয়ী ছিলেন জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা বিষয়েও। দেশের একটি গৌরবময় অতীতের আখ্যান নির্মাণ করা, এবং সেই সোনার যুগ পুনঃস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি যে শেষ অবধি ফ্যাসিবাদের বিপদকে ডেকে আনতে পারে, তা নিয়ে নেহরুর সংশয় ছিল না। আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়, তিনি ঠিক কোন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন।
নেহরু সন্বন্ধে এই আলোচনা বলে দেয় যে, কেন বিজেপি বিশেষ ভাবে এই মানুষটির কথা ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চায়; কেন নেহরুর ভারত-কল্পনা বিজেপির কাছে অসহনীয়। এবং কেন এই মুহূর্তে আরও বেশি করে নেহরুর কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)