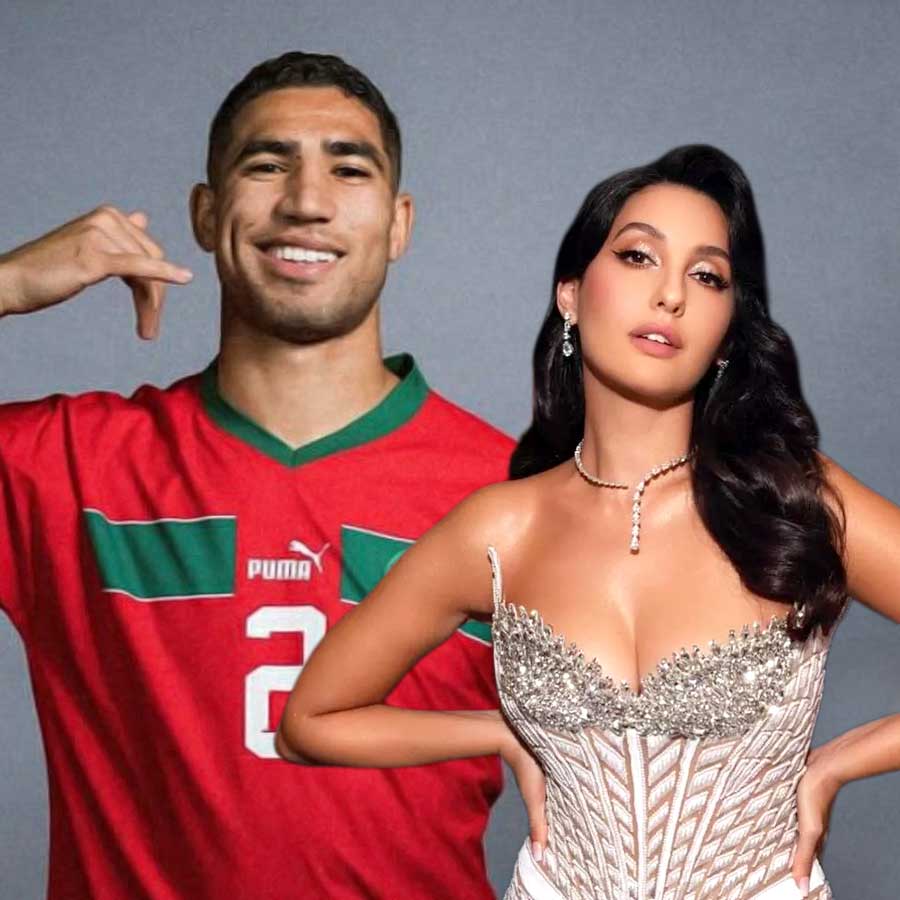এই তো বসেছি কোনও ক্রমে! জানু পেতে বসতে পারিনি, গত এক ঘণ্টা পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে জানু, হাঁটু সবেরই দফা রফা! কিরঘিজস্তানে ওশ শহরের এই পাহাড়টার নাম সুলেমান টু। গোটা পাহাড়টাই ইউনেস্কোর তরফে বিশ্ব-ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃত, বাইবেলের রাজা সলোমন এখানে একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন।
সলোমনের মন্দির আর নেই। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে উঠতে একটা গুহা। ভিতরে সংকীর্ণ, অন্ধকার। তারকেশ্বর মন্দিরে হত্যে দেওয়ার মতো করেই সন্তানহীন মেয়েরা গুহার এই মুখ থেকে ওই মুখে পৌঁছতে পারলে মনস্কামনা পূর্ণ! পুরুষের ধকে গোটাটা কুলোয়নি। শুয়ে, বসে নিজেকে টেনেহিঁচড়ে গুহার অন্য মুখে রোদ্দুরের দেখা পেয়েই কৃতার্থ হয়েছি। গুহার মাঝে দেখলাম এক রমণীকে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে। শুনলাম, ওঁর মেয়ে নিঃসন্তান। তার জন্যই এখানে আসা!
সংস্কার? কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের রাজা সলোমন মানেই তো মাতৃত্বের সেই বিখ্যাত বিচার। সলোমন রাজা হয়েছেন, হিব্রু বাইবেলের ঈশ্বর বা জিহোভা ন্যায়বিচারের জন্য তাঁকে পছন্দ করেন। বিচারসভায় এক দিন এক শিশুকে নিয়ে হাজির দুই নারী। দু’জনেই বলল, তারা শিশুটির মা। সলোমন বললেন, বেশ, বাচ্চাটাকে কেটে আধখানা করে নাও। এক জন বলল, ‘বেশ।’ অন্য জন কেঁদে পড়ল ‘না, ওকে আঘাত করবেন না।’ সলোমন বুঝে গেলেন, কে আসল মা! সেই সলোমনের নামাঙ্কিত পাহাড়ে এ রকম একটি গুহা শুধুই সংস্কার?
গুহা থেকে বেরিয়ে ফের সিঁড়ি, পিচ্ছিল পাথর। নীচে খেলনানগরের মতো ওশ শহর। ‘পাহাড়ে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছিলাম। জায়গাটা চমৎকার, নীচে গোটা শহর দেখা যেত,’ আত্মজীবনীতে লিখেছেন বাবর।
চড়াই শেষে ছোট্ট সাদা ঘর, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। মেঝেতে কার্পেট, পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ করে দেওয়ালজোড়া কুলুঙ্গির মতো মেখরাব, অর্থাৎ আজানের স্থান। ভারতে এখন বাবর ও রামায়ণের রাম একসঙ্গে থাকলেই মুশকিল। অথচ ইহুদি সলোমন ও মুসলমান বাবর আজও বিশ্ব-ঐতিহ্যের এই পাহাড়ে হাত ধরাধরি করে।
সকালবেলায় বেরিয়েছি পাশের দেশ উজবেকিস্তানের ফরঘনা শহর থেকে। বাবরের জন্মভূমিতে আজ সোভিয়েট আমলে তৈরি বড় বড় সব বাড়ি। বেশির ভাগই খাঁ খাঁ, জনশূন্য। গাইড জানালেন, চাকরি নেই, তরুণরা বেশির ভাগই কাজ খুঁজতে মস্কো পাড়ি দিয়েছে।
ফরঘনা পেরিয়ে আন্দিজান। বাবরের আত্মজীবনীতে বারংবার এসেছে এই শহর। প্রাচীরে তিনটে দরজা, ভিতরে ন’টা খাল। এত ভাল তরমুজ আর আঙুর অন্য কোথাও মেলে না। বালক বাবর তখন আন্দিজানে, এক দিন তাঁর বাবা ওমর শেখ মির্জা পায়রা ওড়াতে গিয়ে পাহাড়ের খাদ থেকে বাজপাখি হয়ে উড়ে গেলেন। দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর এই রূপক অন্য কোথাও পাইনি। গাইড বলছিলেন, ‘উজবেক ভাষায় শহরের নাম কিন্তু ফরহোনা। ফর মানে পরি, হোনা মানে মাজার। যে শহরের মাজারে পরিরা নেমে আসে, তারই নাম ফরহোনা।’ এই শহরই তো এক হাতে কাব্যিক রোজনামচা লেখে, অন্য হাতে সাম্রাজ্য তৈরি করে।
আন্দিজান পেরিয়ে কিরঘিজ সীমান্ত, সেখানে ভিসা-পাসপোর্টের এক দফা ধাক্কা সামলে ওশ। বাবর জানতেন না, বিশ শতকের সীমান্ত-রাজনীতি অন্য রকম হবে। তাঁর ফরঘনা, আন্দিজান এক দেশে থাকবে, আর ওশ অন্য দেশে।
সীমান্তে কী আসে যায়? সুন্নি মুসলমান অধ্যুষিত, দুই ভূতপূর্ব-সোভিয়েটে দেশেই জনসংস্কৃতি এক রকম। লাঞ্চ বা ডিনারে চিনামাটির বাটিতে চা আর গ্লাসে ভদকা অবশ্য পানীয়। এক কামড় রুটি খেয়ে একটু চা, দু’তিন গ্রাস পরে নিট ভদকা। হোটেলের মেনিউতে বিফ আর পর্ক পাশাপাশি। বাজারে ঘোড়ার মাংসের সসেজও বিক্রি হচ্ছে। একটু বোটকা গন্ধ, কিন্তু সুস্বাদু। আমাদের গাইড রাইহোনা মেয়েটি বেশ সুন্দরী, সে কথায় কথায় বলেছিল, ‘এটা সিল্ক রুট। বাণিজ্যের কারণে সবাই এসেছে, মেলামেশা করেছে। খাওয়াদাওয়ার বাছবিচার তাই আমাদের নেই।’
রাইহোনা উজবেক, স্বামী তাজিক। শুনলাম, বহুবিবাহ নেই। কোরানের নির্দেশ, পুরুষ চারটি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু সবাইকে সমান চেখে দেখতে হবে, সম্পত্তির সমান ভাগ দিতে হবে। পুরুষরা ওই ঝামেলায় যায় না। সুয়োরানি-দুয়োরানি ভারতেই থাকে।
বিয়ের প্রথম দিন সিভিল ম্যারেজ, পরের দিন কাজিকে ডেকে নিকাহ্ কবুল। সিভিল ম্যারেজ না হয়ে থাকলে কাজি বিয়ে দেবেন না। সেই আইনি অধিকার তাঁর নেই। মাদ্রাসায় ১৬ বছর অবধি সবাইকে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান পড়তে হবে। এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘সোভিয়েট শাসন তোমাদের কী দিয়েছে রাইহোনা? রুটি আর মাংসের লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া?’ ঝকঝকে চোখে হাসল উজবেক মেয়ে, ‘স্বাধীনতা। ধর্মের শিকল থেকে মুক্তির স্বাধীনতা। শিক্ষার স্বাধীনতা। ইচ্ছা হলে জুম্মার নামাজে যাই, নয়তো নয়।’ রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে রেশমপথে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অপ্রত্যাশিত ছিল।
সোভিয়েট শাসন ছিঁড়ে বেরিয়ে-আসা উজবেকিস্তানে তৈমুর লঙ্গ আজ জাতীয় নায়ক। তাসখন্দ, সমরখন্দের প্রতিটি মিউজিয়মে তাঁর বংশলতিকা শেষ হয়েছে ১৮৫৭ সালে ইয়াঙ্গনে নির্বাসিত বাহাদুর শাহ জাফরকে দিয়ে। সমরখন্দে সিল্ক রুটের মিউজিয়মে গাইড দেখিয়েছেন, ‘এটা এখানকার কুষাণ আমলের মৃৎপাত্র।’ কখনও বা ম্যাপ দেখিয়ে বলেছেন, ‘আর্যরা এই পাহাড় বেয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছেছিল।’ রাইহোনা জানাল, ছোটবেলায় তার শাহরুখ খানকে বিয়ে করার খুব ইচ্ছে ছিল। শুনে বাবা বলেছিলেন, ‘দুর! আমরা রাজ কপূরকে চিনতাম।’ আর্য সভ্যতা থেকে কণিষ্ক হয়ে বাবর, বলিউড— তামাম ভারতকে সিল্ক রুট নিজেরই অংশ ভাবে। ভারত থেকে এসেছি জেনে তৈমুর লঙ্গের রাজধানী, মরুশহর সমরখন্দের এক ইমাম বলেছিলেন, ‘প্রার্থনা করি, গঙ্গায় আরও জল থাকুক।’ সেই প্রার্থনায় আমার গঙ্গা স্বচ্ছ হল।
তৈমুর! কয়েক হাজার হিন্দুকে কচুকাটা করে ১৩৯৯ সালে দিল্লিকে শ্মশান বানিয়ে যাওয়া সেই অত্যাচারী। ঠিকই, তবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দেওয়া তখনকার রণকৌশল। তৈমুর দামাস্কাসের মসজিদে আগুন লাগান, ধ্বংস করে দেন আফগানিস্তানের হেরাট শহর। তুরস্কের সুলতান বায়াজিদকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতেই স্পেন ও ইংল্যান্ডের রাজারা পড়িমড়ি তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। কারণ, বায়াজিদ কয়েক বছর আগে ইউরোপের ক্রুসেডারদের কচুকাটা করেছিলেন। শুভেচ্ছার উত্তরে তৈমুর খ্রিস্টান রাজাদের লিখছেন, ‘আপনারা আমার পুত্রের মতো, নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করুন।’
এক বিকেলে গিয়েছিলাম বিবিখানুম মসজিদ। মসজিদের কাজ শুরু করেছিলেন তৈমুরের প্রধান স্ত্রী মালিক উল খানুম। তিনি চেঙ্গিজ খানের বংশের মেয়ে, তাঁকে বিয়ে করার পরই তৈমুর ‘গুরখান’ উপাধি পান। গুরখান মানে, চেঙ্গিজের উত্তরপুরুষ। আবুল ফজল ‘আকবরনামা’য় তাঁর পৃষ্ঠপোষককে এক বারও মুঘল লিখছেন না। বলছেন, ‘গুরখানিদ বংশের উত্তরসূরি।’
বিবি খানুম মসজিদের কাজ শুরু করেছিলেন, ভারত থেকে ফিরে শেষ করলেন তৈমুর। মাথায় নীল গম্বুজ। এই গম্বুজ-স্থাপত্য পরে শোভা পাবে তাজমহলে। মসজিদে ঢোকার আগে গেট পেরিয়ে বিশাল প্রাঙ্গণ, চিনার গাছের বাগিচা। জাহাঙ্গিরের আমলে তৈরি শালিমারবাগ, নিশাতবাগ, সবই এই তৈমুরীয় স্থাপত্যের উত্তরাধিকার।
উল্টো দিকে বিবিখানুমের সমাধি। পড়ন্ত বেলার আলো, কেয়ারটেকার জানালেন, ‘আসল সমাধিটা দেখাতে পারি। ওয়ান ডলার।’
সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভের অন্ধকার। কেয়ারটেকার ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘বিবিখানুমের মুখ কিন্তু পশ্চিমে মক্কার দিকে নয়। উনি চেঙ্গিজের বংশধর। বৌদ্ধ ছিলেন।’ স্থানীয় উপকথা? কিন্তু ইতিহাসও বলে, এই এলাকায় চেঙ্গিজের উত্তরসূরিরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তৈমুরের প্রধান স্ত্রী বৌদ্ধ! জোধা-আকবরের ঢের আগে এই মরুভূমির আকাশেও উড়েছে ভিন ধর্মের প্রেম?
এই পিতৃভূমিকে না জানলে ভারত আমার কাছে অচেনা রয়ে যেত।