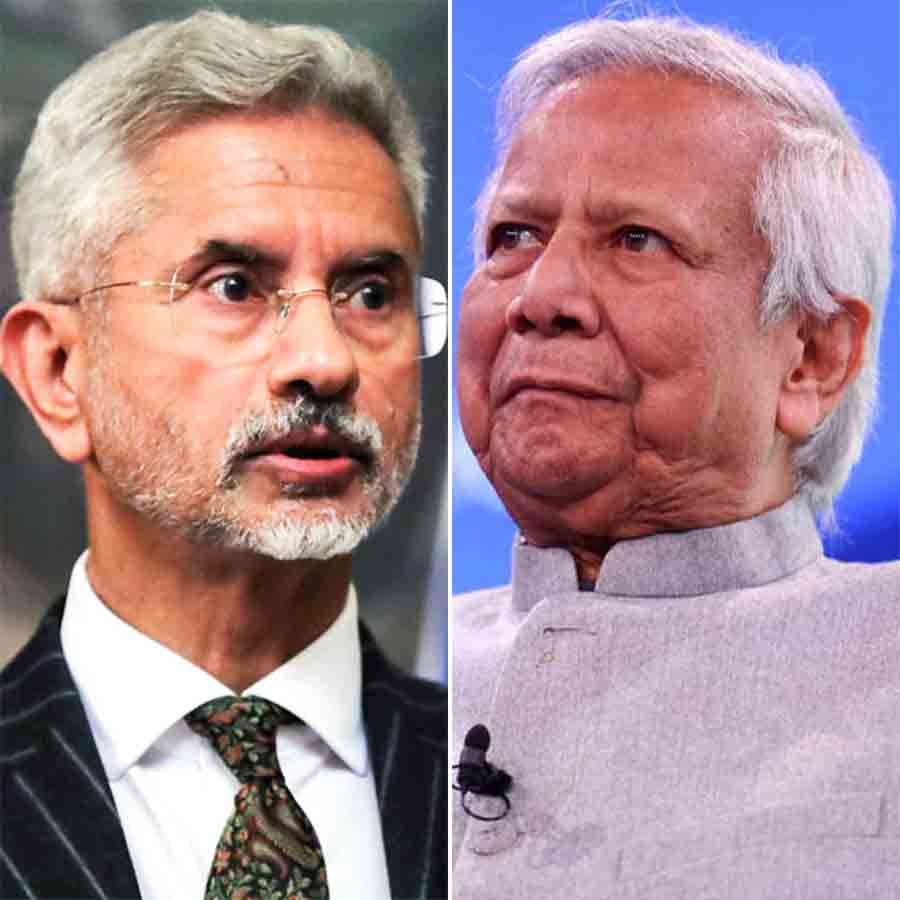বাজেট-ভাষণের প্রথমেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর লক্ষ্যগুলি জানিয়ে দিলেন— আর্থিক বৃদ্ধির হার দ্রুততর করা, সর্বজনীন উন্নয়নের পথে হাঁটা, বেসরকারি লগ্নিকে উৎসাহ দেওয়া, গৃহস্থালির মনোবল বৃদ্ধি এবং ভারতের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। জানালেন, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে দারিদ্র নেমে আসবে শূন্যের স্তরে, সবার জন্য উচ্চমানের স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থা হবে, সবার জন্য সুলভে উচ্চমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকবে, দেশের শ্রমশক্তির ১০০ শতাংশই প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হবে এবং তাঁদের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, মহিলাদের ৭০% শ্রমশক্তিতে যোগ দেবেন, এবং কৃষকরা ভারতকে বিশ্বের খাদ্যভান্ডার করে তুলবেন। চমৎকার সব প্রতিশ্রুতি— তবে, যোগে মিলছে কি না, দেখে নেওয়া প্রয়োজন।
মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে অভূতপূর্ব কর ছাড় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, মধ্যবিত্ত কাকে বলে? সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আট কোটির কাছাকাছি মানুষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছিলেন— তাঁদের মধ্যে চার কোটির সামান্য বেশি লোকের আয় ছিল বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি, অর্থাৎ যাঁরা এই নতুন কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরও ২.৩৫ কোটি লোক উল্লিখিত অর্থবর্ষে আয়কর দিয়েছেন, কিন্তু এখনও রিটার্ন দাখিল করেননি। যদি ধরে নিই যে, তাঁদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি, তবুও দেশের মাত্র ৬.৪৫ কোটি লোকের আয় বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হবে। ২০২৩-২৪’এর পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস)-র তথ্য অনুসারে, ভারতে মোট কর্মীর সংখ্যা ৬০ কোটি। অর্থাৎ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ১০.৭৫% বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি উপার্জন করেন। অতএব, অর্থমন্ত্রী যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলছেন, তাঁরা কোনও মতেই মধ্যবিত্ত নন, বরং আয়ের নিরিখে দেশের শীর্ষ ১০% পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আলোচনার খাতিরে তবুও তাঁদের ‘মধ্যবিত্ত’ বলেই ডাকা যাক।
ভারতে এক জন মানুষ গড়ে কত টাকা আয় করেন? বাজেটের আগের দিন প্রকাশিত ২০২৪-২৫ সালের আর্থিক সমীক্ষা পিএলএফএস-এর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিসাব করে জানিয়েছে, দেশে এক জন স্বনিযুক্ত ব্যক্তি মাসে আয় করেন গড়ে ১৩,২৭৯ টাকা; নিয়মিত বেতনের চাকরিজীবীর গড় আয় মাসে ২০,৭০২ টাকা; এবং ঠিকা শ্রমিকের মাসিক গড় আয় ১২,৭৫০ টাকা। পিএলএফএস পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমাদের অনুমান, দেশের শ্রমশক্তির মাত্র ২৫% মাসে ১৫,০০০ টাকার বেশি আয় করেন; এবং নীচের দিকের ২৫% মানুষের মাসিক গড় আয় ৩,০০০ টাকার কম, অর্থাৎ দৈনিক আয় একশো টাকার কম। আরও দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলের ৪৬% এবং শহরাঞ্চলের ২৪% পুরুষ-শ্রমিকের দৈনিক উপার্জন ৩০০ টাকার কম। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে গ্রামের ৯১% এবং শহরের ৬৪% মহিলা-শ্রমিকের মাসিক আয় ছিল ৯,০০০ টাকার কম।
দেশের যে ৭০-৭৫% পরিবারের মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার কম, সরকারি সাহায্যের তাদের খুব প্রয়োজন— বিনামূল্যে ভাল মানের শিক্ষা; নিখরচায় চিকিৎসা; খাদ্যে ভর্তুকির জন্য মজবুত গণবণ্টন ব্যবস্থা, গ্রাম এবং শহর, উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম নিশ্চিত মজুরিতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা; লিঙ্গবৈষম্য হ্রাসের জন্য জেন্ডার বাজেটিং-এর মতো বিভিন্ন গোত্রের সাহায্য। পেট্রলিয়াম-সহ বিভিন্ন পণ্যে পরোক্ষ করের হার কমালে দেশের সব মানুষের কাছেই সেই সুবিধা পৌঁছত। এ বছরের আর্থিক সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ সালের পর থেকে এ দেশে পুরুষ ও মহিলা, উভয় গোত্রের কর্মীরই প্রকৃত আয় (অর্থাৎ, টাকার অঙ্কে আয় থেকে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ বাদ দিলে যা পড়ে থাকে) কমেছে— চাকরিরতদের ক্ষেত্রে, স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। এই সময়কালে কেবলমাত্র ঠিকা শ্রমিকদের প্রকৃত আয় যৎসামান্য বেড়েছে। কিন্তু, লকডাউনজনিত কারণে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ধাক্কা খাওয়া বাদে এই সময়কালে দেশের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, এই সময়কালে আর্থিক অসাম্য বেড়েছে তাৎপর্যপূর্ণ হারে। এই অবস্থায় পরোক্ষ কর তিলমাত্র না কমিয়ে আয়ের নিরিখে শীর্ষ দশ শতাংশকে কর ছাড় দিলে সেই অসাম্য আরও বাড়বে বই কমবে না।
বাজেট অনুমানের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্র থেকে রাজ্যে অর্থ হস্তান্তর খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১.১৩ লক্ষ কোটি টাকা কম। এর ফলে রাজ্য সরকারগুলির সামাজিক খাতে ব্যয়ের উপরে বিপুল প্রভাব পড়তে পারে। কৃষি, গ্রামোন্নয়ন (এনআরইজিএস-সহ), খাদ্য ভর্তুকি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বাজেট অনুমানের তুলনায় ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকা কম। মূলধনি খাতে ব্যয়ও বাজেট প্রতিশ্রুতির তুলনায় কমেছে ৯২,৬৮২ কোটি টাকা। জিডিপি-র অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমেছে— ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে প্রতিশ্রুত অনুপাতটি ছিল ১৫.০৪%; দেখা গেল, সংশোধিত অনুমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৪.৫৫%; এবং ২০২৪-২৫’এর বাজেট অনুমানে তা ১৪.১৯%। যেখানে অর্থব্যবস্থা আটকে আছে কম চাহিদার ফাঁদে, সেখানে এই বাজেট আশাপ্রদ নয়।
বস্তুত, ধনীদের আয়করে ছাড় দেওয়ায় তাঁদের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় যতখানি বাড়তে পারে, তার মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টের তুলনায় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট বেশি। তার কারণ, সরকার সামাজিক খাতে ব্যয় করলে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে মানুষকে নিজের পকেটের টাকা কম খরচ করতে হয়। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি বা কর্মসংস্থান প্রকল্প দরিদ্রতম মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায়। অবস্থাপন্নদের তুলনায় দরিদ্র মানুষ তাঁদের আয়ের অধিকতর অংশ ভোগব্যয় করেন, ফলে অবস্থাপন্নদের আয় এক টাকা বাড়লে জিডিপি যতখানি বাড়ে, দরিদ্রের আয় এক টাকা বাড়লে জিডিপি বাড়ে তার চেয়ে বেশি।
এই বাজেটে ব্যয়ের ২৫% যাবে সুদ মেটাতে— অর্থাৎ, করদাতাদের থেকে টাকা হস্তান্তরিত হবে বন্ড-ক্রেতাদের কাছে। এতে অবশ্য সার্বিক চাহিদা বিশেষ বাড়বে না। রফতানির অবস্থা ভাল নয়, কারণ উন্নত দুনিয়াতেও আর্থিক ডামাডোল চলছে। জিডিপি-র অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নমুখী; দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে মোট গচ্ছিত অর্থের অনুপাতে ঋণগ্রহণের পরিমাণও কম। কর ছাড়ের ফলে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় নিশ্চিত ভাবেই খানিকটা বাড়বে।
কিন্তু এর পাশাপাশি যদি সরকারের মোট ব্যয়, মূলধনি খাতে ব্যয়, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় এবং রাজ্যগুলির অর্থবরাদ্দের পরিমাণও বাড়ত, তা হলে আর্থিক বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানও গতিশীল হত, অসাম্য কমত, মানবোন্নয়ন নিশ্চিত হত, এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো জোরদার হত। সে ক্ষেত্রে অবশ্য জিডিপি-র অনুপাতে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ এতখানি কমত না। কিন্তু এই মুহূর্তে অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও লগ্নি বাড়াতে, পুঁজির লাভযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, এবং আয়বৃদ্ধি ঘটাতে প্রসারণমুখী আর্থিক নীতি প্রয়োজন ছিল। জিডিপি-র অনুপাত রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ কমা মানেই সুসংবাদ নয়— এতে সার্বিক চাহিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অর্থমন্ত্রী যত জোর গলায় ‘বিকশিত ভারত’-এর কথা বলেছেন, তাঁর বাজেটের সংখ্যাগুলির গলায় তত জোর নেই, এটাই উদ্বেগের কথা।
সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ় অ্যান্ড প্ল্যানিং, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)