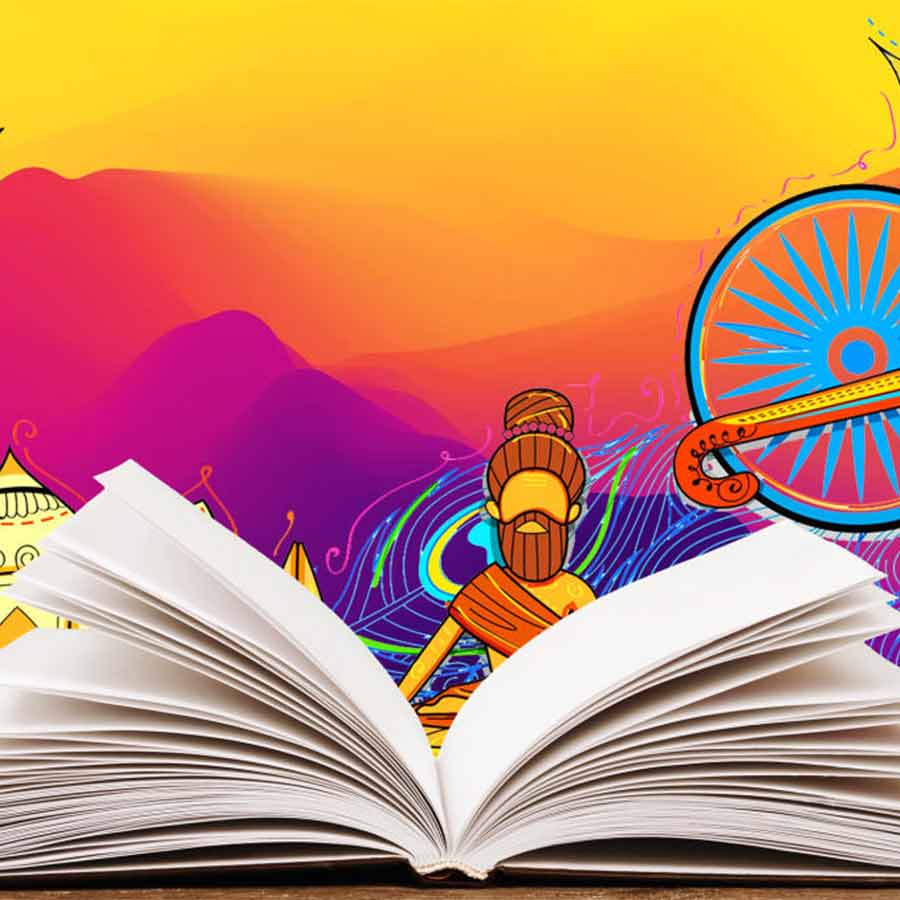ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। ছোট করে আইকেএস। কথাটা পাক খাচ্ছে। উচ্চতর ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বদেশি জ্ঞানতন্ত্রের পর্যালোচনা ও শিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট নীতি ও পাঠ্যসূচিনির্ধারণ করা হচ্ছে। বৈদিক গণিত, মনু-সংহিতা, জ্যোতিষ পাঠ্যসূচিতে উঁকি দিচ্ছে।
এই সূত্রে মনে পড়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের (১৮৭৫-১৯৪৯) একটি বক্তৃতার কথা। ‘স্বরাজ ইন আইডিয়াজ়’ নামের সেই বক্তৃতা-নিবন্ধের প্রসঙ্গ অথবা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দর্শননিষ্ঠার স্মৃতি এ-কালের ‘ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম’-এর ধরতাইতে খুব গভীর ভাবে উঠে আসছে তা অবশ্য নয়।
চিন্তা-ভাবনা ও ধারণায় স্বরাজ বলতে কী বোঝাচ্ছিলেন তিনি? তাঁর ইংরেজি লেখার বাংলা শিরোনাম হিসাবে ‘মননের স্বরাজ’ কথাটিও ব্যবহৃত হয়। বোঝাচ্ছিলেন পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতার অধীনে থাকার ফলে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে পরম্পরার শিকড়টি ছিঁড়ে গেছে। ছিন্নমূল আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করি বটে কিন্তু অপর সংস্কৃতি যখন অজানতেই আমাদের উপরে আধিপত্য করে, তখন সাংস্কৃতিক-স্বরাজের দাবি উত্থাপন করি না। অথচ উচ্চশিক্ষার স্তরে বিশেষত ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য প্রধানত এই তিনটি বিদ্যাক্ষেত্রে দেশজ ভাষাবাহিত (ভার্নাকুলার) মনের নিজস্ব চিন্তা ও অবদান প্রতিষ্ঠার বিশেষ অবকাশ তো গড়ে তোলা উচিত।
প্রসঙ্গটি পরাধীন ভারতে চন্দননগরে ত্রিশের দশকের গোড়ায় যখন উচ্চারণ করছিলেন কে.সি.— এ ভাবেই তাঁকে ডাকতেন ছাত্ররা— কেউ কেউ সে চেষ্টা করেছিলেনও, নানা-সময়। ‘আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত কান্টদর্শনের তাৎপর্য’-সহ প্রকাশিত হয়েছিল রাসবিহারী দাসের গ্রন্থ কান্টের দর্শন। ভূমিকায় ছাত্র রাসবিহারী কৃষ্ণচন্দ্রের ভাবনার অনুষঙ্গেই লিখেছিলেন, বাংলা ভাষায় ‘কান্টের মতো আধুনিক, বিরাট ও দুরূহ দার্শনিকের কথা যদি’ প্রকাশ করতে পারেন তা হলে বাংলায় দার্শনিক চর্চার ক্ষেত্রে ভাষাগত কোনও আপত্তি থাকবে না। বাংলা ভাষায় লেখার দ্বিতীয় কারণটি গুরুতর। ‘অনেক স্থলে কান্টের কথা’ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। এই যে মতপার্থক্য তা নিজের ভাষায় স্পষ্ট করে বলা চাই। এতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তবে সব কিছু গ্রহণ করতে না পারলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন কান্টের কাছ থেকে যে-রকম দার্শনিক শিক্ষা পেয়েছিলেন আর কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিকের কাছ থেকে সে-রকম শিক্ষা পাননি।
এই ছিল তা হলে কে.সি.-র কাছ থেকে শেখা চিন্তা-ভাবনা-ধারণায় স্বরাজ অনুশীলনের মডেল। অপর সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে বোঝা, শেখা, পর্যালোচনা করা ও নিজের বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা। দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমন একই অনুশীলন পদ্ধতি থাকতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়বে সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ জীবনের শেষ পর্বে ইংরেজিতে নয় স্বভাষায়, বাংলা ভাষায়, ইতিহাসচর্চা করছিলেন। রণজিৎ গুহর স্বভাষার ইতিহাস চর্চা পাশ্চাত্যের ‘হিস্ট্রি’-র আদর্শকে অনুসরণ করছিল না।
এই যে স্বাদেশিক আত্মপ্রত্যয় তা কিন্তু ফাঁকিবাজিপনার উপর নয়, কতকগুলি বিষয়ের গভীর অনুশীলনের উপরেই নির্ভর করছিল। কে.সি. ও তাঁর অনুগামীরা কেউ এক-ভাষার সঙ্কীর্ণ দুর্গে নিজেদের বন্দি করেননি। স্বভাষার গুরুত্ব, ক্ষেত্র-বিশেষে জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুবাদ-অসম্ভব নিজস্বতা (স্বধর্ম/সধর্ম)-কে স্বীকার করে নিলেও, অন্য ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময় ও কথোপকথন তাঁরা থামাননি। এই বক্তৃতায় তিনি আর একটি বিপদের কথাও বলেছিলেন। এক দিকে যেমন পাশ্চাত্যের জ্ঞানতন্ত্রের পরভাষা-নির্ভর অক্ষম অনুকরণ আমাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করছে তেমনই ‘আমাদের সংস্কৃতির সবকিছুর নির্বিচার মহিমা-কীর্তন’ আর ‘অপর সংস্কৃতির সবকিছুর অবমূল্যায়ন’ ঘোরতর বিপদ হিসাবে দেখা দিচ্ছে।
নিজের সংস্কৃতি তো বোঝা গেল কিন্তু এই অপর কারা? সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা ‘মুসলমান’ ও ‘শ্বেত-সাহেব’দের সহজেই অপর বলে দাগিয়ে দেন। এই যে ‘নিজের সংস্কৃতির নির্বিচার মহিমা কীর্তন’ ও ‘অপরের অবমূল্যায়ন’ তার চমৎকার সকৌতুক নিদর্শন বিবেকানন্দের একাধিক বাংলা লেখায় আছে। গুরুভাই ব্রহ্মানন্দকে লেখা বাংলা ভাষার চিঠিখানির কথা মনে পড়বে। ‘১৪ বার হাতে-মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ?— এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ দু’হাজার বৎসর ধরে। এ দিকে এক-চতুর্থাংশ মানুষ খেতে পায় না... ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের বাপ-মা আহ্লাদে আটখানা। ...আবার ও কাজে মানা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি... সমস্ত গৃহ্যসূত্রেরই এই আদেশ।’ বিবেকানন্দের এই চিঠি পড়লে লোকাচারকে নির্বিচারে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের মহিমময় অংশ বলার অপকীর্তনের চেহারাই শুধু চোখে পড়ে না, হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতার ধুয়ো তুলে ভারতীয় মুসলমানদের ‘অপর’ বলার রোগও শনাক্ত করা যায়।
শুধু কি মুসলমান? মার্গারেট নোবল তখনও এ দেশে আসেননি, বিবেকানন্দ চিঠিতে তাঁর শিষ্যাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এ দেশের সাধারণ মানুষদের ‘জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। ...ভয়ে হোক বা ঘৃণাতেই হোক— তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে।’ এই ভয় আর ঘৃণার সঙ্কীর্ণতা থেকে অপর সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন করে নিজের সংস্কৃতির বড়াই করা কে.সি. নির্দিষ্ট মননের স্বরাজ নয়, সেই ভয় ও ঘৃণা থেকে জেগে ওঠা আপন মহিমা কীর্তনের সুবাদে পুনরায় যদি বিবেকানন্দ পরিত্যাজ্য ‘গৃহ্যসূত্র’ কিংবা ‘পুরোহিত দর্পণ’ পড়তে হয় ও তাকে আই.কে.এস. বলে দেখাতে হয় তা হলে পিছন দিকে নির্বিচারে এগিয়ে যাওয়াই হবে।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘ইন্ডিয়ানিজ়ম’ এই ইংরেজি শব্দের ভারতীয়করণের জন্য একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন— ‘তহন্নুদ’। লিখেছিলেন, ‘কিসের ইন্ডিয়া, কিসের হিন্দ্, যদি তার ভারতধর্ম, তার ইন্ডিয়ানিজ়ম, তার ‘তহন্নুদ’-ই না রইল?’ কে.সি.-ও কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন তেমন সমন্বয়কেও ক্ষেত্র-বিশেষে অনিবার্য বলে মনে করেন। কী ভাবে এই সমন্বয় ঘটবে তাই তো মননের স্বরাজ ও স্বাধিকারের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। আর সেই সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন একদা ‘অপর’ বলে চিহ্নিত সংস্কৃতির সব কিছুর অবমূল্যায়ন আমরা বন্ধ করব। এই যে হিন্দুত্ববাদীরা, বিবেকানন্দের চিঠি অনুসারে ‘মুসলমান’দের দোষ দিচ্ছিলেন তার কারণ তাঁদের সঙ্কীর্ণপন্থা, অপর সংস্কৃতি মাত্রকেই তাঁরা হীন চোখে দেখেন। এ দিকে সমন্বয়ের সূত্রে যে ভারতীয় ইসলামের নিজস্ব রূপের স্বরাজ তৈরি হয়েছে, তাঁদের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকায় ‘দরাপ খাঁ গাজী’ (১৩৫৪) ও ‘অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত’ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) দু’টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সতথ্য দেখিয়েছিলেন কী ভাবে সমন্বয়ী ইসলামের ভারতীয় রূপ গড়ে উঠেছিল।
এই মননের স্বরাজের সূত্রেই ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব ও চিন্তনপদ্ধতির কথা উঠেছিল নানা সময়ে। যাঁরা জ্ঞানতত্ত্ব ও চিন্তনপদ্ধতির স্বরাজের কথা বলতেন তাঁরা কিন্তু এই জ্ঞানতত্ত্ব ও চিন্তনপদ্ধতি বলতে ভারতের কতকগুলি প্রথা বা পাঠ্যের উপর দাগা বুলোনোকে বোঝাতেন না। অথচ মজার কথা, এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে দাগা-বুলোনোর কথা বললে আর কতকগুলি চিহ্নের জনপ্রিয় দৃশ্যগ্রাহ্য রূপের আমদানি করতে পারলে সহজে ‘জনতোষণ’ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যখন গান্ধীবাদীদের নির্বিচার চরকা-ঘোরানোর বিরোধিতা করছিলেন তখন তিনি গান্ধীর চিন্তা ও পথের নিজস্বতার বিরোধিতা করেননি, গান্ধীর নামে লোকাচারের বিরোধিতা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর নির্মলকুমার বসু ‘গণতন্ত্রের সংকট’ বোঝাতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন খদ্দর, টুপি, কোট জাতীয় বাহ্য চিহ্ন দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার উপায় হয়ে উঠেছে।
মিলন কুন্দেরা তাঁর ইমমর্টালিটি উপন্যাসে সকৌতুকে দেখিয়েছিলেন শ্রমিকদের দাবি, বামপন্থা, শান্তি ইত্যাদি গুরুতর বিষয়গুলি শিকলছেঁড়া হাত কিংবা পায়রার ছবিতে পর্যবসিত হয়েছিল। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলতে যদি নিজের ভাষায় মননের তর্কশীল সমন্বয়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং অপর ভাষার সঙ্গে বিনিময়পন্থী অনেকান্তবাদী বহুত্ববোধক বিদ্যাচর্চা না বুঝিয়ে পুরনো কতকগুলি সংস্কৃত রচনার নির্বিচার বুলি-কপচানো হয় তা হলে ভারতীয় জ্ঞানপদ্ধতির আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবে।
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)