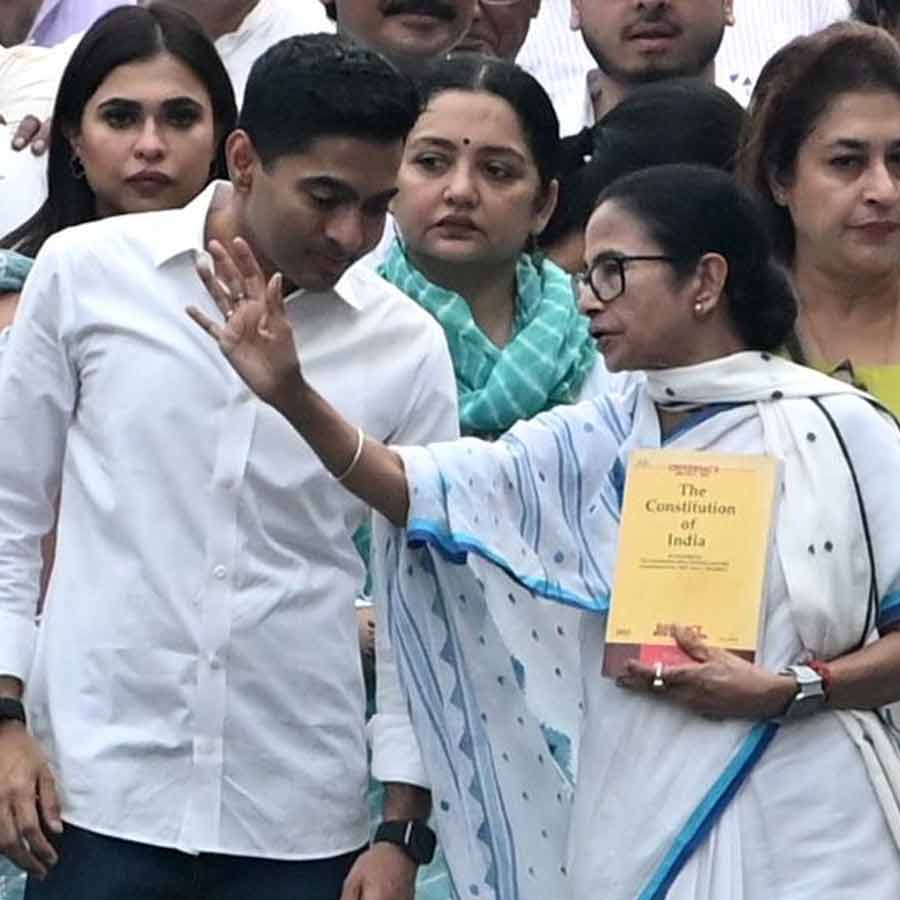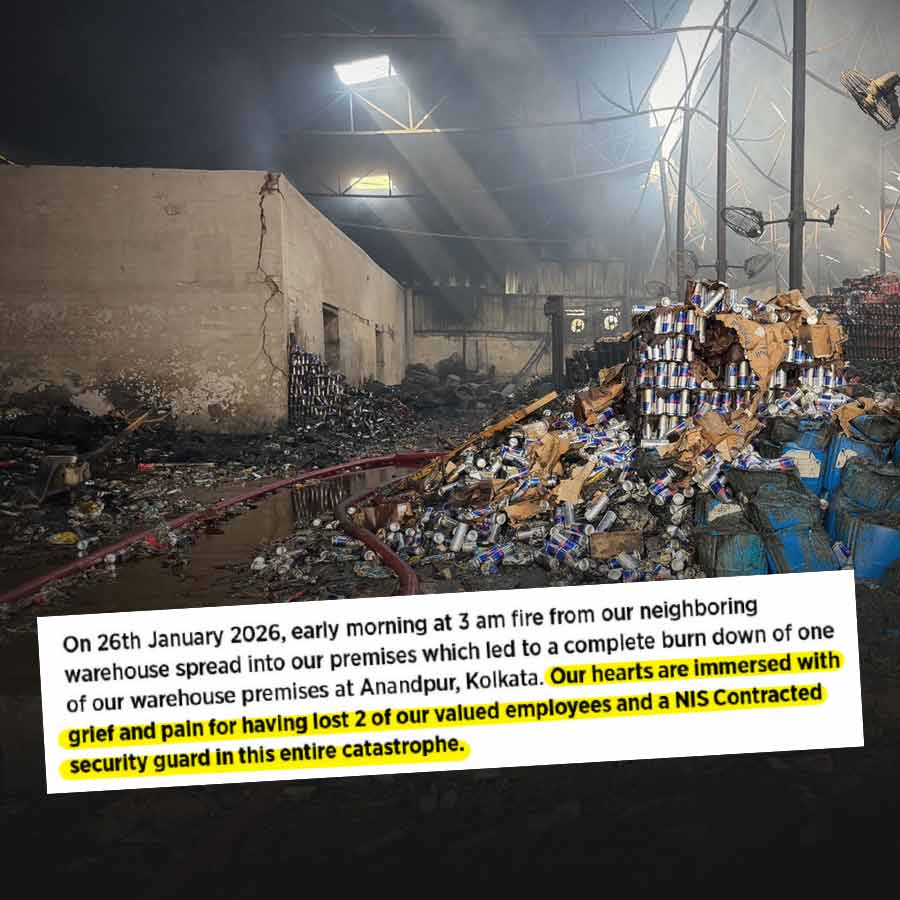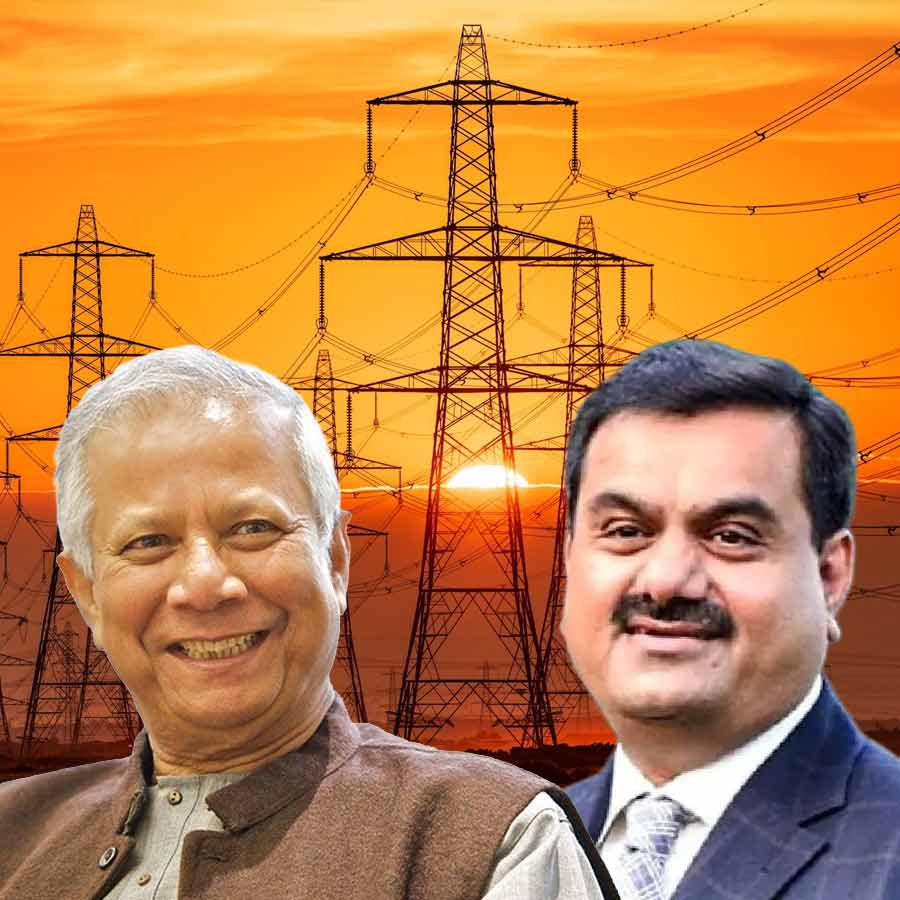রেডিয়োয় শোনা একটা গানের কলি, ঠাকুমার তোরঙ্গের গন্ধ, কিংবা ছেলেবেলার বন্ধুর মুখ বহু বছর পরেও কী অদ্ভুত ভাবে হঠাৎ ভেসে ওঠে, যেন এই সে দিনের কথা। কোথায় থাকে এই স্মৃতি? মান্না দে গেয়েছিলেন বটে, “হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে,” কিন্তু গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা কথাগুলি কতটা সত্যি? আমরা মনে করি বটে, হৃদয় বা মনই ধরে রাখে বহু আগেকার, কিংবা নিকট অতীতের, সব প্রত্যক্ষ, অনুভব, চিন্তাভাবনা। তবে আজকের স্নায়ুবিজ্ঞান (নিউরোসায়েন্স) বলছে, স্মৃতি আসলে এক জৈব-রাসায়নিক রচনা। মস্তিষ্কের মধ্যে কয়েক লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষের (নিউরন) আদানপ্রদান বা সিন্যাপস-এর মাধ্যমে স্মৃতি তৈরি হয়। যে কোনও কোষের মতো, স্নায়ুকোষও তৈরি হয় প্রোটিন দিয়ে। যখন এই কোষগুলোর প্রোটিন প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে, তখন তাদের দ্বারা নির্মিত স্মৃতি টিকে থাকে কী ভাবে? স্মৃতির নতুন পাঠ তাই বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে উঠেছে এক অদৃশ্য বন্ধনের অনুসন্ধান।
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের স্নায়ুবিজ্ঞানী টড স্যাক্টর এবং তাঁর সহকর্মীরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ২০২৪ সালে আবিষ্কার করেছেন, স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় দু’টি প্রোটিনের সংযোগের জন্য। তাদের একটির ভূমিকা হল, স্নায়ুকোষের আদানপ্রদানের সময়ে যে পরিবর্তনগুলি হয়, যা স্মৃতি নির্মাণ করে, সেগুলিকে সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল রাখা, যাতে সময়ের সঙ্গে স্মৃতির ‘ছাপ’ মিলিয়ে না যায়। দ্বিতীয় প্রোটিনটি প্রথমটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে, যা সিন্যাপস-এর শক্তি দীর্ঘ দিন বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে যে কোনও তথ্য শেখার পর তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে মস্তিষ্ক। এই দু’টি প্রোটিনের সংযোগ রয়েছে স্মৃতির স্থায়িত্বের মূলে। এদের বন্ধনেই বাঁধা থাকে আমাদের ফেলে-আসা দিন।
টড স্যাক্টর এবং ডাউনস্টেট মেডিক্যাল সেন্টার-এ তাঁর সহকর্মী স্নায়ুবিজ্ঞানীরা ইঁদুরের উপর পরীক্ষায় করে দেখেছেন, যখন এই প্রোটিনের কাজের ধারা ব্যাহত করা হয়, তখন ইঁদুর তার শেখা বিষয় ভুলে যায়। আবার বন্ধনটি পুনরায় সক্রিয় হলে, পুরনো স্মৃতি ফিরে আসে। এই গবেষণা থেকে বোঝা যায়, স্মৃতি শুধুই মস্তিষ্কে রেখে যাওয়া ছাপ নয়, বরং একে বলা চলে অণুর স্বাক্ষর— যা কোষে গেঁথে থাকে। এ দু’টি প্রোটিন কেবল জৈব অণু নয়, বরং তারা আমাদের জীবনের প্রতিটি ‘মনে রাখা’ মুহূর্তের রক্ষাকবচ। তারা বলে দেয়, কোথায় থেমে ছিল কোনও কথা, কোথায় রাখা ছিল চোখের জল।
এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কতখানি, তা বোঝা কঠিন নয়। এর প্রয়োগের প্রথম ক্ষেত্র অবশ্যই চিকিৎসায়। স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার সম্ভাবনাকে কে না ভয় পান? অনেকেই মনে করেন, স্মৃতি হারিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুও শ্রেয়। ডিমেনশিয়া, অ্যালঝাইমার’স-এর মতো চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশ দিতে পারে। এমনকি কোনও ভয়ানক মানসিক আঘাতের অভিঘাতে স্মৃতি আংশিক নষ্ট হওয়ার (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেট ডিজ়র্ডার বা পিটিএসডি) মোকাবিলাও করতে পারে। এই সব রোগে স্মৃতির অবক্ষয় একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। যদি এই প্রোটিন বন্ধনকে প্রভাবিত করা যায়, তা হলে স্মৃতি মুছে যাওয়ার গতি ধীর করে দেওয়া যায়, এমনকি তার গতি উল্টো মুখে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, যার ফলে হারানো স্মৃতি ফিরে আসে। নিকটজনদের যাঁরা চিনতে পারছেন না, তাঁরা ফের ফিরে পেতে পারেন সে সব সম্পর্ক। এই স্মৃতি-জাগানিয়া ওষুধ বাজারে আসা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার, মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। আবার, বহু চেষ্টা করেও যা ভুলতে পারছেন না, বিজ্ঞানের হাতে হয়তো এসে গিয়েছে তা থেকে রেহাই দেওয়ার চাবিকাঠিও।
কিন্তু রোগ প্রতিহত করা ছাড়াও আরও বড় তাৎপর্য রয়েছে এই আবিষ্কারের। স্মৃতির এই জৈবিক ব্যাখ্যা আমাদের মনের সংজ্ঞা নিয়ে আবার চিন্তা করতে বলে। আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে চিন্তা, উপলব্ধি, বা আবেগও কোষের কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই উঠে আসে আরও গভীর একটি প্রশ্ন, স্মৃতি কার নির্মাণ? ওই গানের কলি, ওই চেনা গন্ধ, সে কি আমি সচেতন ভাবে আমার অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে বেছে নিয়ে ‘মনের মণিকোঠায়’ সংগ্রহ করে রাখি, না কি আমাদের কোষেরা তা করে আমাদের অজানতেই? চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, মূল্যবোধ— সব মিলিয়ে আমার যা পরিচয়, তা সেই স্মৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র?
স্মৃতি কেবল ব্যক্তিগত নয়, তা ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বাহক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য— আমাদের স্বদেশ যেমন স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, তেমনই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। স্মৃতিই ধারণ করে জাতিকে। ইতিহাসের বোধও শেষ বিচারে দু’টি প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ভিতরের প্রকরণকেও এই গবেষণা নতুন করে ভাবতে শেখায়। যা কিছু এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে— গল্প হয়ে, গান হয়ে, স্মৃতি হয়ে— তার সবেরই উৎস স্নায়ুকোষের প্রোটিনে।
কম্পিউটেশনাল জীববিজ্ঞান, ইউনিভার্সিটি অব আরকানসাস
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)