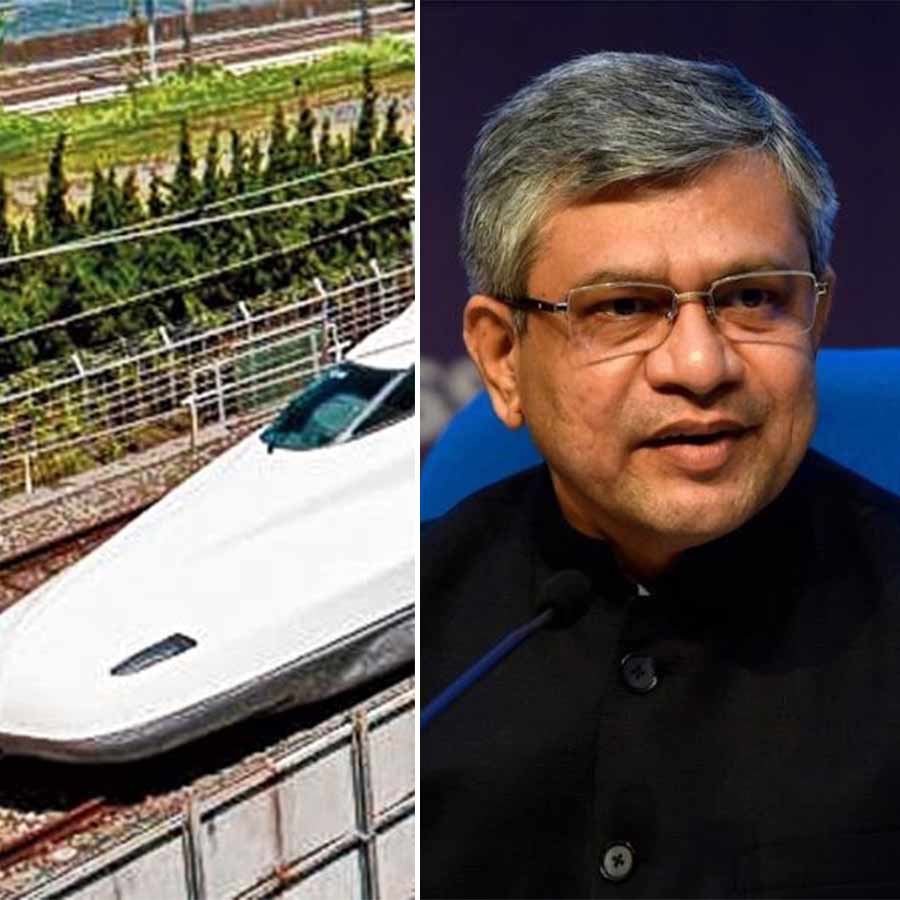সেটা ছিল মার্চ মাস। দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি বর্মার ভাঁড়ার ঘর থেকে অসংখ্য অর্ধদগ্ধ নোট উদ্ধার হল। সরকার নড়েচড়ে বসল, এ বার বুঝি লাগাম লাগানোর সুযোগ এসেছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই বিষয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও সরকার পক্ষের নেতার অতি সক্রিয়তা প্রকাশ্যে এলেও সুপ্রিম কোর্টের সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি তৈরি করে দ্রুত রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন মহলে একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা হল, সর্বোচ্চ আদালত আদতে বিষয়টিকে ঠান্ডা ঘরে পাঠাতে চাইছে। জনৈক বিজেপি সাংসদ সরাসরি সংবাদমাধ্যমে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করলেন। তবে দেখা গেল, প্রধান বিচারপতি খন্না অবসরের এক দিন আগেই রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সরকারের কাছে ওই বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাঠিয়ে অভিযুক্ত বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।
ইতিমধ্যে ৮ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়াল এবং আর মহাদেবন তামিলনাড়ু সরকার বনাম তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের মামলায় এমন এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। বিচারপতি পারদিওয়াল ও মহাদেবন ঘোষণা করলেন, কোনও রাজ্য বিধানসভায় যে বিল পাশ হয় সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে এক মাসের মধ্যে সম্মতি দিতে হবে, অন্যথায় তিন মাসের মধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে হবে। যদি রাজ্যপাল মনে করেন বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে তাঁকে রাষ্ট্রপতির কাছে বিলটি পাঠাতে হবে। রাজ্যের আইনসভা যদি আবারও বিলটি সংশোধিত অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় মঞ্জুর করে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠায়, সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে সম্মতি দিতেই হবে। কোনও বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল যদি আটকে রাখেন তার নিষ্পত্তি রাজ্য ও কেন্দ্রের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে ঘটাতে হবে। স্বরাষ্ট্র দফতরের ৪/২/২০১৬ তারিখের দু’টি নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিল।
এই ঐতিহাসিক রায় ইতিমধ্যে আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অনেককেই উৎসাহিত করেছে, বিশেষত যাঁরা শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের ধারণায় বিশ্বাসী। তবে ভিন্ন মতাবলম্বীদেরও সংখ্যা নেহাত কম নয়। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সুপ্রিম কোর্টের ‘বিশেষ ক্ষমতা’ নিয়ে প্রকাশ্যেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বিচারব্যবস্থা এখন ‘সুপ্রিম পার্লামেন্ট’-এর অবয়ব নিয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। স্বাধীন ভারতে কোনও উপরাষ্ট্রপতি এমন মনোভাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে জনসমক্ষে সমালোচনা করেছেন, এমন কোনও পূর্ব নজির নেই। তবে শ্রীধনখড় নিজগুণে বিশিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন তিনি নিয়মিত রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেন সংবাদমাধ্যমে। রাজ্য বিধানসভায় মঞ্জুর হওয়া ডজন-ডজন বিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রেখে দিতেন। বিরোধী-শাসিত রাজ্যে রাজ্যপালের মাধ্যমে সরকারি প্রশাসন ও বিধানসভাকে পর্যন্ত পঙ্গু করার যে প্রচেষ্টা শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার, সে বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের নাম ‘বাংলা’ করার যে সর্বসম্মত বিল রাজ্য বিধানসভায় মঞ্জুর করা হয়, সেই বিলটি আজও ঠান্ডা ঘরে শুয়ে রয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে যুক্তরাষ্ট্র-পন্থীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ঠিকই, তবে রাষ্ট্রপতি ৮ এপ্রিল রায়ের প্রেক্ষিতে ১৩ মে, সংবিধানের ১৪৩ (১) ধারাবলে মোট ১৪টি সাংবিধানিক প্রশ্নাবলি তৈরি করে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতির সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া নজিরবিহীন নয়। ইতিপূর্বে অন্তত চোদ্দো বার বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ আদালতের মতামত চেয়েছিলেন। তার মধ্যে বাবরি মসজিদ ও কাবেরী জলবণ্টনের বিষয় উল্লেখ্য। সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির আবেদনে সাড়া দিয়ে উপদেশমূলক মতামত দিতে পারে, আবার উপেক্ষাও করতে পারে। যেমন, বাবরি মসজিদের স্থাপত্যের নীচে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের চরিত্র নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মতামত চাওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালত তা উপেক্ষা করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ৪২৪ পাতার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত ইস্যুকে বিচারের অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের যাবতীয় সওয়াল-জবাব লিপিবদ্ধ করেছে। তার পর প্রতিটি বিষয়ে আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ হয়েছে। এমনকি, যাবতীয় আইন ও সংবিধানের প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। তাঁদের মতে, রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিল কোনও যুক্তি বা কারণ না দেখিয়ে আটকে রাখতেন, তাই এই রায় সরকারের মেনে নেওয়া উচিত ছিল। নিতান্ত গ্রহণযোগ্য না হলে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা অনুযায়ী ‘রিভিউ পিটিশন’ দাখিল করা যেত। যে-হেতু তা হয়নি, বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, সরকার কি এই রায় রূপায়ণের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চায়?
ইতিমধ্যে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না ও বর্তমান প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেছেন, আইনসভা না বিচারবিভাগ কে বেশি ক্ষমতাধর, এমন প্রশ্ন নিরর্থক। কারণ, সংবিধানই সর্বোচ্চ এবং সংবিধানের নির্দেশ মেনে সমস্ত সাংবিধানিক ও আইনি সংস্থাকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন, তা কি আদৌ হচ্ছে? এই প্রশ্ন উদ্ভূত পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলছে যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক।
মনে রাখতে হবে, বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা বা ‘জুডিশিয়াল রিভিউ’ সংবিধানের মূল কাঠামোর অন্তর্গত। সুপ্রিম কোর্ট এ-যাবৎ একাধিক রায়ে বলেছে, আইনসভা সংবিধান সংশোধন করতে পারে, কিন্তু সংবিধানের মূল কাঠামোকে কোনও অবস্থাতেই পাল্টাতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টকে ১৪২ নম্বর ধারায় সংবিধান প্রণেতারা যে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন তা বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রকে যুগোপযোগী ও বিস্তৃত করেছে। এখন সেই ক্ষমতাকে যাঁরা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করছেন তাঁরা নিজেদের সাংবিধানিক পদের প্রতিই অমৰ্যাদা করছেন। বিচারব্যবস্থার প্রতি সংসদ বা শাসনব্যবস্থার এ-হেন মনোভাব কোনও ভাবে মান্যতা পেতে পারে না। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে ১৪টি বিষয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন তার অন্যতম বিষয় হল, জটিল আইনি ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রায়দান একমাত্র সাংবিধানিক বেঞ্চই দিতে পারে। কিন্তু রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতার প্রশ্নে এ ক্ষেত্রে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে। সুতরাং সরকারের মতে, এই রায় সংবিধানের ১৪৫(৩) ধারার পরিপন্থী। কারণ, ১৪৩ ধারায় রাষ্ট্রপতি যদি সর্বোচ্চ আদালতের মতামতের জন্য কোনও বিষয় পাঠান সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে তা শুনানি হবে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়— বহু গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও সাংবিধানিক বিষয়ে দুই বিচারপতি-বিশিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ ইতিপূর্বে বহু বার রায়দান করেছে।
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ রাষ্ট্রপতিকে যে মতামতই দিক না কেন, রাষ্ট্রপতি যেমন তা মানতে বাধ্য নন, তেমনই দুই বিচারপতির বেঞ্চ যে রায় দিয়েছেন তার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। কারণ ওই মতামত সম্পূর্ণ ভাবে উপদেশমূলক, তার কোনও আইনি প্রভাব নেই। তবে এক বার সুপ্রিম কোর্ট বৃহত্তর সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে রাষ্ট্রপতির প্রশ্নাবলি নিয়ে শুনানি শুরু করলে তার কত দিনে নিষ্পত্তি ঘটবে তা কেউ জানে না। সেটাই কি লক্ষ্য? সেই বিলম্বিত প্রক্রিয়ার আশাতেই কি সরকার এখন দিন গুনছে, নিজের মুখ বাঁচাতে?
সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)