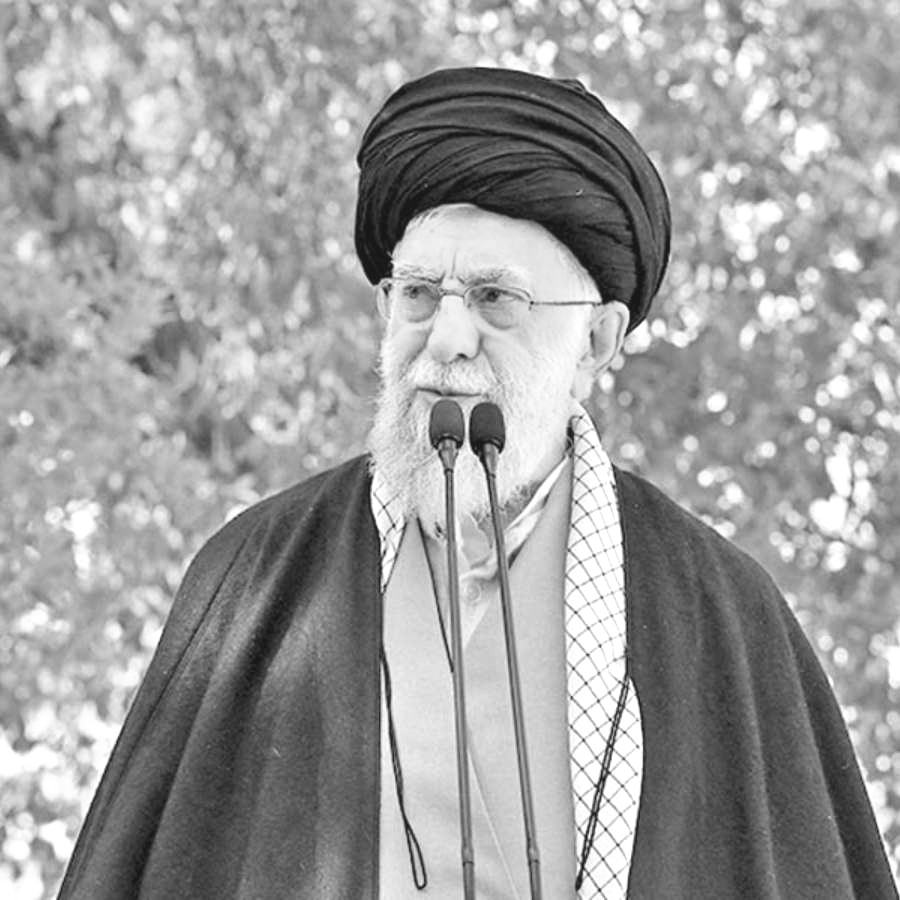এক মাস হল, ফরাক্কা বাঁধের বয়স পেরোল পাঁচ দশক; নির্মাণকাল ধরলে আরও এক দশক। রূপরেখা রচনার সময় থেকে নানা সমালোচনা ও বিরোধিতা এই প্রকল্পের পিছু ছাড়েনি। এমনকি বাঁধ ভেঙে ফেলার দাবিও উঠেছে দেশে এবং বিদেশে। কপিল ভট্টাচার্য থেকে মৌলানা ভাসানি, ভাগলপুরের মৎস্যজীবী থেকে মালদহ-মুর্শিদাবাদের ভাঙনে ঘরহারা উদ্বাস্তু পরিবার— ফরাক্কা প্রকল্পের কঠোর সমালোচকের তালিকা বিপুল। ২০১৬-র অগস্ট মাসে বিহারের বন্যার জন্য ফরাক্কাকে দায়ী করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ভারত সরকারের কাছে বাঁধ ভেঙে ফেলার দাবি করেছিলেন।
১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিন দশকের জন্য যে জল-ভাগাভাগি চুক্তি হয়েছিল, তার মেয়াদ ২০২৬-এর ডিসেম্বরে শেষ হবে। এই উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে নতুন চুক্তি বা বর্তমানে বহাল চুক্তির পুনর্নবীকরণ হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে। কয়েক দিন আগে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন-এর অধ্যাপক বায়েস আহমেদ বলেছিলেন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পিছনে কার্যকর পাঁচটি কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, একটি কারণ অবশ্যই গঙ্গা ও তিস্তার জল। সে দেশের বহু মানুষ মনে করেন যে, ওই দুই প্রকল্প বাংলাদেশকে জলের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শেখ হাসিনার শাসনকালেই প্রকাশিত নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য সরকারি ভূগোল বইতে লেখা হয়েছে যে, ভারতে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভয়াবহ সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে, পদ্মা-সহ উত্তরাঞ্চলের সব নদীতেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে শুষ্ক মরসুমে জলের চরম সঙ্কট দেখা দেয়। হাসিনা-বিরোধী দলগুলি এই বিষয়টিকে প্রচারের হাতিয়ার করেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতি গঙ্গার জলের উপরে নির্ভরশীল নয়; ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে মহানন্দা, টঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়া ও তিস্তা। এ কথা তর্কাতীত যে, ফরাক্কা বাঁধের কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, যার মধ্য দিয়ে গঙ্গার শাখানদীগুলি সাগরের দিকে বয়ে যায়।
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার যে বিপুল জলস্রোত বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সাগরে মেশে, ফরাক্কা ফিডার খাল দিয়ে বয়ে আসা ৪০ হাজার কিউসেক জল তার মাত্র ২.৬%। রাজমহল পাহাড় আর মেঘালয়ের মালভূমির মাঝের সমভূমি দিয়ে গঙ্গা, তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র ছাড়া অন্য যে নদীগুলি বাধাহীন ভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সেগুলি হল মহানন্দা, জলঢাকা ও তোর্সা। সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া নদীর নীচে অলক্ষ্যে বয়ে চলে অন্য এক নদী, যার নাম ভূগর্ভের জলস্রোত। আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ভূগর্ভের কত পরিমাণ জল বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তার কোনও হিসাব না থাকলেও অববাহিকার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছে যে, গঙ্গা দিয়ে বহমান বাৎসরিক ৫২৫ ঘনকিলোমিটার জলের নীচে লুকিয়ে বয়ে চলেছে ২০২ ঘনকিলোমিটার জলের ধারা। নদীর মতো এই গতিশীল জলও আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে যায়। তবে সীমান্ত পেরিয়ে এই জলস্রোতকে বাংলাদেশের দিকে বয়ে যেতে দেওয়া ভারতের বদান্যতা নয়— নদী বয়ে চলে প্রকৃতির নিয়মে, নিম্নমুখী স্রোতকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সিন্ধু বা গঙ্গার জলের উপরে ভারত একক অধিকারের কথা ভাবলে, চিন থেকে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র বা নেপাল থেকে বয়ে আসা কোসী, গণ্ডক ও ঘর্ঘরার জল দাবি করার নৈতিক অধিকার আমাদের থাকে না।
তিস্তার জল নিয়ে অন্তহীন তর্ক-বিতর্কের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে সমস্যার মূল কারণ এবং সমাধানের সূত্র। এ পারের গজলডোবা এবং ও পারের দুয়ানি ব্যারাজ থেকে যে বিস্তৃত এলাকায় বোরো ধান বা শীতের আনাজ চাষের জন্য সেচ দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে, সেই চাহিদা মেটাতে যত জলের প্রয়োজন, তত জল তিস্তা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় না। সিকিমে তিস্তা ও তার উপনদীগুলির খাত রুদ্ধ করে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ফলে জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তিস্তায় যত জল বয়ে যায়, জলের চাহিদা তার চেয়ে অনেক বেশি। নদী থেকে সব জল টেনে নিলে বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা ব্যাহত হয় এবং সেই ক্ষতি অপূরণীয়। অবাস্তব সেচের প্রত্যাশা কমিয়ে কিছু পরিমাণ জল নদীখাত ধরে অবিরল বয়ে গেলে দুই দেশেরই মঙ্গল।
অন্য সব নদী প্রকল্পের মতোই ফরাক্কা বাঁধেরও লাভ-ক্ষতি অনস্বীকার্য। একটি নির্দিষ্ট অনুভূমিক ব্যাপ্তির মধ্যে ভূমিক্ষয় ও পলি সঞ্চয় গঙ্গার স্বাভাবিক ধর্ম। ফরাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের পর বন্দি গঙ্গার অস্থিরতা বাড়লেও মালদহ, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন এখন কিছুটা স্তিমিত। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ফরাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলার প্রস্তাবে যাঁরা উল্লসিত হন, তাঁরা জানেন না যে, ওই কংক্রিটের কাঠামোর উজানে গত পাঁচ দশক ধরে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ পলি বর্ষার স্রোতের টানে বাধাহীন পথে পদ্মার খাত ধরে নীচের দিকে নামতে থাকলে কত শাখানদী মজে যাবে; এমনকি গঙ্গা-পদ্মাও পাড় ভেঙে নতুন পথ করে নিতে পারে। ১৯৭৫ সালে ফরাক্কার জলে বেঁচে উঠেছিল জঙ্গিপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর ২২০ কিলোমিটার গতিপথ। শুকিয়ে যাওয়া যে নদী আগে হেঁটেই পার হওয়া যেত, এখন তা স্রোতস্বিনী। ফিরে এসেছে হারিয়ে যাওয়া ‘গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন’-সহ নানা জলচর প্রজাতি। কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের পথ আশানুরূপ গভীর না হলেও জলের লবণতা কমেছে। ভাগীরথী-হুগলি নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা ৪২টি শহর ও বহু গ্রাম এখন এই নদীর উপর নির্ভরশীল।
ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশের নানা অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য না হলেও কিছুটা অতিরঞ্জিত। গাঙ্গেয় বদ্বীপ গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভূতাত্ত্বিক কারণে পূর্ব দিকে হেলে পড়েছে— এই পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা-পদ্মা নদীর খাত এমন গভীর হয়েছে যে, ভাগীরথী-সহ ভৈরব, জলঙ্গি, মাথাভাঙা, গড়াই ইত্যাদি শাখানদী মূল স্রোত থেকে বছরে অন্তত আট মাস বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু বর্ষাকালেই এই নদীগুলি সজীব হয়ে ওঠে। শুখা মরসুমে ফরাক্কা থেকে আরও ৪০,০০০ কিউসেক জল গঙ্গা-পদ্মার খাত দিয়ে বইতে দিলে শাখানদীগুলি আবার বেঁচে উঠবে, এমন ভাবনার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এই উদ্বৃত্ত জল বিপুলায়তন নদীতে সামান্য প্রভাব ফেলবে।
ফরাক্কা ফিডার খালের সর্বোচ্চ জলধারণ ক্ষমতা ৪০,০০০ কিউসেক; বাকি জল বাংলাদেশের দিকে বয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে চুক্তি হয়েছিল ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ফরাক্কায় গঙ্গা দিয়ে বহমান গড় জলস্রোতের ভিত্তিতে— চুক্তি বহাল থাকে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত। ১৯৯৬ সালের পরবর্তী তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, ওই পাঁচ মাসের মধ্যে মার্চ-এপ্রিল মাসে ফরাক্কায় জলস্রোত সবচেয়ে কম থাকে। মে মাসে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় থেকে হিমবাহ-তুষার গলা জল নেমে এসে গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করে। ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে পাঁচটি শুখা মাসের (জানুয়ারি-মে) প্রতিটিকে ১০ দিন করে মোট ১৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— এবং সাতটি ভাগে ভারতের জন্য ৪০,০০০ কিউসেক জল বরাদ্দ হলেও বাকি আট ভাগে বরাদ্দ ছিল অনেক কম। ফলে হুগলি নদীর মোহনা থেকে পলি ধুয়ে সাগরে যায়নি; ক্রমাগত ড্রেজিং করে জাহাজ চলাচলের পথ করতে হয়েছে।
এ বার চুক্তি হওয়ার কথা ১৯৯৭-২০২৫ সালে মধ্যে প্রবাহিত গড় জলস্রোতের ভিত্তিতে— যা কখনও বাস্তব পরিস্থিতির সমানুপাতিক নয়। আগামী বছরগুলিতে বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি অনিবার্য। ২০১৬ সালে ফরাক্কায় জল এত কমে গিয়েছিল যে, এনটিপিসি-র তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। এই উপমহাদেশের জনসংখ্যা এবং জলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। জলকেন্দ্রিক রাজনীতি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে। জলের জোগান যখন সীমিত, তখন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করাই সুস্থায়ী উন্নয়ন ও ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের অন্যতম শর্ত।
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)