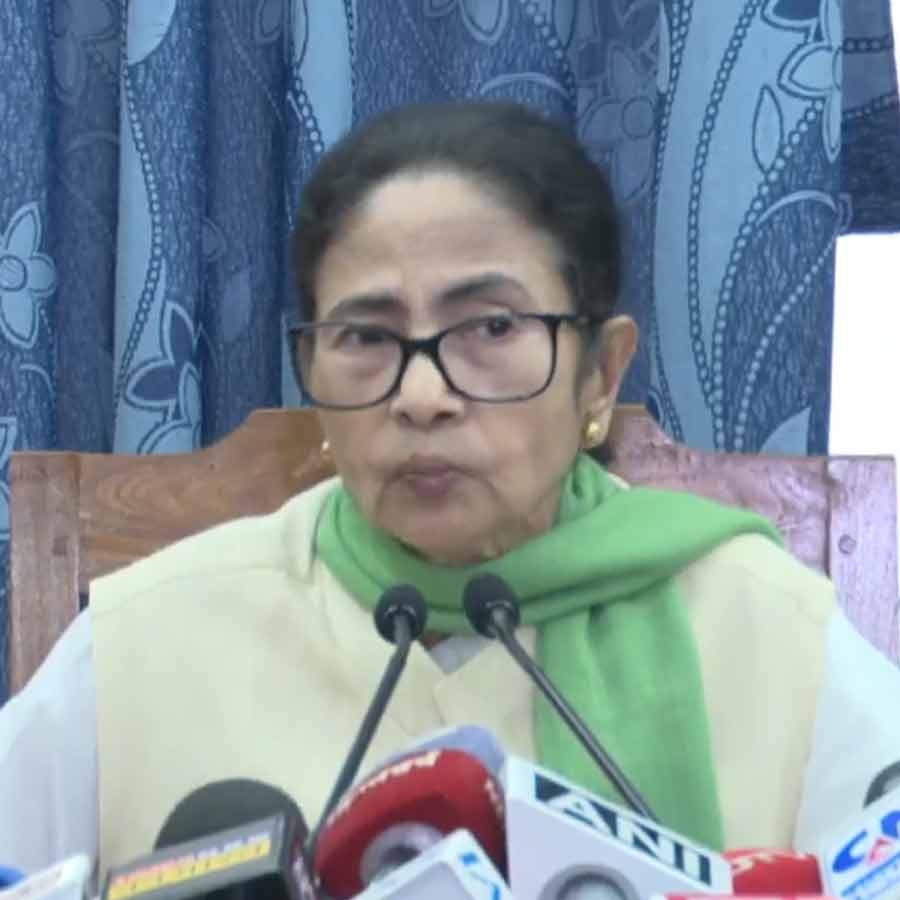‘চাই ঘরে শুশ্রূষার ব্যবস্থা’ (২০-৫) প্রবন্ধে সুব্রতা সরকার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ, অথচ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় অনালোচিত সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন। বর্তমানে ছোট পরিবার বহু এবং সেখানে জীবিকার কারণে গুরুতর অসুস্থ মানুষকে যথাযথ ভাবে দেখাশোনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পরিবারের অন্য ব্যক্তিরা বা বাড়ির বাইরে থাকা সন্তানেরা অসুস্থ মানুষের দেখভালের জন্য পরিচর্যাকারী নিয়োগ করেন। তাঁর এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা নিয়ে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে, তা অনেকের পছন্দ না হলেও রূঢ় বাস্তব। নার্স বা আয়ার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। সেই কারণে এ ক্ষেত্রে পরিচর্যাকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষিত করার জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গৃহ-শুশ্রূষার প্রশিক্ষণ চালু করার সংক্ষিপ্ত কোর্সের যে কথা উল্লেখ করেছেন প্রবন্ধকার, তা অতি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত সরকারের।
তবে বাড়িতে এসে রোগীকে ড্রেসিং করে দেওয়া বা ব্যায়াম করানোর বিষয়গুলো বিদেশে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় থাকার যে কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতেও চালু হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না বললেই চলে। কারণ, স্বাস্থ্যবিমার আওতাভুক্ত প্রত্যেক নাগরিকই জানেন, জিএসটি সংক্রান্ত কারণে বিমার প্রিমিয়াম অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও, সরকার এখনও অবধি এই বিষয়ে সুরাহার জন্য কোনও ব্যবস্থাই করেনি। যে কারণে সাধারণ মানুষ, বিশেষত অবসরপ্রাপ্তদের এই বিমার প্রিমিয়াম দিতে প্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। তা ছাড়াও দেখা যায়, চিকিৎসা-সংক্রান্ত অনেক খরচই বিমার আওতার বাইরে থাকার কারণে সে সব নিজেকে মেটাতে হয়। এর পরে প্রয়োজন হলে, বর্তমানে রাজনীতির ছত্রছায়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নার্স-আয়াদের সেন্টার থেকে পাঠানো পরিচর্যাকারীদের দ্বারস্থ হতে হয়। এঁদের মধ্যে কিছু জনের অপেশাদারিত্বের ফলে মানুষ অনেক সময়ই সুস্থ হতে পারেন না, যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। জনস্বাস্থ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সরকারি নজরদারির অভাবে এখনও অবধি অবহেলিত, কিন্তু তা মোটেই কাম্য নয়। এমতাবস্থায় উপযুক্ত সরকারি উদ্যোগের ফলে এই ক্ষেত্রে যেমন অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, তেমনই বিপুল অর্থ ব্যয়ের পর নার্সিং পাশ করে কর্মহীনরাও একটা সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন। এতে মানুষ অর্থের বিনিময়ে যে শুশ্রূষা পাবেন, তা অতি অবশ্যই নিরাপদ হবে এবং আগামী দিনে মানুষকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে, এই সামান্য আশাটুকু করা যেতেই পারে।
অশোক দাশ, রিষড়া, হুগলি
প্রশিক্ষণ দিন
সুব্রতা সরকার ‘চাই ঘরে শুশ্রূষার ব্যবস্থা’ প্রবন্ধে অত্যন্ত সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। গৃহে শুশ্রূষার জন্য মূলত তিন ধরনের ‘কেয়ার গিভার’ পাওয়া যায়। আয়াদিদি, প্রশিক্ষণ-বিহীন স্বাস্থ্য সহায়িকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স। এখন আয়া সেন্টার থেকে যাঁদের পাঠানো হয় তাঁদের রোগী বা বয়স্ক মানুষের পরিচর্যার বিষয়ে কোনও প্রশিক্ষণ থাকে না। আরও কিছু বেশি অর্থের প্রত্যাশায় আগে গৃহসহায়িকার কাজ ছেড়ে তাঁরা এই পেশায় আসেন। এঁদের মধ্যে খুব কম জনই রক্তচাপ মাপতে, ইনজেকশন বা নেবুলাইজ়ার দিতে পারেন। এই স্থানীয় সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের বড়ই আকাল।
অভিজ্ঞতা থেকে বলি, বেশির ভাগ সময়ই যাঁরা আসেন, তাঁদের পরিচালনা করার জন্য রোগীর বাড়ির কাউকে দায়িত্ব নিতে হয়। তাঁদের হাতে পুরো ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা হয় না। কিন্তু প্রবীণদের দেখভাল করার জন্য কেয়ার গিভারদের চাহিদা বেড়ে চলেছে। সরকারকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হতে হবে এবং কিছু নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এর ফলে বহু মানুষ কাজের সুযোগ পাবেন। রোগী, প্রবীণ ও তাঁদের নিকটাত্মীয়রা উপকৃত হবেন।
মলয় ভট্টাচার্য, কলকাতা-৬১
বিপদের মেঘ
সুব্রতা সরকারের প্রবন্ধ ‘চাই ঘরে শুশ্রূষার ব্যবস্থা’ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। আমার এক পরিচিতজনের বাড়িতে কর্তব্যরত আয়াদিদিকে নিয়ে একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিযোগ উঠেছিল। এই রোগিণীকে পুনরায় নার্সিংহোমে দিতে হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, রোগিণীর পেটের সমস্যাহেতু একটি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ উনি তাঁকে খাওয়াতে চাইতেন না, কারণ এতে বারে বারে রোগিণীর বর্জ্য পরিষ্কারের কাজটি করতে হত। দ্বিতীয় ঘটনাটিকে অপরাধ বললে অত্যুক্তি হয় না। আয়াদিদি এ ক্ষেত্রে মোবাইলে আসক্ত ছিলেন। বারে বারে ফোন ঘাঁটা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলার অভ্যাস ছিল তাঁর। আমার বৃদ্ধা জেঠিমার ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলেন না। তিনি নিজে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাথায় মারাত্মক চোট পান। তড়িঘড়ি জেঠিমাকে জেলা সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ঘণ্টাখানেকেই সব শেষ।
এই ঘটনাগুলি জানা যায় নজরদারি ক্যামেরার প্রমাণ মারফত। অপটু, অপ্রশিক্ষিত মানুষগুলিকে পেশাদারিত্ব এবং রোগী-সেবার গুরুদায়িত্ব বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা অত্যন্ত জরুরি। আশা রাখি, আগামী দিনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার নিরিখে উত্তীর্ণ সেবা-সহায়িকাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মযোগে গৃহকোণে সেবা দানের অনিবার্য সোপানটি আরও পোক্ত হবে।
সুপ্রতিম প্রামাণিক, আমোদপুর, বীরভূম
জয়গাথা
সায়ন্তনী শূরের লেখা ‘যুদ্ধ এবং ভারতকন্যা’ (২১-৫) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই চিঠি। বহু পথ পেরিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহরা। সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি যখন নিশ্চিত হল ১৯৯৩ সালে, ভারতের প্রথম মহিলা সেনা অফিসার হিসাবে ইয়াশিকা ত্যাগীকে প্রথমে উত্তর-পূর্ব, আর তার পর লেহ-লাদাখের উচ্চতায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট ছেলে। কার্গিল যুদ্ধকালে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই ইয়াশিকা থেকে গেলেন ছেলের সঙ্গে, লড়বার জন্য। প্রিয়া ঝিঙ্গান প্রথম মহিলা ক্যাডেট যিনি ২৫ জন অন্য অনন্য প্রতিভাবান মহিলার সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, সেনাবাহিনীতে তাঁরা মহিলাদের প্রথম ব্যাচ।
গুঞ্জন সাক্সেনা— ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় তিনি শ্রীনগরের পাইলট দলের দশ জনের এক জন। যখন তাঁর ‘চিতা’ চপারের চালকের আসনে বসে উড়তে শুরু করেছিলেন, তিনি তখন শুধুই পাইলট। তাঁর কাজ, কার্গিল যুদ্ধের জখম অফিসার-জওয়ানদের উদ্ধার করে আনা। তখন মহিলাদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কিংবা যুদ্ধবিমান চালানোর অনুমতি দেওয়া হত না। তবে গুঞ্জন এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন। স্কোয়াড্রন লিডার মোহনা সিংহের হাতে বাজপাখির রূপ ধারণ করছে ‘হক এমকে. ১৩২’। প্রথম মহিলা হিসাবে ২০১৮-র ১৯ ফেব্রুয়ারি মিগ ২১ বাইসনের চালকের আসনে বসেছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার অবনী চতুর্বেদী। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভাবনা কান্ত, ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম মহিলা পাইলট যিনি যুদ্ধবিমানে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আছে অসংখ্য নাম। ২০২৩ সালের মার্চে ভারত সরকার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ৭০০০-এরও বেশি মহিলা কর্মরত। বিমানবাহিনীতে ১,৬৩৬ জন এবং নৌবাহিনীতে ৭৪৮ জন। ছেলে নয়, মেয়ে নয়... সৈন্য। ‘ফাইটার’। এটাই তাঁদের পরিচয়।
সুপ্রিয় দেবরায়, বরোদা, গুজরাত
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)