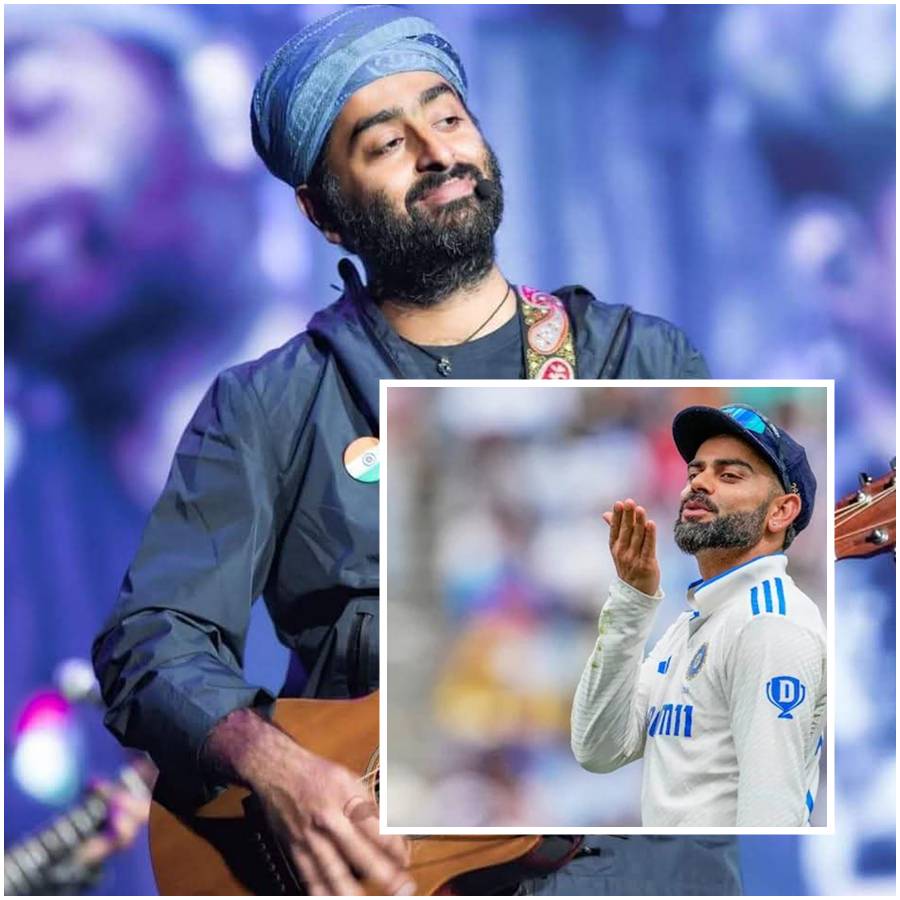স্বাতী ভট্টাচার্যের ‘ঠায় দাঁড়িয়ে দশ ঘণ্টা’ (৩-৫) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। শ্রম আইনে আট ঘণ্টা কাজের বিধি অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থায় মানা হয় না। শপিং মলের রক্ষী, বহুজাতিক কোম্পানির প্যাকিং কর্মী, চটকল শ্রমিক প্রমুখ দশ-বারো ঘণ্টা একটানা দাঁড়িয়েই কাজ করেন। এঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে মালিকপক্ষ উদাসীন। এমনকি এই কর্মীরা শৌচালয়ে বা অন্য কোথাও কিছু ক্ষণের জন্য গেলেও মালিকের বিরাগভাজন হন। অথচ, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের শিরা ফুলে, জড়িয়ে জটিল রোগ হতে পারে। শৌচালয় ব্যবহার না করার ফলে মূত্রথলির উপর চাপ পড়ে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
শ্রম কোডে কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা বা ন্যূনতম মজুরির বিষয় বলা হলেও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়নি। ইটভাটায় ঠিকাদারের অধীনে মহিলা শ্রমিকদের তো নথিভুক্তই করা হয় না। অথচ তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথায় ইটের বোঝা নিয়ে কাজ করে চলেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অলীক কল্পনামাত্র। তামিলনাড়ু ও কেরলের বিধানসভায় বিশেষ শ্রম আইনবলে যেখানে কর্মীদের বসতে না দিলে শাস্তির বিধান আছে, সেখানে আমাদের রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসক দল মুখে অনেক জনদরদি কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তেমন আইন বলবৎ করেনি। কলকাতার নামকরা হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় দেখেছি, নার্সদের বারো ঘণ্টা ডিউটিতে কোনও বসার চেয়ার নেই! শুধু হল-এ লম্বা টেবিল আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে লেখালিখি করা যাবে বা ফাইল রাখা যাবে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত অমানবিক মনে হয়েছে।
আমার এক আত্মীয়া প্রথমে ছাঁট কাপড়ের স্টোরে কাজ করার সময়ে গুড়ি সুতো বা তুলোয় ফুসফুসে সংক্রমণ হওয়ার কারণে সে কাজ ছেড়ে নামকরা রেডিমেড পোশাকের স্টোরে কাজ নিয়েছে। ফ্যাক্টরি থেকে আসা পোশাকে কোনও খুঁত আছে কি না, সেটা দেখাই তাঁর কাজ। সেখানে তাঁকে দশ-এগারো ঘণ্টা দাঁড়িয়েই কাজ করতে হয়, বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে কোমর, শিরদাঁড়ায় ব্যথা শুরু হয়েছে। চেয়ার না দেওয়ার এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এখনই রাজ্য সরকারকে বিশেষ আইন চালু করার দাবি জানাচ্ছি।
শিখা সেনগুপ্ত, বিরাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
অবিচার
“‘মা, চুরি করিনি’, সিসি ক্যামেরাতেও দেখা গেল সেই সত্য” (২৪-৫) শীর্ষক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। ছোট্ট কৃষ্ণেন্দু চলমান সমাজব্যবস্থার মুখে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছে। অপবাদ, অমূলক সন্দেহ, অহেতুক দোষী সাব্যস্ত করা, এই সব সামাজিক ব্যাধি যে আজ মহামারির আকার ধারণ করেছে, সে কথা ভাবার অবকাশ নেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলা এই সময়ের। বছর চোদ্দোর এক কিশোরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগটুকুও না দিয়ে তার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করা হল। অতটুকু বয়সে নিজেকে সামলে নেওয়ার দমটুকুও ছিল না ওর। ফলে আত্মহননের পথটাই উপযুক্ত মনে করেছে সে।
ভাবলে অবাক লাগে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর জনরোষ আছড়ে পড়েছে অভিযুক্তের পরিবারের উপর। অথচ যখন ঘটনা ঘটল, তখন এই নাগরিকরা কি শীতঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন? অকুস্থলে কৃষ্ণেন্দুর মা এসে ছেলেকে মেরেছেন। তখনও কি অবকাশ ছিল না, সত্য উন্মোচনে সক্রিয় হওয়ার? না কি সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, ওই ছেলেটাই চুরি করেছে। প্রতি দিন চুরি হয়ে যায় জঙ্গলের অধিকার, হাজার হাজার একর কৃষিজমি রাতারাতি গ্রাস করে নেয় শিল্পদানব, নগরায়ণের চক্করে প্রান্তিক মানুষ বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটাও হারিয়ে রিক্ত হয়ে যায়, বনভূমিকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানানো জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ চলমান সমাজব্যবস্থায় ক্রমশ অপাঙ্ক্তেয় হয়ে যান। প্রশস্ত সুসজ্জিত রাজপথের নাগরিক সুখবিলাসে বর্ণহীন পথবাসীর জীবনযাপন আড়াল করার কত না কৌশল! সেখানে কৃষ্ণেন্দুর মতো ফুলগুলো ঝরে পড়লে কী আর আসে যায়? আমাদের মনন, চিন্তন, বোধের সমষ্টিও একরত্তি কিশোরটিকে বাঁচাতে অক্ষম, এর চেয়ে হতাশার আর কী থাকতে পারে? চেতনার এই যে অবনমন, যা ধীরে ধীরে ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে গোটা সমাজে, সে বিষয়েও ভাবতে ভুলে গেছি আমরা।
পথের পাঁচালী-র দুর্গা প্রমাণ করতে পারেনি যে, সে চোর নয়। তেমনই কৃষ্ণেন্দুর কথাটাও কেউ বিশ্বাস করেনি। দুর্গার অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবারের যে মর্মান্তিক বর্ণনা বিভূতিভূষণ দিয়েছেন, তৎকালীন সমাজব্যবস্থা থেকে অত্যাধুনিক এই সমাজ তার কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে? সংযমী হতে পেরেছি কি আমরা? যাঁরা সেই অকুস্থলে ছিলেন, নীরবে সমর্থন দিয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ঘটনায়, তাঁরাও কি তাঁদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব সময় সততার পরিচয় দেন? অবশ্যই না। কোনও মানুষ একশো শতাংশ সৎ এমন ভাবনাটাই অমূলক। তবুও প্রায়শই বাজারহাটে চোখে পড়ে, চোর সন্দেহে এক দল জনতা পিটিয়ে যাচ্ছে কোনও এক জনকে। আর সেই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে আর এক দল জনতা। এটা কোন সভ্যতা? এ কোন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে মানবতা? সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে চাকরি চুরি, ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ না করে বিদেশে পলায়ন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের গৃহ থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, চিটফান্ড নামক কৃষ্ণগহ্বর বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ফেরার চিটফান্ডের মালিক— ইত্যাদি সংবাদ। আর অন্য দিকে স্রেফ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গণপিটুনিতে প্রাণ জেরবারের খবর।
অদ্ভুত সমান্তরাল সমাজে বাস করছি আমরা।
রাজা বাগচী, গুপ্তিপাড়া, হুগলি
সীমারেখা
‘মা, আমি চুরি করিনি, লিখে গেল ছেলে’ (২৩-৫) শীর্ষক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়াতে একটি তরতাজা কিশোরের জীবন অকালে চলে গেল চিপস-এর প্যাকেটের জন্য। এক সিভিক ভলান্টিয়ার যে ভাবে চুরির অপবাদ দিয়ে সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া কৃষ্ণেন্দু দাসকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে নির্যাতন করেছেন, তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বর্তমান সমাজে প্রচুর মানুষের অর্থ, চাকরি থেকে শুরু করে আরও নানা ধরনের মূল্যবান জিনিস প্রতিনিয়ত চুরি হয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর প্রশাসনকে আবেদন-নিবেদন জানিয়েও কোনও রকমের সুরাহা হয়নি। সেখানে দাঁড়িয়ে সামান্য কিছু টাকার চিপস-এর জন্য একটি শিশুকে আত্মহত্যা করতে হল, এটি মর্মান্তিক।
এই ঘটনার দায় কার, সেটি যত শীঘ্র সম্ভব প্রশাসনকে নির্ধারণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ রকম কোনও ঘটনা না ঘটে— সেটিও প্রশাসনকেই নিশ্চিত করতে হবে। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। রাজ্যে বিভিন্ন কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী কাজ, সেটি সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অথচ, হামেশাই দেখা যায় তাঁরা সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করে নানা ধরনের কাজ করে থাকেন, যেটি তাঁদের করার কথা নয়। আগামী দিনে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী কাজ করা উচিত আর কী করা উচিত নয়— সেই সম্পর্কিত একটি সীমারেখা বেঁধে দেওয়া উচিত প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের।
একই সঙ্গে, এক জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনের ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া নাগরিকদের সঙ্গে তাঁরা কেমন আচরণ করবেন, সেই ব্যাপারেও তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। আশা, এর মাধ্যমে আগামী দিনে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি অনেকটাই কমবে।
সুদীপ্ত দে, কলকাতা-১০২
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)