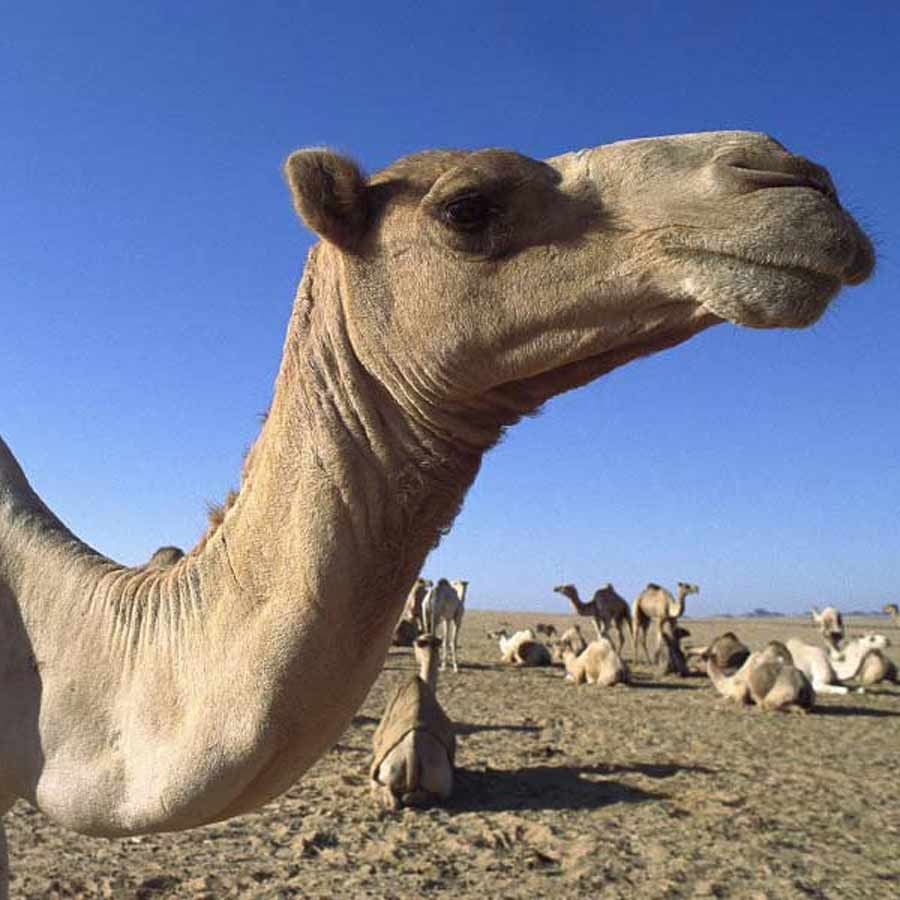দেবপ্রতিম চক্রবর্তীর ‘এক দুঃসহ আঁধার’ (৭-৪) প্রবন্ধ এক চরম অশুভ সময়ের কথা প্রকাশ্যে এনেছে। শিক্ষায় এত বড় আঘাত একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে গেল প্রায় ২৬ হাজার মানুষের চাকরি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় এত বড় নিয়োগ-দুর্নীতি অভূতপূর্ব। সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের ব্যপম কেলেঙ্কারিকেও পিছনে ফেলে দিল। যাঁরা চাকরি ‘কিনলেন’, অথবা যাঁরা যোগ্যতা দেখিয়ে নিয়োগ পেলেন, সকলেই বরখাস্ত। কিন্তু যাঁরা টাকা নিলেন সেই রাঘববোয়ালদের কিছুই হল না। হায় রে গণতন্ত্র!
এই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগ-দুর্নীতির ঠিক বিচার হলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে, তাই কি তদন্তের খবর সে ভাবে আর প্রকাশ্যে এল না? আর এই একের পর এক দুর্নীতির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করার মাধ্যমে করদাতাদের দেওয়া কোটি কোটি টাকা যে খরচ করা হচ্ছে, সেটাও কি ঠিক হচ্ছে? আবাস দুর্নীতি থেকে খাদ্য, নিয়োগ এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে, সর্বত্র টাকা দিতে হবে ভাল পরিমাণে— সেই ট্র্যাডিশন চলছেই। এত দুর্নীতির জোয়ার দেখেও নাগরিক সমাজ চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কষে আজ নীরব হয়ে বসে আছে। শিক্ষক-আন্দোলন আগের মতো দানা বাঁধে না। কারণ, বাদ সাধে হুমকি-সংস্কৃতি— “বদলি করে দেব গ্রামীণ স্কুলে!” বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ থেকে দূষিত স্যালাইন, টাকা দিয়ে ভর্তি এ সব চলছিল রমরমিয়ে। আর জি কর কাণ্ডের পর এ সব মানুষের গোচরে এসেছে। এক দিকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনার পরিকাঠামো দিন দিন বিলীন হচ্ছে, অন্য দিকে বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবসার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। এ রকম চলতে থাকলে দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের ছেলেমেয়েদের কাছে কি শিক্ষা তবে অধরাই থেকে যাবে?
দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা
দায় নিন
দেবপ্রতিম চক্রবর্তীর ‘এক দুঃসহ আঁধার’ প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, সরকারের অবিবেচনা, অপরিণামদর্শিতা ও সেই সঙ্গে প্রশাসনের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিদের সীমাহীন অর্থলোলুপতায় আজ বিপন্ন হাজার হাজার শিক্ষক ও তাঁদের নির্দোষ পরিবার। এর দায় তো প্রশাসনের উপরেই বর্তায়। আজ নেতা মন্ত্রী ও শিক্ষাজগতের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের অনিয়ম প্রকাশ্যে রাজ্যবাসীর কাছে ধরা পড়েছে, তার ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের জীবনে আচমকা অন্ধকার নেমে এসেছে।
প্রশাসনকে বলব, “কোথাও সামান্য দু’-একটা ভুল হয়ে গিয়েছে” বলে সাফাই না গেয়ে ঘটনার দায় স্বীকার করাই সমীচীন। শোনা যায়, কলিঙ্গ যুদ্ধের শেষে বিপুল রক্তক্ষয় দেখে সম্রাট অশোক নতমস্তকে স্বীকার করেছিলেন এই রক্তস্রোতের দায় তাঁর। তার পর তিনি অন্য চেহারায় প্রজাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। আজ প্রশাসন যদি সব জেনেশুনেও সব দোষ অন্যদের ঘাড়ে চাপায় তা হলে সেটা হবে চরম ভুল, যার খেসারত হয়তো এক দিন তাদেরই দিতে হবে।
সমীর কুমার ঘোষ, কলকাতা-৬৫
চাকরির বিপণি
‘এক দুঃসহ আঁধার’ প্রবন্ধটিতে মনোরঞ্জক স্বপ্ন ফেরি করে ক্ষমতায় আসার পর সরকারের মান-অবনমনের চিত্র নিঁখুত ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শীর্ষ ন্যায়ালয়ের আদেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগে এক লপ্তে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বাঙালি হিসাবে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। দুর্লভ সরকারি চাকরির বাজারে ফিসফিস করে চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল— চাকরি আছে, লাগলে বলবেন। জমি, গয়না, লাঙল, বলদ বিক্রি করে শিক্ষিত বেকারেরা উপযুক্ত জায়গায় টাকা পৌঁছে দিয়েছিলেন, ঠিক যে কায়দায় ঘুষ দিয়ে রেলের টিকিট কনফার্ম করা থেকে হাসপাতালের বেড বুকিং সর্বত্রই আমজনতা প্রতিনিয়ত কার্যসিদ্ধি হতে দেখতে অভ্যস্ত। প্রশ্ন হল, শিক্ষকের চাকরি বিক্রয় এবং পূর্বোক্ত দুর্নীতি কি এক গোত্রভুক্ত হতে পারে? শত শত যোগ্য শিক্ষককে পথে বসিয়ে, অযোগ্যদের শিক্ষকতার চাকরি ছিনিয়ে নেওয়া এক ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ। এর অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। এবং এই অপরাধের কুশীলবদের যেখানে ঘৃণ্য অপরাধী হিসাবে কারাগারে পাঠানো উচিত, তাঁদের প্রশ্রয়দাতাদের যখন নৈতিক দায় স্বীকার করা কর্তব্য, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে বিরোধী দল বা বিচারব্যবস্থার দিকে দোষারোপ করতে দেখা গেল প্রশাসনকে।
পানীয় জলের লাইন থেকে নিকাশির লাইন আলাদা করাই তো প্রশাসনের দায়িত্ব, চাল থেকে কাঁকর বেছে নিতে তারা এত নিস্পৃহ কেন? দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অগোচরে এত বড় মাপের দুর্নীতি ঘটে যাওয়ার তত্ত্ব মেনে নিতে আজ অনেকেই রাজি নন। তার উপরে শিক্ষা দফতরের প্রধান মুখকে যখন এ নিয়ে সাফাই দিতে দেখা যায় তখন অন্দরের অলীক কুনাট্য চোখ কাড়ে।
কৌশিক বসু আনন্দবাজার পত্রিকার শতবর্ষের ক্রোড়পত্রে ‘শিক্ষাই উন্নয়নের পথ’ (১৮-৩-২২) প্রবন্ধে লিখেছিলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার স্কুল শিক্ষকদের মাইনে দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশের চাইতে বেশি। এই বেশি মাইনের কারণে ভাল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকতার পেশায় আসেন এবং তার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম পায়। স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল হলে এই যে এক প্রজন্মের গণ্ডি ছাপিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার সুফল পৌঁছে যায়, অর্থনীতির ভাষায় একে পজ়িটিভ এক্সটার্নালিটি বা ইতিবাচক অতিক্রিয়া বলা হয়। শিক্ষকদের ইতিবাচক অতিক্রিয়ার মূল্য যদি সরকার ঠিকঠাক দিতে পারে, তা হলে তার সুফল কিন্তু হবে সুদূরপ্রসারী, যুগান্তকারী।
কিন্তু বর্তমানে তো এ রাজ্যের শিক্ষকদের ভাগ্যে বরাদ্দ হয়েছে নেতিবাচক অতিক্রিয়া। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে এর কুফল সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চান, অযোগ্য শিক্ষক স্কুল চৌহদ্দির বাইরে থাকুন। যোগ্য শিক্ষক মাথা উঁচু করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।
রাজশেখর দাস, কলকাতা-১২২
মুক্তি চাই
দেবপ্রতিম চক্রবর্তীর ‘এক দুঃসহ আঁধার’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। প্রথমত, জনসমর্থনের বিষয়টি বিচার করলে দেখা যাবে, নানা ভাবে জনসাধারণকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে জনসমর্থন আদায় করা চলছে। দুর্বৃত্ত পাঠিয়ে ভয় দেখানোর প্রবণতাও রয়েছে। এই ভাবে জনসমর্থন আদায় করে নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়ার কু-প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখা গিয়েছে। পথেঘাটে কথা বললেই জানা যায়, সমাজের বড় অংশ কিন্তু প্রশাসনের নৈতিক অবনমন ও সামগ্রিক কাজকর্মে বেশ বিরক্ত। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদের সাহস দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন না। তবুও শাসকের জনসমর্থন কিন্তু ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, এক কালে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ‘সততা’ শব্দটির তার প্রয়োগ বাস্তবে সে ভাবে হয়নি। তৃতীয়ত, রাজ্যের মানুষ খুব একটা উগ্র মনোভাবাপন্ন নন। যোগ্য সরকারি আধিকারিক এবং অন্যান্য সহযোগিতা না পেলে এই দুর্নীতিগ্রস্তদের হাত থেকে তাঁদের রেহাই পাওয়া খুবই দুষ্কর।
সুব্রত সেনগুপ্ত, কলকাতা-১০৪
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)