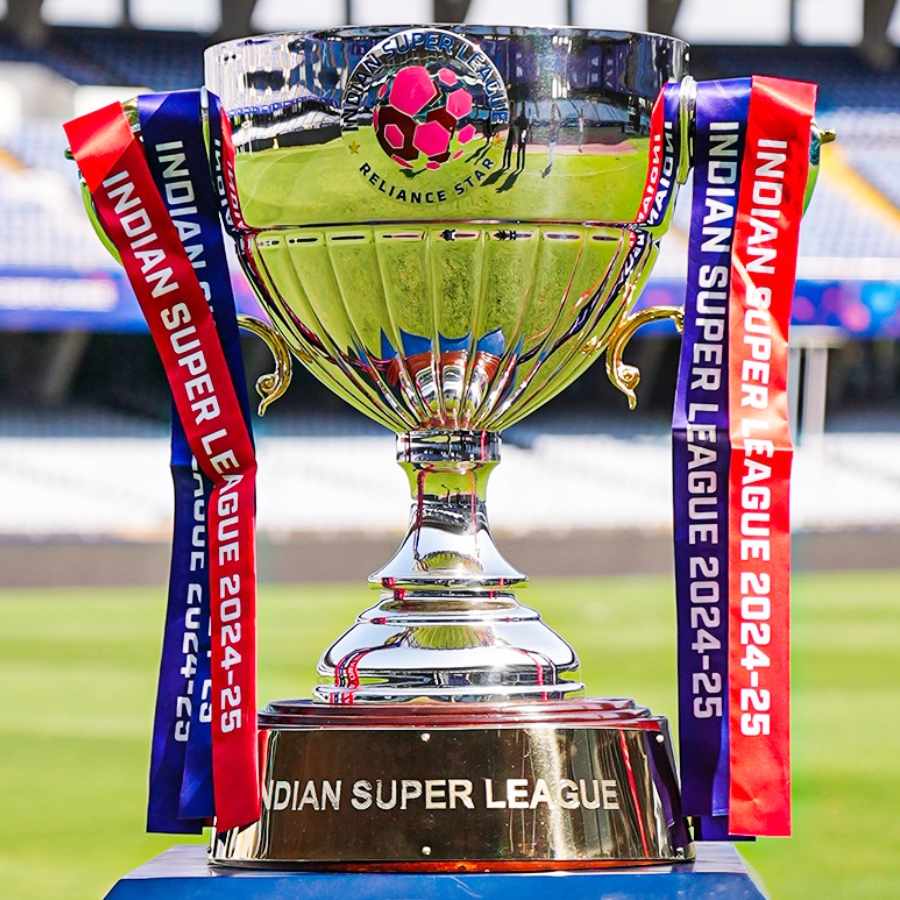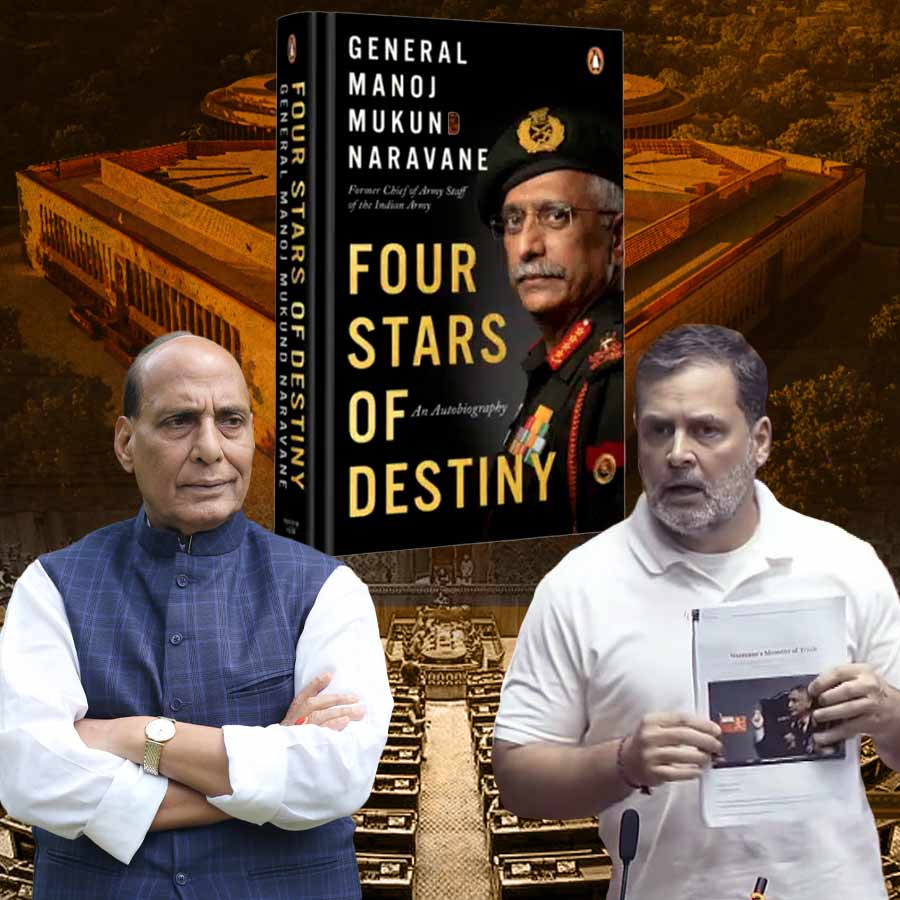জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের “‘বেছে নেওয়া’র হিসাব” (২৯-৪) শীর্ষক সময়োপযোগী প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা। খুব সঙ্গত কারণেই প্রবন্ধকার এমন অনেক সত্যি কথা এখানে বলেছেন, যা সাধারণত তথাকথিত প্রগতিশীলদের মুখে শোনা যায় না। যেমন, তিনি বলেছেন, “ইসলাম মানেই সন্ত্রাস নয় বা সন্ত্রাস মানেই ইসলাম নয়, এটা মনে করিয়ে দিতেও কিন্তু ইসলামি জঙ্গিবাদকে ‘ইসলামি জঙ্গিবাদ’ বলে ডাকার প্রয়োজন আছে।” এবং এর কারণ হিসাবে খুব সুন্দর একটা যুক্তিও তিনি দিয়েছেন, “এই শব্দবন্ধ দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব, ইসলাম একটা আলাদা শব্দ। ইসলামি জঙ্গিবাদ আলাদা। ঠিক যেমন, হিন্দু একটা শব্দ। হিন্দুত্ববাদ একেবারে আলাদা।”
তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নিরীহ, নিরপরাধ কোনও মানুষ যদি অন্যায় ভাবে আক্রান্ত হন বা সমস্যায় পড়েন, তবে তাঁর বা তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এক বিষয়, আর শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষের কিছু অংশের অন্যায়কে মেনে নেওয়ার বিষয়টি একেবারে অন্য। প্রথম পক্ষাবলম্বনটা যদি ‘বিপদে পাশে দাঁড়ানো’ বোঝায়, পরেরটা কিন্তু অবধারিত ভাবেই পক্ষপাতদুষ্টতার একটি উদাহরণ হিসাবে গণ্য হবে। এবং এই পক্ষপাতদুষ্টতার নিদর্শন যত বাড়বে, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিও তত বেশি পর্যুদস্ত হবে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ এই শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে ‘নিরপেক্ষতা’। সুতরাং, কোনও বিশেষ ধর্মের লোকের অন্যায় আচরণে কেউ যদি নীরব থাকেন, তবে তার একটাই অর্থ, তিনি ‘নিরপেক্ষ’ অবস্থান নিতে ব্যর্থ।
হিন্দু ধর্মের কেউ যদি কোনও অন্য ধর্মের মানুষের প্রাণনাশের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে প্রমাণিত হন, তবে তাঁর জন্য যেমন সমগ্র হিন্দু জাতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অবিচার হবে, ঠিক সে রকম ভাবে, একই ধরনের অপরাধের কারণে সম্পূর্ণ ভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেদের দোষী রূপে চিহ্নিত করাটাও অন্যায় কাজ রূপেই পরিগণিত হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিককে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলগুলো যদি সমদৃষ্টিতে দেখে, তা হলে এক দিকে যেমন পারস্পরিক ধর্মীয় বিদ্বেষ অনেকটা কমানো যায়, অন্য দিকে তাদের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে একটা সদর্থক বার্তা দেওয়াও সম্ভব হয়। বাছাই করা ধর্মনিরপেক্ষতা বা ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে আর যা-ই হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সম্মান জানানো যায় না। আর সেই কারণে, তাঁর উদ্দেশে আক্রমণকেও ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য উভয় ধর্মের কট্টরবাদীরা যতটা নিন্দনীয়, কোনও রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কট্টরবাদীদের কৃত অন্যায় উপেক্ষা করার জন্য উদারবাদীরা ঠিক ততটাই দোষী। কোদালকে কোদাল বললে ভোটব্যাঙ্কের হিসাবে হয়তো কিছু গরমিল দেখা দিতে পারে, কিন্তু, দিনের শেষে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ই জয়ী হবে। এই কথা হলফ করে বলে দেওয়া যায়।
গৌতম নারায়ণ দেব, কলকাতা-৭৪
উত্তর মেলে না
জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের “‘বেছে নেওয়া’র হিসাব” প্রবন্ধটি সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা। সেকুলার ও উদারবাদীদের উপর ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা যে আক্রমণ নামিয়ে আনছেন, তার বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য লেখককে ধন্যবাদ। আমার মতে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ধর্মের পরিচয়কে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে একটা মূল বিষয় আড়ালে চলে যাচ্ছে। এই ধর্মীয় মৌলবাদের উৎস ধর্মীয় অন্ধতা হলেও সেই মৌলবাদী ভাবনাকে ভিত্তি করে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে চলেছে, কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, দেশে দেশে যাঁরা শাসনক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরা। কে না জানে, সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন ঠিক কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি? পূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলিতে সন্ত্রাসবাদীদের সব রকমের সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করছে কারা? সাম্রাজ্যবাদীরাই নয় কি? আজ পাকিস্তানে মুসলিম মৌলবাদ ও ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের মদত দিচ্ছে কারা? দেশের সাধারণ জনগণ, না কি প্রশাসনেরই অংশবিশেষ? এর উদ্দেশ্য বুঝতে খুব অসুবিধা হয় কি? মেহনতি মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরানোর প্রয়োজন কার? শাসকশ্রেণির নয় কি? তাই সন্ত্রাসবাদী হামলাকে নিন্দা করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ধর্মবিশ্বাস এবং নিহত মানুষদের ধর্মবিশ্বাসকে বড় করে দেখলে আসলে লাভ হয় শাসকশ্রেণির। তাই তো সরকারি মদতে রামনবমীর উন্মাদনা সৃষ্টির মধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে গেল; বিভাজন সৃষ্টিকারী বিলের সংশোধনী আইন প্রণয়নের আবহেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতে পেট্রল-ডিজ়েলের দাম বেড়ে গেল। লেখক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ের যোগাযোগের পক্ষে বলতে গিয়ে হিটলারের উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু হিটলারও যে ইহুদি নিধন শুরু করেছিলেন, তার কারণ কী ছিল? তাঁর প্রয়োজন ছিল দেশের মানুষের মধ্যে অন্ধ ও উগ্র উন্মাদনা সৃষ্টির। তার জন্যই তাঁর একটা বিশেষ অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। ইহুদি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি ছিল সেই অবলম্বন।
যতই জবাব দেওয়া নিয়ে আস্ফালন করে নজর ঘোরানো হোক, সংশয়গুলো থেকেই যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত নিশ্ছিদ্র সেনাবলয়ের মধ্যে জঙ্গিরা এত সহজে ঢুকতে পারল কী করে? ঘটনার পরেও সেনার আসতে দেরি হল কেন? গোয়েন্দারা কী করছিলেন? জঙ্গিদের গতিবিধি তাঁরা জানতে পারলেন না কেন? প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার জন্যই তাঁরা সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে দিয়েছেন। তা হলে সন্ত্রাসবাদীরা এল কোথা থেকে? এই সব অপ্রিয় প্রশ্ন থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই কি প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির কথা এড়িয়ে গিয়ে প্রত্যাঘাতের হুঙ্কার তুললেন? তৃতীয়ত, সন্ত্রাস-কবলিত মানুষদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কারা? ধর্মীয় পরিচয়ে তাঁরা মুসলিম মানুষ নন কি? তা হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সব মানুষকেই সন্ত্রাসবাদী বলে দেগে দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, তা কি ঠিক এবং নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য? চতুর্থত, এই ঘটনা পরম্পরায় সবচেয়ে ক্ষতি হল কার? কাশ্মীরের জনসাধারণের রুটিরুজির সঙ্গে যে পর্যটন শিল্পের ওতপ্রোত সম্পর্ক, সেই পর্যটন শিল্পের উপরে আঘাত করে আখেরে লাভ হল কার? যাঁরা প্রকাশ্যে বলেন, ওই সম্প্রদায়ের এ দেশে থাকার অধিকার নেই, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন হল না কি?
তা হলে আজ যে এক দল মানুষ তারস্বরে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, সেটা মেনে নেওয়া যায়? সেকুলার ও উদারবাদীদের বিরুদ্ধে যাঁরা বিষোদ্গার করছেন, পেট্রল ডিজ়েল ও গ্যাসের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কি তাঁরা একটা শব্দও উচ্চারণ করেছেন? তা হলে তাঁরা কাদের উপকার করছেন? কর্মসংস্থান শূন্যের কোঠায়। মানুষের জীবন রক্ষা করা যখন যন্ত্রণাময়, তখন সীমান্তে গোলাগুলি আছড়ানোটাই কি বড়? আদানি-অম্বানীর পুঁজির পাহাড় আকাশ ছুঁয়েছে। অথচ সাধারণ মানুষের করের টাকা দিয়ে তাঁদের লক্ষ-কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কোনও কথা নেই কেন?
সুব্রত গৌড়ী, কলকাতা-১২
এত ক্রোধ!
জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের “‘বেছে নেওয়া’র হিসাব” প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর অন্য মুসলিম প্রধান দেশগুলিতেও সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের মাত্রা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার হয়, তার চেয়েও বেশি। তবু সেখানে সেই সংখ্যালঘুদের কিছু অংশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ বা প্রবল উষ্মা এত প্রবল নয়। এখানেই এমন অবস্থা কেন, কাদের জন্য?
অতনু পাল, আমতা, হাওড়া
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)