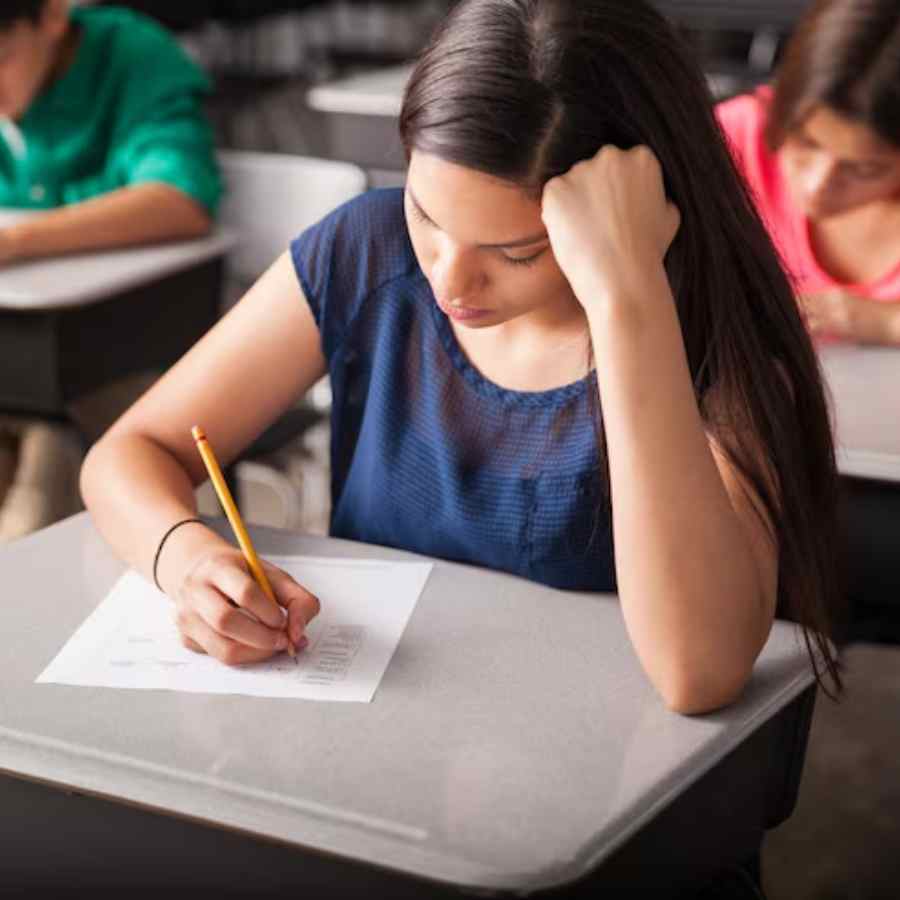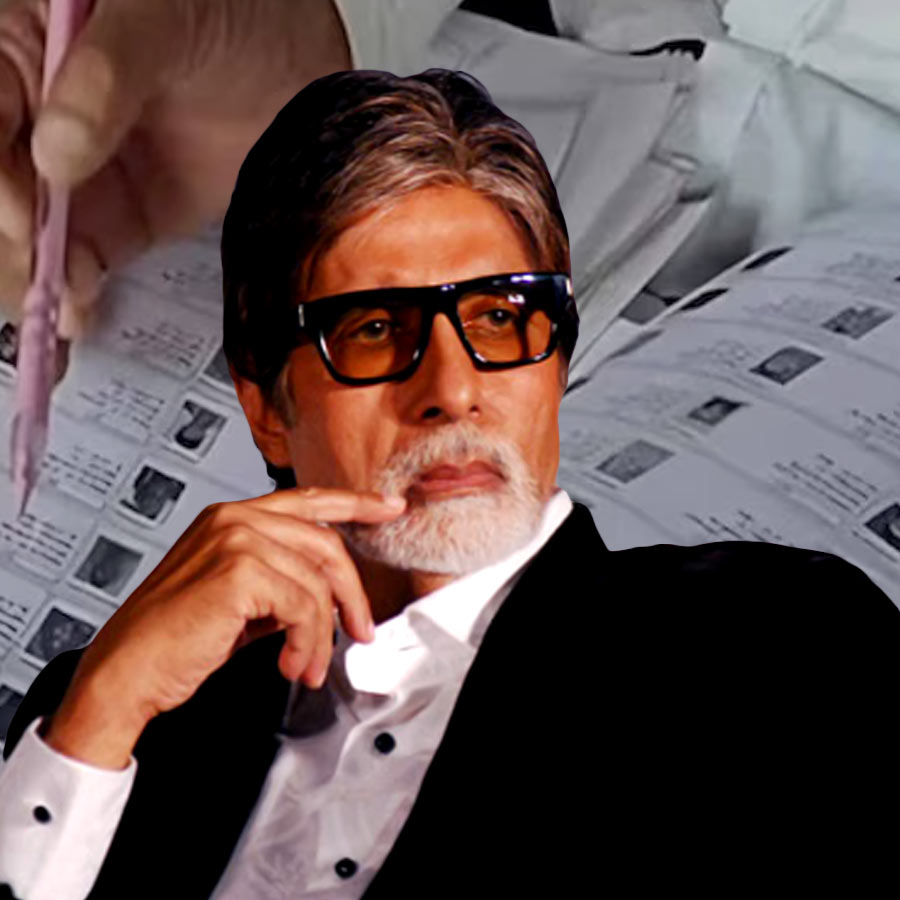ভোটের সময়টা অদ্ভুত। কত কিছু সামনে আসে। আবার কত কিছু পিছনে মিলিয়ে যায়। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, কয়েক দিন আগে রাফাল চুক্তি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে কথাগুলি বলল, অত্যন্ত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো হারিয়ে যেতেই বসেছে। অথচ এরই ভিত্তিতে রাফাল চুক্তি বিতর্কের গুরুত্ব অনেকটা বাড়তে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাফাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে নেহাত নিয়মমাফিক ভোট-তরজার বিষয়— যার গুরুত্ব কেবলই ক্ষণিক, যার দাম আপাতত চড়া হলেও ক্রমশ বিলীয়মান। ভোটের বাজারে রাফাল নামটা বার বার শোনা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে সব খালি উপর-উপর চাপানউতোর। কথার প্যাঁচে কে কাকে বিপদে ফেলতে পারে তার প্রতিযোগিতা। নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য, সর্বোচ্চ আদালত তাঁদের ‘ক্লিন চিট’ দিয়ে দিয়েছে। আর রাহুল গাঁধীর বক্তব্য, সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তেই বোঝা গিয়েছে ‘চৌকিদার চোর হ্যায়’। কংগ্রেস বলছে, মোদী ডাহা মিথ্যে বলছেন, আর বিজেপির মীনাক্ষী লেখি-রা বলছেন, বিচারকদের মুখে ভুল কথা বসিয়ে রাহুল আদালত অবমাননা করছেন। হইচই ঝগড়াঝাঁটি। এইটুকুই কি সুপ্রিম কোর্টের বার্তার ভবিতব্য ছিল?
দুর্ভাগ্য। গত কয়েক বছরে সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য মাইলফলক-রায়ের মতো রাফাল-সংক্রান্ত বার্তাটিরও সম্ভাবনা ছিল, ভারতীয় গণতন্ত্রের ‘ডিফাইনিং’ বা সংজ্ঞাত্মক মুহূর্ত হয়ে ওঠার। ভারত ঠিক কী রকম দেশ, সেই মৌলিক চরিত্রটিকে মনে করানোর মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার।
পুরো ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে ‘দ্য হিন্দু’ সংবাদপত্রে কিছু গোপন সরকারি নথির ভিত্তিতে প্রকাশিত রাফাল বিমান কেনার পদ্ধতি নিয়ে পর পর পাঁচটি রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার যে, ফরাসি কোম্পানির কাছ থেকে রাফাল বিমান কেনা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ছিল গুরুতর আপত্তি। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা দফতরের অসম্মতি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অভিযোগের তির সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের দিকে। বর্তমান সরকারে যে মন্ত্রক ও দফতরগুলির কোনও মূল্য নেই, সমস্ত রকম সরকারি কাজকর্মই যে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুড়ির নির্দেশে চলে, এই অভিযোগ অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। উপরের রিপোর্টগুলি তাই সঙ্গে সঙ্গেই রাহুল গাঁধীদের প্রচারেও একটা নতুন অক্সিজেন এনে দেয়। স্বভাবতই, সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে আসে সরকারের সাঁড়াশি আক্রমণ।
দিল্লি দখলের লড়াই, লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র প্রসঙ্গ তুলে পাল্টা যুক্তি দেন— এই সাংবাদিকতা অনৈতিক, কেননা, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে এত গোপন ও গভীর ভাবে যুক্ত তথ্য নিয়ে সংবাদ এ ভাবে প্রকাশ করা যায় না। আদালতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালও বললেন যে, এই সংবাদপত্র ভারতের অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট (ওএসএ) অমান্য করেছে। বেণুগোপালের মুখেই ধ্বনিত হল দ্বিতীয় অভিযোগ: যে নথির ভিত্তিতে এই তথ্য প্রকাশ, সেই নথিটি সরকারের কাছ থেকে ‘চুরি’ করা হয়েছে। প্রথমত আইন অমান্য, এবং দ্বিতীয়ত চুরি— দুই দিক দিয়ে আক্রমণ। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা কিন্তু সরকারি যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বললেন যে, রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি সংক্রান্ত যা রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে ‘প্রমাণ’ হিসেবে গ্রাহ্য করতে কোনওই অসুবিধে নেই। বললেন, ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র জন্য তথ্যের অধিকার (রাইট টু ইনফর্মেশন) আর মতপ্রকাশের অধিকার (ফ্রিডম অব স্পিচ)— এই দু’টিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।
ওএসএ বিষয়ে এমন কথা বলা কিন্তু সহজ ছিল না। ব্রিটিশ আমলের এই আইনটি গুপ্তচর-বিরোধিতার কাজে ব্যবহৃত হত, ফলত এই আইন অমান্যের অপরাধটিও খুবই বড় মাপের বলে গণ্য হত। অপরাধ প্রমাণিত হলে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হত। স্বাধীন ভারতেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আইন অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে। দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলি অনেক দিন ধরেই এই আইনের বিরুদ্ধে সরব। অর্থাৎ সিডিশন বা দেশদ্রোহ আইনের মতোই, ওএসএ বা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনটিও কতখানি স্বাধীন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত, এর ভিত্তিতে শাস্তিদানই বা কতখানি সঙ্গত— তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকারের ‘জাতীয়তাবাদ’-প্রেম কেবল সিডিশন আইনটিকেই ফিরিয়ে আনেনি, ওএসএ-কেও জনসমক্ষে নিয়ে এল রাফাল-এর সূত্রে। এবং সুপ্রিম কোর্টের জন্যই— আরও এক বার— সরকারের সেই স্পর্ধাকে প্রতিহত করা গেল।
কেবল রাফাল মামলাই তো নয়। গত কয়েক বছর ধরে প্রচারমাধ্যমের উপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ চলেছে, তাতে এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পাল্টেছে প্রভূত পরিমাণে— এই নির্বাচনী মরসুমে সেটা আর আলাদা করে বলার দরকার নেই। এই আক্রমণেরও একটা সাঁড়াশি চরিত্র আছে। এক দিকে তা সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখে। অন্য দিকে তা লোভ দেখিয়ে নিজের সঙ্কীর্ণ আজেন্ডার মধ্যে টেনে নেয়। দুর্ভাগ্য যে, এ দেশের প্রচারমাধ্যমের একাংশও এই আক্রমণের সামনে মোটেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, হয় ভয়ে, নয় লোভে আত্মসমর্পণ করেছে।
সাম্প্রতিক রাফাল-সংবাদপত্র-সুপ্রিম কোর্ট ঘটনাটি সেই দিক দিয়েও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা হাঁপ ছাড়তে পারি যে আর কিছু না হোক, শুধু বিচারবিভাগের জন্যই অন্তত আরও কিছু দিন গণতন্ত্রে আস্থা রাখা যাবে। ভারতীয় সংবাদপত্র-জগৎ এবং সেই সূত্রে নাগরিক সমাজ আরও কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকবে যে, সর্বোচ্চ আদালত কঠিন পরীক্ষায় তাদের পাশে আছে। এবং, হয়তো, সেই আশ্বাসেই, এখনও কিছু সংবাদমাধ্যম নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষার সাহস দেখাতে পারবে।
কত যে ঐতিহাসিক আমাদের দেশের এই মুহূর্ত, তা ভাবতে গিয়ে তুলনা টানতে ইচ্ছে করছে উনিশশো সত্তর দশকের আমেরিকায় পেন্টাগন পেপার্স নিয়ে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ এবং ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর সেই কঠিন পরীক্ষার সঙ্গে। কিংবা আরও সাম্প্রতিক অতীতে ব্রিটেনে উইকিলিকস-এর সূত্রে ‘দ্য গার্ডিয়ান’ সংবাদপত্রের হেনস্থার সঙ্গে। দু’টি ক্ষেত্রেই অসম্ভব কঠিন আইনি লড়াই হয়েছিল ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র সঙ্গে ‘বাক্স্বাধীনতা’র।
না, এই তুলনা টানা যে পুরোপুরি সঙ্গত নয়, তা স্বীকার করেই কথাটা বলছি। ভারতের ক্ষেত্রে রাফাল চুক্তি ঠিক কতখানি গভীরে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত— কেউ তা জানে না। কিন্তু উপর উপর জেনেই বলতে পারি, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার পেন্টাগন পেপার্স এবং ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী উইকিলিকস মোদী সরকারের রাফালের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মাত্রায় স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। এবং দু’টি ক্ষেত্রেই যে ভাবে, যে ভাষায় এবং যে সাহস ও ঝুঁকি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বাক্স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেছিলেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের সম্পাদক, প্রকাশক ও তাঁদের আইনজীবীরা, এবং অবশ্যই, বিচারপতিরা— গণতন্ত্রের ইতিহাস বইতে তা একটা আলাদা অধ্যায় দাবি করে। ‘ফ্রি প্রেস’ যে সন্দেহোর্ধ্ব ভাবে ‘ফ্রি সোসাইটি’র প্রথম স্তম্ভ, এটা বলা সহজ হলেও নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আদালতে তা দাবি করা আর এক জিনিস। ভারতে তেমন কোনও সুযোগই হয়নি।
এ প্রসঙ্গে অবশ্যই অন্য একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক অ্যালান রাসব্রিজার নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা সাম্প্রতিক সুপাঠ্য বইটিতে পড়লাম, পেন্টাগন পেপার্স-এর সময় যখন ভয়ঙ্কর নিরাপত্তা-ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে, অন্যতম মার্কিন বিচারক বলেছিলেন: ‘‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কেবল রাষ্ট্রীয় দুর্গের প্রাকার রক্ষার মধ্যে থাকে না, জাতীয় নিরাপত্তা থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতার মধ্যে।’’ বলেছিলেন, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, বাক্স্বাধীনতা রক্ষা এবং মানুষের জানার অধিকার রক্ষার খাতিরে তাঁদের সহ্য করতেই হবে সংবাদমাধ্যমের অত্যাচার (‘আ ক্যান্টাঙ্কারাস প্রেস, অ্যান অবস্টিনেট প্রেস, আ ইউবিকিটাস প্রেস’)! আমাদের দেশের বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফও রাফাল-সূত্রে বলেছেন, যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের ‘হায়েস্ট লেভেল অব প্রোবিটি’ বা ‘সর্বোচ্চ পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্যতা’ অর্জন করতেই হবে— সংবাদমাধ্যম এবং সমাজ লক্ষ রাখবে তাঁরা সেই অর্জনে পৌঁছলেন কি না।
অর্থাৎ বিচারবিভাগ— এ দেশেও— তাঁদের কাজ করে চলেছে। কিন্তু বাকিরা নিজেদের কাজটা করছেন তো? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের একটা জরুরি দায় আছে, সেটা মনে করিয়ে দেওয়া, কিংবা সমস্ত ক্ষেত্রে বাক্স্বাধীনতার অধিকার, আর তথ্য জানার অধিকার দাবি করা কিন্তু প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। কেবল বিচারপতিদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না!