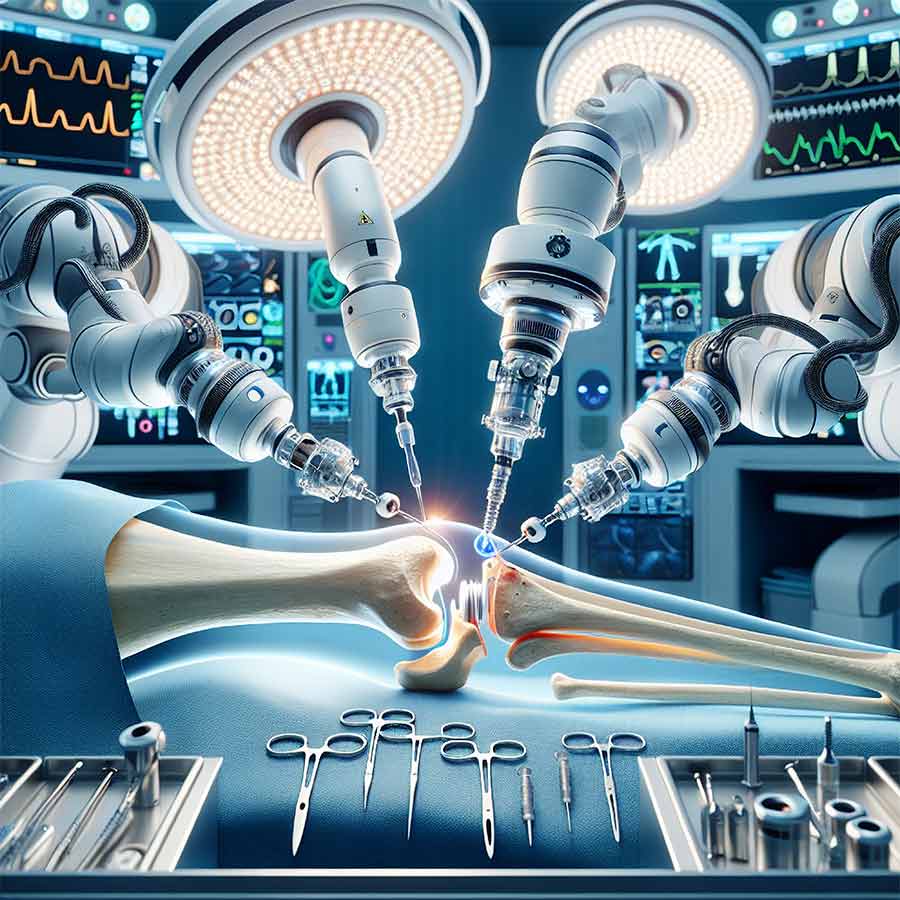‘স্বাধীনতা’ শব্দটির সঙ্গে গণতন্ত্রের ধারণা অবিচ্ছেদ্য বলেই আমাদের কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। ‘একনায়কতান্ত্রিক স্বাধীনতা’ ব্যাপারটা ঠিক ভেবে ওঠা মুশকিল। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যতই তার নাগরিকদের সম্পর্কে যত্নশীল হোক না কেন, তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মানুষ কিন্তু তার নিজস্ব মতপ্রকাশের, জীবনযাপনের অধিকার হারাতে চায় না, তার প্রচুর প্রমাণে ইতিহাস ভরা। নিজস্ব জীবনযাপনের এই যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, তার কারণ একটি দেশে নানা সমাজের মানুষ বাস করেন। জীবিকা বা পরিবেশগত কারণে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তা সময়ের সঙ্গে অবশ্যই পাল্টায়, কিন্তু ওপর থেকে চাপ দিয়ে এক রকমের জীবনযাপনে বাধ্য করা, এমনকী তাদের ‘কল্যাণার্থে’ হলেও, মানুষ বেশি দিন মেনে নেন না। সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক শর্ত তাই পরস্পরের মত ও জীবনযাপনকে সহ্য করে চলা। সেটা না হলে কারওরই নিজস্ব জীবনযাপনের অধিকার রক্ষিত হয় না।
আরও পড়ুন: দেখুন স্বাধীনতার প্রথম সকালের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলো
ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে কথিত, হতে পারে আমাদের জনসংখ্যা আমাদের এই গৌরব এনে দিয়েছে। এ দেশের সংবিধানে, যা সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানও, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয়, দার্শনিক, ভাষাভিত্তিক, সমস্ত রকম সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্ররক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। মেনে নেওয়া হয়েছে সকলের জীবিত থাকার, অর্থাৎ নিহত না হওয়ার, অসুস্থ না-হওয়ার, নিজগৃহে বাস করার অধিকার— এ রকম আরও বহু বুনিয়াদি মানবিক অধিকারকে আমাদের নাগরিক অধিকার হিসাবে। সেই হিসাবে আমরা সত্যিই গৌরব অনুভব করতে পারি। প্রতি বছর পনেরোই অগস্ট এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি দেশের প্রধান শাসকরা ‘জনসাধারণ’কে খুব বড় করে এ কথা মনে করিয়ে দেন। দেশ যে সদাসর্বদা নানা আক্রমণের বিপদের মধ্যে আছে, সে কথার সঙ্গে। সে-ও স্বাভাবিক। একশো কুড়ি কোটি নানা রকম অধিবাসীর দেশে অনেকেই বার বার বিস্মৃত হতে পারেন গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ।
গণতন্ত্রের আরও স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক জন চিন্তাশীল দার্শনিক। তাঁর মত ছিল, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কখনও গণতন্ত্রের স্বরূপ হতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণই যদি লক্ষ্য হয়, তা হলে কোনও পদক্ষেপ ঠিক কি না তা বিচারের মাপকাঠি হতে হবে সে কাজের দরুণ সমাজের সবচেয়ে নীচে থাকা মানুষটির কল্যাণ সাধিত হবে কি না। এই কথাটিই যে গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করে তা একটু ভাবলেই স্পষ্ট হয়। অধিকাংশ মূল্যবান চিন্তার মতোই এই কথাটিও বাস্তবে পালিত হতে দেখা যায়নি। দার্শনিক মত হিসাবে থাকতে থাকতেই অব্যবহারে ঝাপসা হয়ে আসছে।


বরং গত বেশ কিছু দিন যাবৎ আমাদের দেশে এক রকম ‘জবরদস্তির গণতন্ত্র’ দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রের প্রধান বা একমাত্র অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘নির্বাচনে জেতা’। অর্থাৎ, ‘ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল’। এই ক্ষমতা দখলের সঙ্গে রাষ্ট্রের, সমাজের বা নাগরিকের কল্যাণসাধনের সম্পর্ক বোঝা সহজ নয়। বিশেষত ইদানীং যখন নির্বাচনের অনেক আগে থেকে সারা দেশে উদ্বেগজনক ভাবে তরুণ প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর হিংসার মধ্যে টেনে আনা হয়, নির্বাচনে জেতার ক্ষেত্রে ‘নৈতিকতা’ কথাটি সম্পূর্ণ লুপ্তশব্দ বলে বিবেচিত হয়, এবম্বিধ প্রলয়কাণ্ডের পর বিজেতা ‘জনপ্রতিনিধি’রা প্রায় প্রকাশ্যে অর্থমূল্যে বিক্রি হয়ে দলবদল করেন ইত্যাদি। মূর্খ নাগরিকদের অনেকের সন্দেহ হয় যে দেশসেবা ছাড়াও কিছু অন্য স্বার্থ ‘জনপ্রতিনিধি’দের চালিত করে। এই বিপদের আশঙ্কা থাকে বলেই গণতন্ত্রের প্রবক্তারা নাগরিকদের অধিকার বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে বার বার সতর্ক করেন। কারণ গণতন্ত্রের মূল জোর হল নাগরিকদের নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকা।
সেই সক্রিয় সতর্কতার অভাব হলে যা হয়, সেটাই আমরা গত কিছু দিন যাবত প্রত্যক্ষ করছি। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের নীতি বা আদর্শের বালাই শিকেয় তুলে রেখে পরস্পরকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিগত কুৎসা করার স্তরে নামিয়ে এনেছে। ফলে সরকার পক্ষের সঙ্গে বিরোধীপক্ষের নীতিগত বা কার্যসূচিগত কোনও তফাৎ নেই। যে কোনও দলের সরকার যদি আসনে বসে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করার, ধ্বংস করার, দেশের পরিবেশ বা নাগরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনও শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কোনও বিরোধী পক্ষকেই সচরাচর তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে শোনা যায় না। ঝগড়াঝাঁটি চলে কেবল কে কোন কাজের থেকে নিজেদের পছন্দমত লোকদের কতো সুবিধা পাইয়ে দেবেন, তাই নিয়ে। এ ব্যাপারে সরকার পক্ষকেই অধিক দায় নিতে হবে কারণ তাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারী। বাস্তবে আমরা সত্রাসে লক্ষ্য করছি সরকার বা বিরোধী, কোনও পক্ষই দেশে গণতন্ত্রের বিপন্নতা সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কথা বলছেন না। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের যা প্রথম শর্ত, এ দেশে তা নিত্য লঙ্ঘিত হচ্ছে। এবং এই লঙ্ঘনকে প্রায় স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। মতপ্রকাশের এবং জীবনযাপনের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে প্রতি দিন। এমনকী, সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও কোনও পরোয়া না করে কিছু অপরাধী, সমাজবিরোধীর হাতে চলে যাচ্ছে অন্য রকম মানুষদের পীড়ন করার ক্ষমতা।
আরও পড়ুন: এক হননকালের মধ্যে বাস করছি যেন
পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা আমাদের স্বাভাবিক বাতাবরণ হয়ে উঠল। এটা একদিনে ঘটেনি। আমরা জানি, বিরোধী রাজনীতির স্বর স্তব্ধ করে দেওয়া আমাদের কাছাকাছিতেও চলেছে কয়েক দশক ধরে। সারা দেশে আজ তা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় এল যে ‘বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত’ হওয়াটা যে একটি বহুস্বর রাজনীতির দেশে লজ্জাজনক সেই বোধও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষ ক্রমশ ঢুকে পড়ছেন এমন এক ভয়ের বাতাবরণে, যা এক অসুস্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে। একদিকে বিপুল বেকার সমস্যা, কোটি কোটি মানুষ নিঃশব্দে নিজেদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে কোনও রকমে বুকে হেঁটে বাঁচছেন, অন্য দিকে রাজনীতির নামে সমাজে কালো টাকার অবাধ চলাচল— দুইয়ে মিলে সমাজকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে এক বেপরোয়া, অনৈতিক জীবনযাপনের কিনারে ঠেলে দিয়েছে। ফলে সমস্ত সমাজকে ছেয়ে ফেলছে এক অনিশ্চিতি, অকারণ প্রতিযোগিতা ও যে কোনও উপায়ে ‘এগিয়ে থাকা’র মানসিকতা। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহনশীল স্বাভাবিক সম্পর্কের বদলে প্রতি দিন সঞ্চিত হতে থাকা প্রতিযোগিতায় অসফল হওয়ার ক্রোধ, অন্যের প্রতি, নিজের চেয়ে দুর্বলের প্রতি পীড়নের মধ্যে দিয়ে এক রকম ক্ষমতার তৃপ্তি আস্বাদন, সমাজের খাঁজে খাঁজে গেড়ে বসছে। এর ফলে সাধারণ ভাবে শাসকের সুবিধা হয়। ‘হয় তুমি আমার পেছন পেছন যাবে, অর্থাৎ বোধবিহীন ভাবে আমাকে মেনে নেবে যে ভাবে কোনও প্রাণী মেনে নেয় তার প্রভুকে, অথবা তুমি হয়ে যাবে আমার শত্রু। আমি তোমাকে ধ্বংস করে দেব’— এই মনোভঙ্গি ক্রমশ একরকম মান্যতা পায়। যার হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে সে ততটুকু অত্যাচারী হয়ে ওঠে, কোনও বিকল্প মতকে সহ্য করে না। একটি বৈচিত্রময়, স্বাভাবিক ভাবে বহুবর্ণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই বহুকাল ধরে একতাবদ্ধ একটি সমাজ ক্রমশ অসহিষ্ণু, ক্ষুব্ধ, হয়ে নিজে নিজেকে আঘাত করে, নিজে দুর্বল হয়ে যেতে থাকে।
আরও পড়ুন: ফিরে দেখা স্বাধীনতা, আনন্দবাজার আর্কাইভ থেকে
আজ হয়তো আমরা প্রবেশ করছি আরও সূক্ষ্ম, আরও গভীর এক বিপদের মধ্যে। আমাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার জন্য কোনও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপও আর প্রয়োজন হচ্ছে না। হয় তুমি আমার সঙ্গে একমত, না হলে তুমি ‘অপর’। অপরকে ধ্বংস করে নিজেকে নিরাপদ করার অধিকার আমার আছে— এই মানসিকতা সমাজের এক বড় অংশ আত্মস্থ করেছেন। এবং সেখানে ‘অপর’-এর ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি, এমনকী অস্তিত্বও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করা হয়। সাধারণ মতানৈক্যও ভয়ঙ্কর ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে দু’-একটি ছোট ছোট কথা বলা যায়। এ দেশের বহু অঞ্চলের লোক সহজপ্রাপ্যতা, অভ্যাস ইত্যাদি নানা বাস্তব কারণে কিছু খাদ্যাভ্যাসের সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিছু লোক হঠাৎ ধর্মের স্বঘোষিত ঠিকাদার হয়ে বিনা প্ররোচনায় তাঁদের আক্রমণ করেন এবং ‘শিক্ষিত সমাজ’-এর এক বৃহৎ অংশ তাঁদের কাজকে সমর্থন জানান। ক্রমশ সেটা এক সামাজিক আতঙ্কবাদে রূপ পায়। যে কোনও জায়গায় কাউকে আক্রমণ, এমনকী হত্যাও করা যায় বিনা শাস্তিবিধানের নির্ভয়ে। কাশ্মীরে সেনাবাহিনী যে ভাবে নিজেদের জিপের সামনে একজনকে বেঁধে নিয়ে যায়, একজন সাংবাদিক নিজের রিপোর্টে এই ঘটনাকে জাতীয় সম্প্রীতির পক্ষে হানিকারক বলে সমালোচনা করেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ফেসবুক অন্তত হাজারখানেক ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্যে ভরে যায়।। যার অনেকগুলিই ছিল অশালীন ও কাপুরুষসুলভ।
প্রথম যখন স্বাধীন দেশেও নিজেদের দেশের কিছু সহ-নাগরিককে ‘আদার ব্যাকোয়ার্ড পিপল’ নামে চিহ্নিত করে ভিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন বাকিরা তাতে আপত্তি প্রায় জানাননি। আজ অসহিষ্ণুতা, এক সার্বিক হিংস্রতার মানসিক অভ্যাস, সেই সহ-নাগরিকদের কিংবা যে কোনও ভাবে অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকা, অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের ওপর পীড়ন করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে আর অন্য কিছু লোক, যাঁরা নিরাপদ দূরে থাকবেন, সব কিছু থেকে কেবল নিজের সুবিধা ছাড়া আর কিছু নেবেন না তাঁরা ওই হিংস্রতাকে সমর্থন করে এক রকম মানসিক আরাম পাবেন বলশালীর পক্ষে আছেন ভেবে। এ ভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজও ধীরে ধীরে মানসিক একনায়কতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়। যে কোনও অন্যায় বিনা বিরোধে ঘটতে পারে। কোনও সভ্যতা এই ভাবে কেবল ক্ষমতাপন্থী হয়ে টিঁকে থাকতে পারেনি, ইতিহাস তার নির্মম সাক্ষী। মহান, বর্ণময় অদ্ভুত সুন্দর ভারতবর্ষও পারবে না যদি আমরা এখনই স্বাধীনতার মর্যাদা বিষয়ে যত্নবান আর নৈতিক সাহসে সাহসী না হই।
অলঙ্করণ: অর্ঘ্য মান্না।