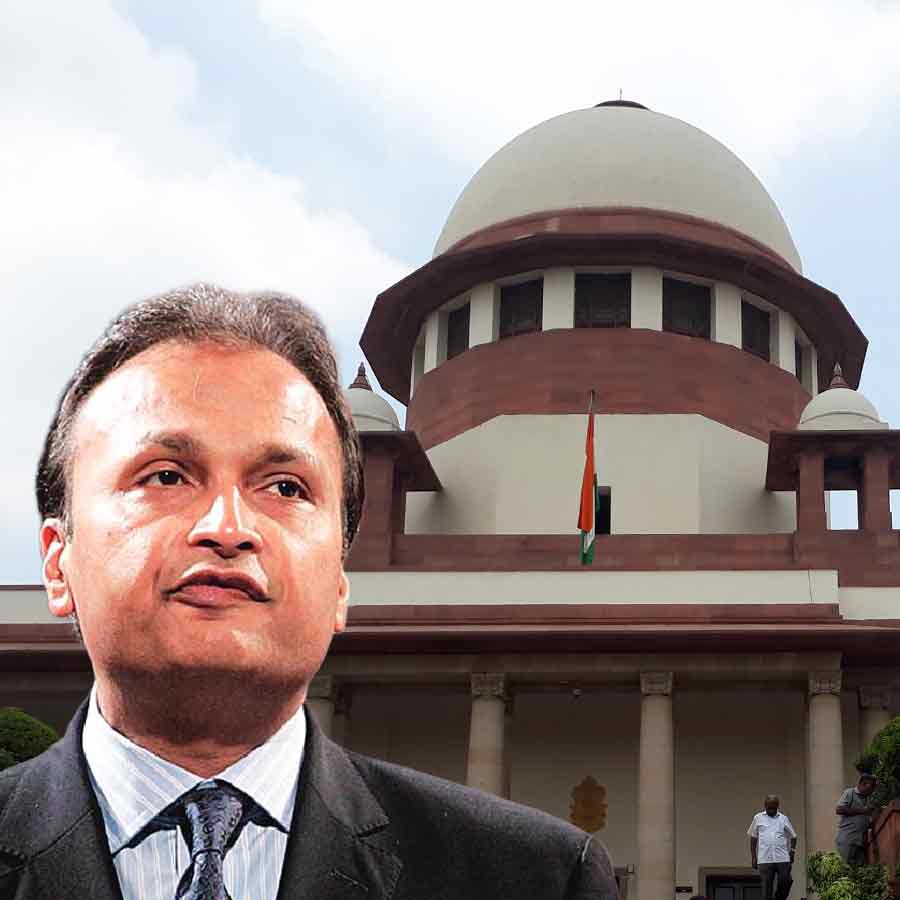রামধনু নিয়ে আহ্লাদিপনা যিনি মোটে সইতে পারেন না, নাম ভুলে গিয়ে যাঁকে স্রেফ ‘খুঁত-ধরা বুড়ো’ বলে দাগিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁকে আজ স্মরণ করতে হচ্ছে। রং-কলাপের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে তাঁর প্রখ্যাত সতর্কবাণী— ‘দেখছ কি এই রং পাকা নয় মোটে!’— নতুন অর্থ পেয়ে গেছে একুশ শতকে। রামধনু সত্যিই রং হারাচ্ছে। বলা ভাল রামধনুটাই হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর জনবহুল এলাকাগুলো থেকে। আরও শুনতে পাচ্ছি, শুধু রামধনু নয়, শুধু আকাশেও নয়— বিশ্ব জুড়ে জলে স্থলে সবখানে রং মুছে যাওয়ার এক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বিশেষ করে জীবদেহ থেকে। এ সবের শেষ কোথায় তা ভেবে বেদনা লুকোচ্ছেন হাতে-গোনা কয়েক জন বিজ্ঞানী, যাঁদের চোখে প্রথম ধরা পড়েছে এই ঘটনাগুলো।
বেদনা পেয়েছিলেন কবি কিটস-ও। রামধনুর সৃষ্টিরহস্য ফাঁস করে দিয়ে বিজ্ঞানীরা নাকি এই রং-বিনুনির মাধুর্যকে ফিকে করে ফেলেছেন— এই ছিল কবির মত। তেমনটা ঘটেনি যদিও; জলকণার সঙ্গে আলোর আলাপন থেকে রামধনুর জন্ম, সে কথা জেনে ফেলার পরেও আমাদের মুগ্ধতা কমেনি। শহরের অলিগলিতে কংক্রিটের ঠুলি আমাদের নজর আটকায়, তবু ঠিকঠাক আবহাওয়ার সঙ্গত পেলে রামধনু সেখানেও ফোটে। অনেকেরই জানা আছে, কয়েকটা বিশেষ প্রাকৃতিক স্থলে, বিশেষ ঋতুতে, রামধনুর সুবাদেই পর্যটনের পালে লাগে বাতাস; যেমন ভিক্টোরিয়া বা ইগুয়াজ়ু জলপ্রপাতে। চিত্রকূটেই বা নয় কেন! অরুণাচলের পাহাড়ে-ঘেরা জ়িরো উপত্যকা বা হাওয়াই-এর কয়েকটি বেলাভূমি বিখ্যাত হয়েছে তার প্রায় অলৌকিক রামধনুর জন্য। কিন্তু হালে এ নিয়ে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। পৃথিবী জুড়ে নানা এলাকায় রামধনু ফোটার হিসেবনিকেশ থেকে ইঙ্গিত মিলছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বহু জায়গায় রামধনু সৃষ্টির উপযুক্ত আবহাওয়া বিরল হয়ে আসবে। গরম এলাকাগুলোয়— যেমন ভারতে, এমনকি ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর মতো নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতেও বছরপ্রতি রামধনুর সংখ্যা নীচে নামবে। উল্টোটা ঘটবে মেরুর কাছাকাছি অক্ষাংশে, সেখানে রামধনুর সংখ্যা বাড়বে, কারণ উষ্ণতার কারণে তুষারের বদলে সেখানকার বাতাসে বাড়বে জলকণা। সে জায়গাগুলো অবশ্য বড় জনবিরল, অন্তত এখনও অবধি। কাজেই বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সব মিলিয়ে পৃথিবীতে রামধনু বাড়লেও মানুষের দৃষ্টিকে ধন্য করবে তার ক্ষুদ্রতর অংশ।
এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তা দেখা দিলে তাকে কি আদিখ্যেতা বলা হবে? পর্যটনলক্ষ্মীর মুখের হাসি ছাড়া আর কিছুই কি এর ফলে মলিন হবে না? এই সময়ের একের পর এক মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষায় ধরা পড়ছে, আমাদের সুস্থতাবোধের সঙ্গে রামধনুর মতো আরও বহু প্রাকৃতিক বিষয় অঙ্গাঙ্গি। পাখির ডাক, অরণ্যবীথি, প্রবাহিত স্বচ্ছ জল, প্রাকৃতিক বর্ণসুষমা— এ সমস্তই আমাদের অন্তরমহলে বার্তা পাঠায়। অমলিন, বৈচিত্রময়, অনাহত প্রকৃতির ছাপ পড়ে মনে ও শরীরে। শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালায় যত হরমোন, যেগুলির কয়েকটা আবার স্নায়ুর বার্তাবাহক, তাদের স্বচ্ছন্দ আচরণের সঙ্গে প্রকৃতির বিশুদ্ধতার নিবিড় সংযোগ রয়েছে। রামধনু অবশ্যই তার একটা উপাদান।
এই কথাগুলো লিখতে লিখতেই ভাবি, শেষ রামধনু কবে দেখেছিলাম তা কি মনে পড়ে? পড়ে না। পাঠকও কি স্মরণে আনতে পারেন শেষ কয়েক বছরে কত বার রামধনু দেখেছেন? অথচ, চোখ বুজে অতীতের দেখা কোনও রামধনুর ছবি স্মরণে আনলেও গায়ে পুলক লাগে! এ এক আশ্চর্য বিস্ময়। সহজেই মনে হয়, রঙে রঙে আমাদের মগজের তন্ত্রী বাঁধা আছে— এ কথাটায় আর যা-ই হোক আতিশয্য নেই। চিত্রশিল্পীর কাছে এর জন্য সাক্ষী খুঁজতে যাওয়ার দরকার হয়তো পড়বে না, তবু মনে পড়বে ‘আমসুন্দরী’-তে পরিতোষ সেন কী ভাবে একটা আনাজপাতির বাজারে নিয়ে গিয়ে আমাদের রঙের চোখ খুলে দিয়েছিলেন। অথবা নতুন করে মনে পড়বে পাউল ক্লি-র নামে চলে আসা বয়ান: আমাদের মগজ যেখানে এসে জগতের সঙ্গে মেলে, ঠিক সেটাই হল রং।
নিউরোসাইকোলজিস্ট নিকোলাস হামফ্রি— মানুষ তথা বানরজাতীয় প্রাণিদল অর্থাৎ প্রাইমেটদের বোধশক্তি নিয়ে যিনি গবেষক জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, তিনি অবশ্য এক বার বলেছিলেন, মানুষ বুঝে বা না-বুঝে রঙের বারোটা বাজিয়েছে। অপ্রয়োজনে এত রং সে লেপ্টেছে— কেবল নিজের শরীরে আর শিল্পীর ক্যানভাসে নয়, তার আবাসে আসবাবে তৈজসে পোশাকে যে, রঙের অন্তর্নিহিত অর্থগুলো সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতিতে, বিশেষ করে জীবজগতে, রং প্রায়শই একটা সঙ্কেত, একটা ভাষা। যথেচ্ছ রং ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ সে ভাষা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তৈরি করেছে নিজের বর্ণজগৎ। তবুও, বিবর্তনের দীর্ঘ সময় জুড়ে তার চেতনায় প্রকৃতির সঙ্গে যত কথোপকথন চলেছিল, তার কিছু আভাস হয়তো রয়ে গেছে এখনও। আর সে কারণেই রামধনু তার গভীরে গিয়ে বাজে।
বাস্তবিকই রং হল সঙ্কেত। ট্রাফিক আলোর বেলায় আমরা তা গড়েছি সচেতন ভাবে। কিন্তু প্রকৃতিতে সঙ্কেত ব্যবস্থাগুলো পরিস্থিতি অনুযায়ী জন্ম নিয়েছে আপনা থেকে, পরে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ক্রমশ জোরালো হয়েছে। এ সব সঙ্কেতের কোনওটার জন্ম কেবল আপন প্রজাতির অন্য সদস্যদের জন্য। যেমন ময়ূরের পেখম। সবচেয়ে খুঁতহীন পেখমের অধিকারীটিই পায় ময়ূরীর বরমাল্য। কারণ সেটাই বলে দিচ্ছে, এর অধিকারী প্রাণীটির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে অমন বাহারি এক পেখম গড়ার, এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতা থেকে পেখমের সৌষ্ঠবকে, আর নিজেকেও, রক্ষা করার। কাজেই অমন পুরুষকেই তো চাই ময়ূরীটির।
এর তুলনীয় সঙ্কেত পৃথিবীতে রয়েছে ভূরি ভূরি। কখনও তা রঙের মাধ্যমে, বলা উচিত দৃশ্যমাধ্যমে ফুটে ওঠে, কখনও-বা শব্দ হয়ে বাজে। যেমন ব্যাঙের ডাক, পাখির গান; ফুলের বর্ণমালা থেকে মৃগনাভির ঘ্রাণ। সত্যি বলতে কী, প্রতিটি ঋতুর যত রং-রস-রূপ-গন্ধ-গীত আমাদের কাছে বিশুদ্ধ প্রকৃতির বার্তা বয়ে আনে, তার অনেকটাই আসলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির নানা বিচিত্র কারণে তৈরি সঙ্কেত-চালাচালির খেলা। আমরা মাঠের বাইরে বসে থাকা দর্শকের মতো তা উপভোগ করি কেবল।
আজ, মানুষের অবিবেচনায় এই সঙ্কেত চালাচালির দুনিয়ায় ভাঙচুর ঘটে যাচ্ছে। সঙ্কেত গঠন, আর সঙ্কেত পড়া, দুটোতেই ঘটছে ব্যাঘাত। জোনাকির সমস্যাটাই ধরুন। তার কথোপকথন চলে আলোর স্পন্দনে। সে জন্য নিকষ আঁধার হল শ্রেয় পরিবেশ। কিন্তু মানুষ নির্বিচারে এত বেশি আলোয় রাত্রিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে যে, জোনাকির ক্ষীণ আলো হয় ধরা পড়ছে না সম্ভাব্য সঙ্গীটির কাছে, অথবা, সঙ্কেত-প্রেরক নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। তাদের স্বাভাবিক কথোপকথন ডুবে গেছে আলোর কোলাহলে।
রাতের আলোর আরও সমস্যা আছে। আমি পেশাদার বা শখের জ্যোতির্বিদদের কথা তুলছিই না, যাঁরা আলোর অত্যাচারে ধাঁধিয়ে যাওয়া দূরবিন নিয়ে দিনে দিনে আরও বেশি বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠছেন। দিনে যেমন মাছি মৌমাছি প্রজাপতি, রাতে তেমনই মথ বা অন্য পতঙ্গ আসে ফুলের হয়ে পরাগ বহনের কাজ করতে। এখন যে বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী এলইডি বাতি জ্বালানো হয়, তা আমাদের চোখে সাদা দেখালেও তাতে বেশ কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো অনুপস্থিত। এই অভাব পতঙ্গদের ইন্দ্রিয়ে ব্যাঘাত ঘটায়, তারা ফুলের সঙ্কেত ঠিকঠাক পড়ে উঠতে পারে না। ফলে রাতে ফুলের সঙ্গে পতঙ্গের ব্যবসায়িক আদানপ্রদান যেমন চলার তেমনটা ঠিক চলছে না।
রং বোঝার জন্য, সঙ্কেত-চালাচালির জন্য, চাই ঠিকঠাক স্বাভাবিক আলো। বেশি নয়, কমও নয়। একটা বিচিত্র সমস্যা ধরা পড়েছিল আফ্রিকার মিষ্টি জলের মাছেদের বেলায়। মাছের শরীরেও রং ঝলকায়— ঘরের অ্যাকোয়ারিয়াম তার সাক্ষী, আমাদের চেনা (যদিও ইদানীং বিরল) খলশে মাছটিকে স্মরণ করুন। জলের নীচে পুরুষ মাছেরা স্ত্রী মাছেদের বার্তা পাঠায় শরীরের নানা অংশের উজ্জ্বল রঙের সাহায্যে। কখনও লেজ, কখনও পাখনা, কখনও শরীরের কোনও বিশেষ আঁশের বিন্যাস থেকে প্রচারিত হয় রং-বার্তা। এ ব্যবস্থা চলে আসছিল ভালই, কিন্তু সম্প্রতি জলাশয়ে এসে মিশছে নানা রকম আপত্তিকর পদার্থ। মাটি-ময়লা-সূক্ষ্ম আবর্জনা তো আছেই, এমনকি জলে যদি চাষের খেত ধুয়ে গড়িয়ে আসা রাসায়নিক সার এসে মেশে তো তাতেও বিপত্তি। জলে প্রবল হারে জন্ম নেয় অবাঞ্ছিত শৈবাল, জলকে ঘোলাটে করে তোলে। ঘোলা জলে রঙের সঙ্কেত মাটি হয়ে যায়, কারণ রং বোঝার মতো যথেষ্ট আলো আর ঢুকতেই পারছে না জলের তলায়। এবং তারফলেই, স্ত্রী আর তার আপন পুরুষটিকে চিনে উঠতে পারে না।
এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, বার্তা পড়ার গোলযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, এবং জন্ম নিচ্ছে সংকর প্রজাতির মাছ। এ ঘটনা ধরা পড়েছে আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদে, রঙিন সিকলিড ফ্যামিলির (তেলাপিয়া ও নাইলোটিকার গোত্র) কিছু মাছে। আংশিক রং খুইয়েছে ব্রাজিলের গাপ্পি মাছেরাও (মশার প্রকোপে রাশ টানতে ব্রিটিশরা যাদের এ দেশেও এনেছিল)। ঘটনা হল, ঘোলা জলে রঙের ভাষা অকেজো, আর রং তৈরির কাজটাও ব্যয়সাপেক্ষ। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়াও এর আর-এক কারণ হল, মানুষী ক্রিয়াকর্মের ফলে জলাশয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। মাছেরা তাদের সঠিক পুষ্টি আর জোটাতে পারছে না, শরীরে রং তৈরির জন্য যে পুষ্টি জরুরি ছিল।
বহু জীবশরীরের লালচে-কমলা রঙের উৎস ক্যারোটিনয়েড নামের এক গোত্রের পদার্থ। নামটার মধ্যে গাজর বা ‘ক্যারট’ ঢুকে আছে; বলা বাহুল্য কমলা-রঙা গাজর ক্যারোটিনয়েডের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কিন্তু একমাত্র উৎস নয়। বহু উদ্ভিদে, শৈবালে, প্রাণিদেহে এর উপস্থিতি। কিন্তু পরিবেশের বৈগুণ্যে গাপ্পি ও সিকলিড যথেষ্ট ক্যারোটিনয়েড পাচ্ছে না তাদের খাবারে। এখানে কেবল এদেরই নাম উঠে এল বলে ভাবার কারণ নেই যে বাকি জলচর সকলে নিরাপদে আছে।
প্রাণীরা কিছু রং তাদের শরীরে তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু আরও বহু রঙের প্রাথমিক উপাদানের জন্য পরিবেশ থেকে জোটানো স্বাভাবিক আহারের উপর নির্ভর করতে হয়। নষ্ট পরিবেশ সেই সব উপাদান আর জোটাতে পারছে না। একই ঘটনা দেখা গেল, জলে নয়, আকাশচারী এক প্রাণীতে। সেটি আমেরিকান কেস্ট্রেল, এক ধরনের ছোট শিকারি পাখি। লেসার কেস্ট্রেল-সহ অন্যান্য ফ্যালকন-এর নানা প্রজাতি আমাদের দেশেও মিলবে। আমেরিকান কেস্ট্রেলের ঠোঁটের গোড়ায় মুখের কিছু অংশ এবং চোখের কোল ঢেকে রেখেছে পালকহীন ত্বক। তার রং হলুদ। পায়ের নগ্ন ত্বকের একাংশও হলুদ, এবং এইসমস্ত হলুদের কাঁচামাল ক্যারোটিনয়েড। হলুদের ঔজ্জ্বল্য মাপতে গিয়ে দেখা গেল, তা ক্রমশ নীচে নামছে। ক্যারোটিনয়েড কি কম পড়িতেছে?
ঠিক তা-ই। আমেরিকান কেস্ট্রেলের খাদ্য হল মেঠো ইঁদুরের মতো এক প্রাণী, ভোল (vole), সেই সঙ্গে ফড়িং, উচ্চিংড়ের মতো নানা কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, এমনকি ছোট পাখি। কয়েক বছরের নজরদারিতে ধরা পড়েছে, যে সব কেস্ট্রেল যথেষ্ট পোকামাকড় বা অন্য খাবার পাচ্ছে না, কেবল বেশি করে ভোল ধরে পেট ভরাচ্ছে, তাদের গায়ে হলুদ রঙের ঔজ্জ্বল্য পড়তির দিকে। বলা চলে আহারের বৈচিত্রই কেস্ট্রেলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছে, সেখান থেকেই আসে ক্যারোটিনয়েডের জোগান। অপুষ্টির ছাপ পড়েছে ইউরেশিয়ান কেস্ট্রেল-এর ছানার শরীরেও। এদের পালকের জোরালো কালো রং আর আগের মতো নেই। তবে, এদের বেলায় অভাবটা ক্যারোটিনয়েডের নয়, মেলানিনের, যা থেকে তৈরি হয় পালকের ধূসর ও কালো রং। আর মেলানিন তৈরি হয় পাখির শরীরেই। কিন্তু পরিবেশে কীটপতঙ্গ বিরল হয়েছে বলে আমেরিকান কেস্ট্রেলের মতো এদেরও আহারে বৈচিত্র গেছে কমে, ঠিকঠাক পুষ্টি জুটছে না। শরীরে যথেষ্ট মেলানিন তৈরি হচ্ছে না তাই।
পাখিরা প্রোটিনের একটা বড় অংশ পায় পতঙ্গ থেকে। যে সব পাখি কেবল শস্যদানা খায় বা ফল খায়, তাদেরও শাবক অবস্থায় ‘দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি’ বলার জন্য পেতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে পোকামাকড়। কোনও কোনও পাখি শাবকদের বড় করার নামে এক-এক পালায় ছ’হাজার থেকে ন’হাজার শুঁয়োপোকা শিকার করে। সেগুলো অমিল হলে জীবন আর আগের মতো থাকে না।
কেস্ট্রেলের বেলায় তবু রং হারানোর কারণটা গেঁথে ফেলা গেছে, কিন্তু সমুদ্রতটবাসী এক ধরনের কাঁকড়ার বেলায় (শোর ক্র্যাব) তাও ঠিকঠাক করা যায়নি। দিনে দিনে এদের শরীর-ঢাকা শক্ত খোলস রং হারাচ্ছে। এটুকু কেবল জানা গেছে যে, তার মূলে আছে তীব্র শব্দের অত্যাচার। সেটা ঘটছে সমুদ্রতলে, সমুদ্রপৃষ্ঠে জাহাজ চলাচল-সহ আনুষঙ্গিক নানা মানুষী কর্মব্যস্ততার কারণে। যদিও, শব্দ কী ভাবে বর্ণ নাশ করছে সে প্রক্রিয়া গুনে-গেঁথে বোঝা যায়নি এখনও।
রাসায়নিক দূষণ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। সত্যি বলতে কী, আজকের দিনে পরিচিত যে পরিবেশ ভাবনা, তার জন্মই হয়েছিল ষাটের দশকে র্যাচেল কারসন-এর প্রায় একক লড়াই দিয়ে। রাসায়নিক দূষণের বিরুদ্ধে। সে দিন তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ডিডিটি। ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’-এর লেখিকা আজ হয়তো তাঁর বইয়ের নাম দিতেন ‘বিবর্ণ বসন্ত’। জীবদেহ থেকে রং চুরি করা নানা রাসায়নিকের মধ্যে আছে কিছু ভারী ধাতু এবং জৈব যৌগ। সমুদ্র উপকূলের পাখি গাল (gull)-এর ঠোঁটে যে হলুদ ছোপ থাকে তার উৎস ক্যারোটিনয়েড, কিন্তু জৈব রাসায়নিক-ঘটিত দূষণ এসে ক্যারোটিনয়েড ব্যবহারের শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থাটাতেই গোল পাকিয়েছে। পাখির ঠোঁটে হলুদের গোত্র আর ঘনত্ব ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ইউরোপের পাখি গ্রেট টিট-এর বেলায় (কিছু দিন আগেও আমাদের ঘরোয়া পাখি রামগাংরাকে এর স্বজাতিভুক্ত বলে ভাবা হত) ভারী ধাতু-ঘটিত দূষণের প্রভাব পড়েছে দ্বিমুখী। এদের বুকের রং অংশত হলুদ, কিন্তু ক্যারোটিনয়েড সদ্ব্যবহার নিয়ে গোলযোগের ফলে সে রং ফিকে হয়ে আসছে। অপর দিকে শরীরের অন্যঅংশে পালকের কালো রং গাঢ় হচ্ছে, দূষণের প্রভাবেই।
ইন্টারনেটে একটু নজর চালালে এ ধরনের রং মোছার বৃত্তান্ত মিলবে আরও বহু ক্ষেত্রে। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মনীষা কোনেরু আর টিম কারো এ নিয়ে একটা সমীক্ষাও প্রকাশ করেছিলেন ২০২২-এ। কিন্তু এখানে এসে আমাদের একটু ভাবতে হচ্ছে, কারণ, প্রশ্নটা কেবল রং ফিকে হওয়া নিয়ে নয়। সেটা আসলে একটা উপসর্গ। মূল সমস্যাটা বহু দূরে আর গভীরে প্রসারিত, চরিত্রেও নানা রকমের। কিন্তু একটা বিন্দুতে গিয়ে তারা মিলছে, দেখা যাচ্ছে এ সবের প্রতিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির উপর মানুষের চাপ। নির্বিচারে তাকে নিষ্কাশনের চেষ্টা। তাকে দিনে দিনে রিক্ত করে তোলা।
এই শেষের কথাগুলো কম করে গত চার-পাঁচ দশক জুড়ে এত বার, এত ভাবে বলা হয়েছে যে আজ যে ভাবেই বাক্য গাঁথা হোক, তা বড় ‘ক্লিশে’ মনে হয়। আপাত-নজরে ধীরে, কিন্তু আসলে ক্রমবর্ধমান গতিতে পৃথিবী রিক্ত হচ্ছে, কিন্তু তার বিপরীতে যা দেখছি তা আজকের লব্জে ‘বিজ়নেস অ্যাজ় ইউজ়ুয়াল’।
রং-হারানো পৃথিবীকে দীন ভেবে কাতর হওয়া কি আদিখ্যেতা? পৃথিবীটা ভাল নেই, এই বোধটাই কি আমাদের ভেতর থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে না? যে পরিবেশ ছিল প্রকৃতির বহু বিচিত্র সদস্যের রঙে উজ্জ্বল, তা ক্রমে ম্যাটমেটে অনুজ্জ্বল ধূসর খয়েরি হয়ে আসছে, এ কথাটা চোখ বুজে মনে মনে ভাবুন এক বার। এক বার ভাবুন চার পাশে কেবল সেই প্রজাপতিরাই রয়েছে, যাদের রঙে কোনও ঔজ্জ্বল্য নেই। তারা সব ম্যাটমেটে, ধূসর, খয়েরি, যাদের নজরে আনাই কঠিন, দেখলেও মনে যেন সাড়া জাগে না। কেমন হবে সেই পৃথিবী?
ব্রাজিলের কয়েকজন জানাচ্ছেন, সেই প্রক্রিয়াটাও শুরু হয়ে গেছে। কোনও এলাকায় অরণ্য বিনাশের ফলে যে প্রজাপতিরা পড়ে থাকছে, তাদের রং ম্যাড়মেড়ে। কারণ স্বাভাবিক অরণ্যে, যেখানে রঙিন প্রজাপতিরা পরিবেশের সৌজন্যেই শিকারি প্রাণীদের চোখ এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারত, সেই পরিবেশটাই তাদের জন্য আমরা রাখিনি।
রং, প্রজাপতির ক্ষেত্রেও, দস্তুরমতো সঙ্কেত। আর সে সব সঙ্কেত-চালাচালি হয় কখনও তার নিজের প্রজাতির উদ্দেশে— যেমন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, কখনও তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি-হানা বুভুক্ষু শিকারি প্রাণীর উদ্দেশে। জলের তলার মাছেদের মতো এখানেও ডানার রঙের চরিত্র দিয়ে স্ত্রী চিনে নেয় তার আপন প্রজাতির পুরুষকে। অধিকাংশ স্ত্রী আর পুরুষের ডানা থেকে ঠিকরে বেরনো আলোর রং হয় আলাদা।
রংই একমাত্র মাধ্যম নয় অবশ্য চেনাচিনির ক্ষেত্রে— গন্ধ, ডানার ছন্দ, সামগ্রিক চলন, এমনকি কখনও বা শব্দ— এ রকম অনেক কিছুই তাতে কাজে লাগে। কিন্তু শেষ অবধি দূর থেকে সঙ্কেত পাঠানোর জন্য আলোই হল সেরা মাধ্যম, আর আলোর চরিত্র ধরা পড়ে তার রঙে। তাই, বেশির ভাগ প্রজাপতির ডানায় যে এক রংদার হল্লা শুরু হয়েছে, তার জন্য অনেকাংশে দায়ী অন্যান্য প্রজাতি থেকে নিজেকে আলাদা করে মেলে ধরার প্রজাপতীয় চেষ্টা। একটা প্রাণীর কাছে যা মরিয়া তাগিদ, সেটাই আমাদের কাছে নয়নাভিরাম অভিজ্ঞতা, পৃথিবী যে এখনও বাসযোগ্য আছে তার সাক্ষ্য। প্রজাপতির রঙের অভিঘাত কী প্রবল হতে পারে, তা পরবর্তী দিনের মানুষদের জন্য লিখে গেছেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, বিবর্তন তত্ত্বের জনক হিসেবে আজ যাঁর নাম চার্লস ডারউইনের সঙ্গে একযোগে উচ্চারিত হয়।
১৮৫৯ সাল। ওয়ালেস তখন রয়েছেন মালয়ের জঙ্গলে, পশুপাখি-কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করছেন, সেগুলো ধরে ধরে নমুনা পাঠাচ্ছেন দেশের এজেন্টের কাছে। বেশ কয়েক দিন তক্কে তক্কে থাকার পর শেষ পর্যন্ত তিনি এক বার্ডউইং প্রজাপতির পুরুষকে জালে বন্দি করতে পেরেছিলেন। তার পর লিখেছিলেন—
“যা ভেবেছি ঠিক তা-ই, এটা একেবারে নতুন একটা প্রজাতি, আর সব থেকে রাজকীয়। পৃথিবীর সমস্ত দরাজ রংঢালা প্রজাপতিদের মধ্যে সেরা। পুরুষ প্রজাপতির টাটকা নমুনাগুলো ডানার আড়ে সাত ইঞ্চিরও বেশি বড় হবে। মখমল-কালো, আর সেই সঙ্গে আগুন-আগুন কমলা রং। অন্যান্য নিকট প্রজাতিগুলোতে এই কমলার জায়গায় থাকে সবুজ। এমন সৌন্দর্য আর এই ঔজ্জ্বল্যের বর্ণনা দিই সাধ্য কী।
“অনেক চেষ্টায় সেটাকে ধরতে পারার পর যে কী প্রচণ্ড উত্তেজনা হচ্ছিল সেটা কোনও দিনই আর-এক জন ন্যাচারালিস্ট ছাড়া বুঝতে পারবে না। যেই জাল থেকে বার করেছি এটাকে, আর তার জমকালো ডানাগুলো মেলে ধরেছি, অমনি আমার বুকটা প্রচণ্ড ধকধক করতে শুরু করল, রক্ত ছুটল মাথায়, মনে হচ্ছিল যেন জ্ঞান হারাব। এর আগে মৃত্যুর মুখে পড়েও কোনও দিন এমনটা হয়নি।... এমন প্রবল উত্তেজনা শুরু হল যে, তার ধাক্কায় আমার মাথাটা ধরে রইল গোটা দিন।”
এ লেখাকে এক জন প্রজাপতি-পাগল মানুষের আতিশয্য বলে অগ্রাহ্য করা যায় কি না, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু রঙিন কোনও প্রজাপতির নির্ভার ওড়ার ছন্দ আমাদের কাউকে কোনও দিন সম্মোহিত করেনি, এ কথা মেনে নেওয়া দুষ্কর। শৈশবে ধরা প্রজাপতির ডানা থেকে এক বার যে-রং কারও আঙুলে লেপ্টেছে, তা সারা জীবন ঘষে চললেও মোছে না।
প্রজাপতির রং হারানোর এই সব উদাহরণকে নেহাত ব্রাজিলের ব্যাপার বলে বসে থাকা মূর্খামি। কারণ এই অঘটনের ধাপগুলো স্পষ্ট, সেটা যে কোনও জায়গায় ঘটতে পারে। প্রবলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর অন্যতম সফল উপায় অবশ্যই লুকিয়ে থাকা। সে জন্য বাইরে থেকে পড়ে ফেলা যায় এমন সব সঙ্কেতকেই চেপে রাখতে হয়। কিন্তু নিজের শরীর থেকে ঠিকরে বেরনো আলো বা রংকে ঠেকাব কী করে? তাই যেটা করা চলে, তা হল চার পাশের প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলা। সবুজ পাতায় বসে থাকা সবুজ গঙ্গাফড়িংকে যেমন নজরে আনা মুশকিল, তেমনই ন্যাড়া পাথর-মাটি-ধুলোয় ভরা মরুসদৃশ প্রকৃতিতে ধূসর খয়েরি প্রজাপতিকেও নজরে আনা দুষ্কর।কিন্তু ওখানেই যদি একটা রঙিন প্রজাপতিকে আনা হয়, তা হলে শত্রু প্রাণীরা তাকে সহজে শনাক্ত করবে এবং তাকে দিয়ে পেট ভরাবে। সেখানে সফল হবে কেবল রংহীনতা।
ব্রাজিলে আমাজ়নের অরণ্য মুছে যাচ্ছে বিপুল হারে। শুধু ২০২৩-এ কাটা হয়েছিল ১৮ লক্ষ হেক্টর আয়তন, যা নাগাল্যান্ড রাজ্যটির থেকেও বড়। বহু পূর্বতন অরণ্যের স্বাভাবিক চরিত্র গেছে নষ্ট হয়ে। অরণ্যের বিনষ্টির মাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, অকৃত্রিম অরণ্যে যত রঙিন প্রজাপতি মিলছে, ক্ষয়প্রাপ্ত অরণ্যে তত নয়। যে পরিবেশ যত বৃক্ষহীন, বাআদি অরণ্যকে সরিয়ে যেখানে যত বেশি বিকল্প গাছ লাগিয়ে জমি ছাওয়া হয়েছে, সেখানে ম্যাড়মেড়ে বেরঙা প্রজাপতির অনুপাত বেশি।
এত সব বেরঙা উদাহরণের পরিণাম কী? এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় মনার্ক প্রজাপতির সংখ্যায় ধস নামা সম্পর্কে ও দেশেরই এক বিজ্ঞানী লিঙ্কন ব্রাওয়ার-এর মন্তব্য মনে পড়ছে।
মনার্ক প্রজাপতি একটা আইকন— কেবল আমেরিকায় নয়, বিশ্ব জুড়ে। এর মূলে আছে তাদের বিস্ময়কর উড়াল। মার্চ থেকে মোটামুটি অগস্ট মাস অবধি, কয়েকশো কোটি মনার্ক ধাপে ধাপে কয়েক প্রজন্ম ধরে মেক্সিকো থেকে উত্তর মুখে উড়তে উড়তে পৌঁছয় কানাডার দক্ষিণ প্রান্তে (অপর একটা স্রোত আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত ধরে ও দিকেই এগোয়, কিন্তু তাদের শীতের ডেরা মেক্সিকোয় নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায়)। ফেরেও ঠিক সেই পথেই, কিন্তু এ বার গোটা দূরত্ব পেরিয়ে আসে একটিই প্রজন্ম, শেষ খেপে যারা জন্মেছিল। ভাবা যায়, এক গ্রামেরও কম ওজনের একটা পোকা উড়ে আসছে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার লম্বা পথ! খুঁজে নিচ্ছে তার চার প্রজন্ম আগের দিদিমা-ঠাকুমারা যে গাছগুলো অবলম্বন করে নিষ্ঠুর শীত কাটিয়েছিল, ঠিক সেই গাছগুলোকেই। এবং বরফের কামড় সহ্য করে টিকে থাকছে পরের বসন্ত অবধি, নতুন বছরের উড়াল শুরু করার জন্য। এ বিস্ময় ছাড়া আর কী!
যদিও এই অভিযাত্রীদের মোট সংখ্যা প্রায় কয়েকশো কোটি, কিন্তু নানা কারণে এদের সংখ্যা নেমে আসছিল দ্রুত (আশার কথা, সদ্য কয়েক বছর হল, বিশেষ করে এ বছর, তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে)। সে সময়ে কেউ কেউ এদের বিলুপ্তি নিয়ে আশঙ্কিত হচ্ছিলেন। লিঙ্কন ব্রাওয়ার তখন বলেছিলেন, না, প্রজাতি হিসেবে মনার্ক বিলোপের আশঙ্কা নেই, কারণ মেক্সিকো ও আমেরিকা ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ়-সহ কয়েকটা জায়গায় এই প্রজাপতিরা বাস করে। তারা হয়তো টিকে যাবে। কিন্তু ঘটনা হল, তাদের মধ্যে তো এ ধরনের দূরান্তে মাইগ্রেশন ঘটতে দেখা যায় না। কাজেই মনার্ক হয়তো থাকবে, কিন্তু এমন এক বিরল ঘটনা হারিয়ে ফেলার পর পৃথিবীকে কি বড় মলিন আর দীন বলে মনে হবে না! সেটা কি আমরা সইতে পারব?
এই ছিল লিঙ্কন ব্রাওয়ারের প্রশ্ন।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)