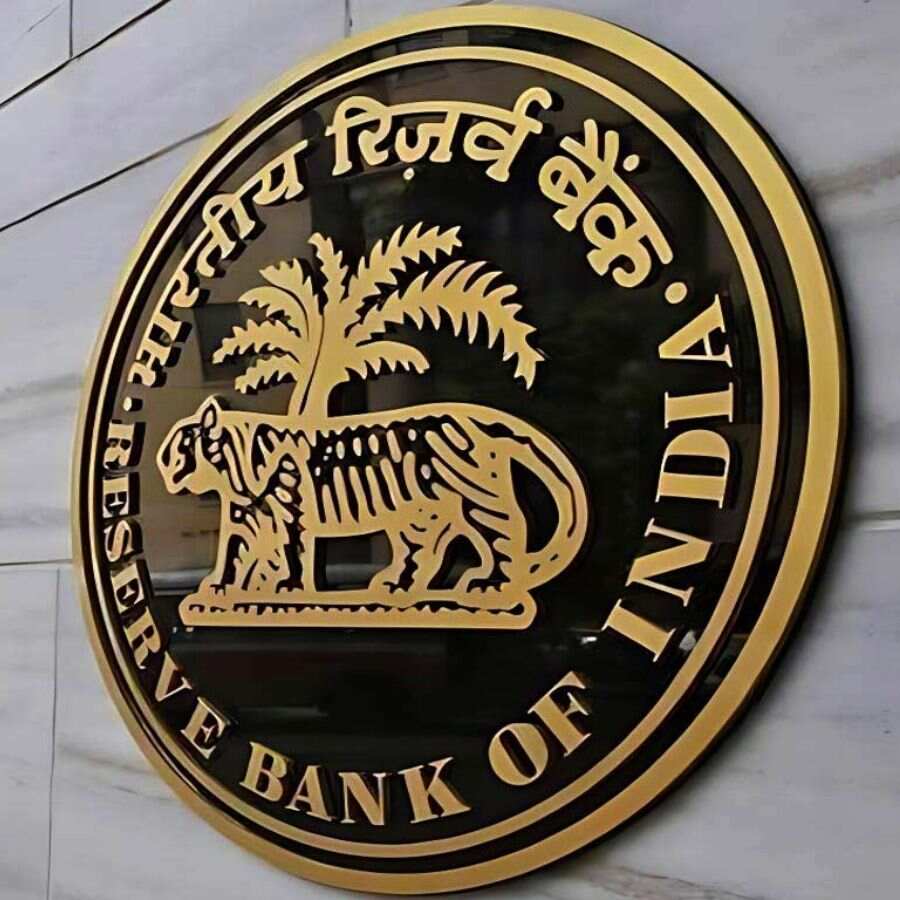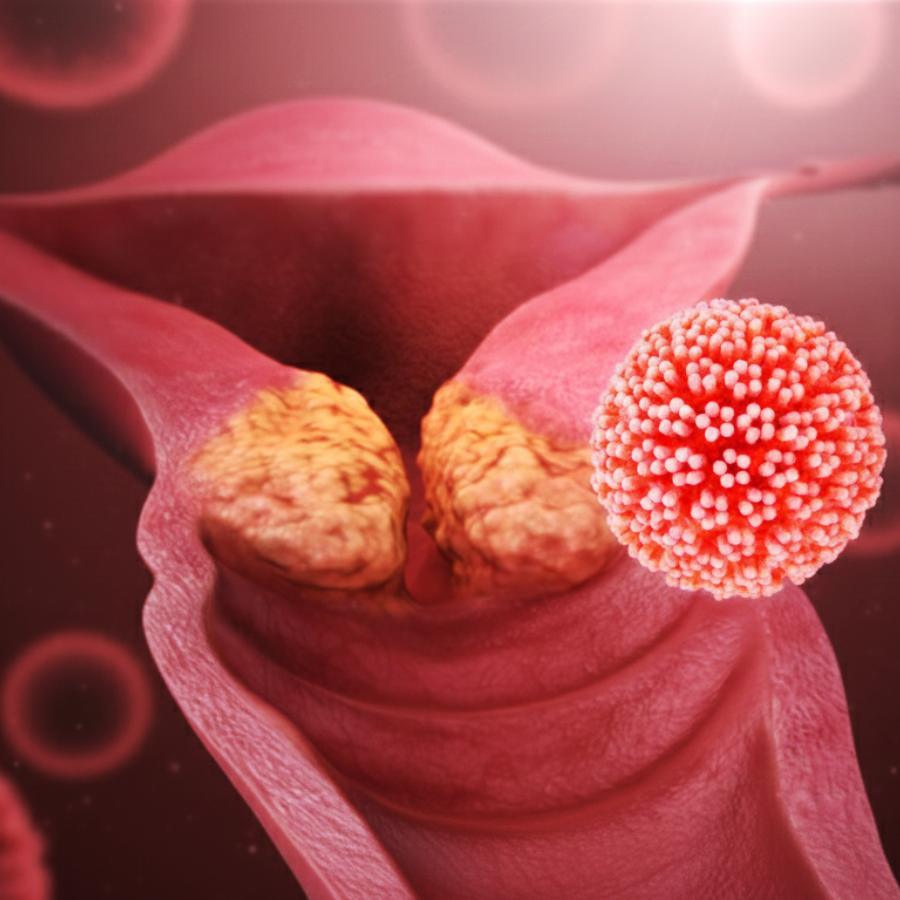প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯১৩ সালে ভর্তি হলেন এক যুবা। দরাজ গলা, চোখমুখ উজ্জ্বল। মাঝেমধ্যেই সহপাঠীদের জড়ো করে ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা দেন। খেতেও ভালবাসেন খুব, ক্লাস শেষে হেমন্ত সরকার ও আরও ক’জন বন্ধু জুটিয়ে পৌঁছে যান কলেজের পিছন দিকটায়। ৮/২ ভবানী দত্ত লেন-এ। হাঁক দেন হোটেল মালিককে, ‘‘কী মনগোবিন্দ, আজ হয়েছে নাকি তোমার পুঁইশাকের চচ্চড়ি? তাড়াতাড়ি খেতে দাও।’’ নিজের হাতে শতরঞ্চি পেতে বন্ধুদের নিয়ে গোল হয়ে বসে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু।
সে দিনের কথা বলতে বলতে ৯৮ বছরের প্রহ্লাদচন্দ্র পন্ডার চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। দাদা মনগোবিন্দ পন্ডার কাছে এই গল্প কত বার যে শুনেছেন! পরে নিজেও একাধিক বার দেখেছেন নেতাজিকে। এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীর, ফ্যাকাসে মুখ, সেই সব স্মৃতি তবু অমলিন। চার-পাঁচ বছর বয়স তখন, দাদার হাত ধরে ওড়িশা থেকে এলেন কলকাতায়। দাদা তত দিনে খুলে বসেছেন ভাতের হোটেল। উদ্দেশ্য একটাই, নিরন্ন ভারতবাসীর মুখে যৎসামান্য অর্থে খাবার জোগানো। মাত্র এক আনায় দু’বেলা ভরপেট মাছ-ভাত। কোনও দিন সঙ্গে মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি। ট্যাঁকে পয়সা না থাকলেও কেউ ফিরে যেত না। ‘‘দাদা বলতেন, হোটেল খুলেছি ব্যবসা করতে নয়, লোকের সেবা করতে। ভুখা মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার যে কী আনন্দ, তা কেবল আমরাই জানি।’’
মনগোবিন্দ নাম রাখলেন ‘হিন্দু হোটেল’। জায়গা দিলেন এক মুসলিম পরিবার। শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত যে কোনও বিপদে কলাবাগানের মুসলিম ভায়েরাই ছুটে এসেছেন সবার আগে। আগলে রেখেছেন তাঁদের সাধের ‘হিন্দু হোটেল’কে। খদ্দের হোক বা কর্মচারী, হোটেলে সবার অবাধ যাতায়াত। প্রহ্লাদবাবুর কথায়, ‘‘একসঙ্গে দেশ স্বাধীন করেছি। আমাদের কোনও ভেদ নেই। সবাই ভাই ভাই।’’
১৯১০ সালে শুরু। হোটেল-অন্তপ্রাণ মনগোবিন্দ ও ভাই প্রহ্লাদচন্দ্রের যোগ্য সঙ্গতে অল্প সময়েই আড়ে-বহরে বেড়ে উঠল হোটেল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল সুনাম। মাছের হালকা ঝোল-ভাত খেতে অনেকেই হাজির হত। যদিও তত দিনে সেটা আর শুধু ভাতের হোটেল নেই। হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন আখড়া। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ঝকঝকে তরুণরা দল বেঁধে খেতে আসত। খেতে খেতেই চলত তাদের বৈঠক। ঠিক হত আগামী দিনের কার্যপ্রণালী। ‘‘সে বার হোটেলে এক ঝাঁক স্বাধীনতা সংগ্রামী। হানা দিল ইংরেজের পুলিশ। দরজা আগলে দাঁড়ালেন দাদা। মার খেলেন, তবু এক চুল সরলেন না। দাদার প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হল পুলিশ। তরুণরা সবাই জড়িয়ে ধরল মনগোবিন্দকে। তখন তাঁর কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চাপচাপ রক্ত। কিন্তু চোখেমুখে শিশুর মতো হাসি,’’ বলতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে প্রহ্লাদচন্দ্রের।
কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন পুরোদস্তুর রাজনীতিতে। ফের তাঁর পায়ের ধুলো পড়ল হিন্দু হোটেলে। এ বার সঙ্গে তাঁর রাজনীতির গুরু। তত দিনে হিন্দু হোটেল আরও জনপ্রিয়, মনগোবিন্দের নতুন নাম হয়েছে ঠাকুরমশাই। দোকানে ঢুকেই সুভাষচন্দ্র বললেন, ‘‘দেখো ঠাকুরমশাই, কাকে নিয়ে এসেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তোমার হোটেলের তো খুব নামডাক হয়েছে দেখছি। ভালমন্দ খাওয়াও দেখি! দুজনে কবজি ডুবিয়ে খাই।’’ ভরপেট খেলেন দু’জনে। যাওয়ার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ মনগোবিন্দকে বললেন, ‘‘এই ছেলেটাকে ভাল করে খাওয়াবে। ও দেশের ভবিষ্যৎ।’’
তবে সে বারও নেতাজিকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি প্রহ্লাদচন্দ্রের। শিকে ছিঁড়ল আরও কয়েক বছর বাদে। ১৯৩০। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। নীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, অমূল্য চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীশ জোয়ারদার সহ একাধিক অনুগামীকে নিয়ে হাজির হলেন হিন্দু হোটেলে। প্রহ্লাদবাবুর সেই প্রথম নেতাজিকে দেখা। আগামী দিনের কর্মপন্থা নিয়ে অনুগামীদের বেশ কিছু নির্দেশ দিলেন। খেতে খেতেই উঠল স্লোগান ‘জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম্’। নেতাজির সুরে সুর মেলালেন মনগোবিন্দ ও প্রহ্লাদচন্দ্র।
’৪৩-এর মন্বন্তর। বাংলায় উপস্থিত এক ভয়াবহ সংকট। চোখের সামনে খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। সঙ্গে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্তের মতো মারণব্যাধি। কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠছে কঙ্কালসার মানুষে। স্থির থাকতে পারলেন না মনগোবিন্দ। ‘‘আমর হোটেল থাকতে কেউ না খেয়ে মরবে না।’’ দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধলেন প্রহ্লাদচন্দ্র। চালেডালে মিশিয়ে খিচুড়ি চড়ানো হল হাঁড়িতে। শয়ে শয়ে মানুষ সার দিয়ে খেতে বসল। বহু দিন পর ভরপেট খেতে পেয়ে ধন্য ধন্য করল সবাই। ‘‘ওঁদের আশীর্বাদেই আজও টিকে আছে আমাদের হোটেল,’’ চোখ চিকচিক করে ওঠে প্রহ্লাদবাবুর।
কয়েক বছরের মধ্যেই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যার জন্য এত লড়াই, আন্দোলন, এত রক্তক্ষয়, সেই মুহূর্ত। ১৯৪৭। ১৪ অগস্টের রাতে কলেজ স্ট্রিট আলোয় আলো। বাড়ি বাড়ি থেকে ভেসে আসছে রেডিয়োর আওয়াজ। রাত একটা। ভারতবর্ষ স্বাধীন! উল্লাসে ফেটে পড়লেন শহরবাসী। লোকে লোকারণ্য রাস্তা। মুহুর্মুহু উঠছে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি। পর দিন সকালে দল বেঁধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেরল পদযাত্রায়। পরনে পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় গাঁধী টুপি। হোটেলের সামনেই পতাকা তুললেন দুই ভাই। কিছু ক্ষণের মধ্যেই এক দল স্বেচ্ছাসেবক এসে হাজির। শোভাযাত্রা শেষে খাওয়াদাওয়া সারতে এসেছে। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, ‘‘আর হিন্দু হোটেল নয়। ভারত এখন স্বাধীন। আজ থেকে নাম হোক ‘স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল’।’’
সে দিনের স্মৃতিচারণায় আজও চোখ ছলছল করে প্রহ্লাদবাবুর। দাদা নেই। ছেলে আর নাতিদের নিয়ে এখনও বজায় রেখেছেন সে দিনের ঐতিহ্য। এই বয়সেও ঘণ্টাখানেকের জন্য হলেও রোজ দোকানে বসেন। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন বাজার করতে। হোটেলে মার্বেল বাঁধানো পুরনো কাঠের টেবিল। মাটির ভাঁড়ে জল। কলাপাতায় খাবার। দেওয়াল জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি।
এখনও প্রতি বছর স্বাধীনতার দিন নতুন করে সেজে ওঠে স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল। দেওয়ালে পড়ে রঙের পোঁচ। ১৪ অগস্ট রাতে নতুন করে লেখা হয় হোটেলের নাম। তাতে তুলির প্রথম আঁচড়টি কাটেন প্রহ্লাদচন্দ্র নিজে। ১৫ অগস্ট সকালে পরিবারের সব সদস্য হাজির হন হোটেলে। পতাকা তোলেন প্রহ্লাদবাবু। ছোট্ট বক্তৃতায় মনে করিয়ে দেন সেই সব দিনের কথা। স্বাধীনতার দিনে হোটেলে রান্না হয় ‘ইনডিপেনডেন্স ডে স্পেশাল’ পদ। সেই খাবার পরিবেশন করতে করতে হোটেলের কর্মী অনাদি বলেন, ‘‘আজ ৫০ বছর এই হোটেলে কাজ করছি। ছেড়ে যাব কোথায়? ‘স্বাধীন ভারত’-ই আমাদের ঘরবাড়ি!’’