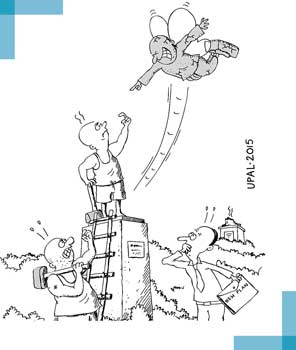চেনা গল্প অচেনা মোচড়
দুর্গা ও রেলগাড়ি
ঈপ্সিতা হালদার
বুক ধুকধুক করিতেছে দুর্গার। সেজঠাকুরপোর খাওয়া হইতে না হইতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। গয়াকাশী, সে অনেক পথ। রেলগাড়িতে যাইতেই এক রাত্তির এক দিন। গত সাত আট দিনের মধ্যে তিনি বহু বার গুছাইয়াছেন ফেতরা থানে তৈরি পুঁটুলিখানা, তবু আর এক বার এক মুষ্টি আতপ, কাঁচাকলা ও একখানি নোনা আতা তিনি গুছাইয়া লন। দালানের এই তরফে এখন কেউ কোত্থাও নাই। যাত্রা শুরুর আগে সে হেঁট হইয়া তক্তপোশের নীচ হইতে এই সরা ওই কুলো ওই মেজননদের শ্বশুরবাড়ি হইতে আসা পাটের গাঁটরি, যজমানের দেওয়া থালাবাটি সবের অন্তরাল থেকে বের করে আনে একখানি টিনের কৌটা।
বিয়ের সময় তো কিছুই দিবার ছিল না বাপের, দুর্গার নিজের বলিতে আর কী ছিল, খালি লীলার কলকাতা থেকে আসা বউদির দেওয়া একটা গোল হাত-আয়না, যার পিঠে পুঁতি আর কাচ বসানো। এত দিন পর, যখন পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া রুক্ষ চুলের স্মৃতি আর যেন পিঠে নাই, এমনকী স্বামী সেই যে এক বার বলিয়া ফেলিয়াছিলেন ‘ও তো নিজে চুল বাঁধতে পারে না, তোমরা তো একখানা খোঁপা করে দিতে পার বিকালে’, সে শুনে সব্বার কী হাসি কী হাসি, সেও যেন মনে পড়িতে চাহে না।
কিন্তু এই আরশি আরশি আরশি। সুদর্শন পোকা আসিয়াছিল গত ভাদ্রের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে, দুর্গা বলিয়াছিলেন, সুদর্শন সুদর্শন, আরশিখানি তুমি লও, কিন্তু পোকা বোঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাই দুর্গা তড়বড় করিয়া চলেন, খিড়কির দরোজা দিয়া বাঁশঝাড়, আকন্দের ঝোপ, তেঁতুলের বন পার হইয়া যেন তিনি সেজঠাকুরপোর গরাস মাখিবার চেয়েও দ্রুত ঘাটলায় যাইবেন ও ফিরিয়া আসিবেন। হাতের আরশিখানা মাঝপুকুরে ছুড়িয়া ফেলিতে, আচমকা আঘাতে পানা শতভাগ হইয়া যায়, তার পর বহু ক্ষণ লয় ঢাকিয়া লইতে, গোল ফ্রেমে আঁটা একখানি কিশোরী বধূর মুখ। অবশ্য তত ক্ষণে খোঁজাখুঁজি শুরু হইয়াছে। — কী গো খুড়িমা, রেলগাড়ি কি তোমার কথা শুনে চলবে? সে কয়লা গিলে চলে আর দত্যিদানোর মতো শিঙে ফোঁকে।
দুর্গা চলিতেছেন বাবা বিশ্বনাথের থানে। রেলগাড়ি চড়িয়া। জলতেষ্টায় প্রাণ টা টা করিতেছে। যা ঝিমদুপুরে জানলা দিয়া মিষ্ট লেবুফুলের গন্ধে উপশম হইত, তা এই ধাতুর গন্ধে অজানা ধকধকিতে ধাক্কা খাইতে খাইতে এতগুলি নিশ্বাসে ভেপসাইয়া ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, দুর্গার অস্বস্তি নাই। এই ভিড়, পুঁটলি-পোঁটলা, জানলা দিয়া চাহিলে মাথা ঘুলাইয়া ওঠা, খর ও মোলায়েম কণ্ঠস্বরগুলিতে কী যেন কী হইবে কাশীধামে, এই ভাবিয়া তিনি একেবারে টইটম্বুর করিয়া উঠিলেন।

ছবি: সায়ন চক্রবর্তী।
আসিয়া, সকাল-সন্ধ্যা একত্র কীর্তন আর দশাশ্বমেধ ঘাটে আসাযাওয়া করিতে হইবে ভাবিয়া মন শিহরিত হইয়া উঠিল। এত কিছু আছে এই পৃথিবীতে? এই কলরোল, বাঁকা বাঁকা গলি, চিলতে রৌদ্র, ঠান্ডা অন্ধকার, গুমগুম বাজনা আর ঘণ্টার রোল, উফ এত কপ্পুরের গন্ধ ঘিয়ের প্রদীপ চূড়ার মতো সন্ধ্যার না আলো না অন্ধকারে জ্বলে ওঠা— দুর্গা ভাবিতে পারিয়াছেন কখনও? তিনি ধূলির উপর বসে মাথাটি নোয়ান, লোকের পুণ্যি লোকে করে, ঘাটে যাওয়ার পথে কেউ, বেশির ভাগ ঘাট হইতে ফিরিবার পথে। আর ভোজ্যের কী সমারোহ! কী আসিয়া যায় যদি তাঁহাদের বিধবাপট্টিতে সেই সিদ্ধ শস্তা আতপ কাঁচাকলা কিংবা সিদ্ধ আর দুইটি বেগুন। যে-সব স্বামীহারাদের রসনা বলিতে মুখের ভিতরে সেই মাপে এই একখানি পোড়া কাঠ, তাহাদের জন্য কাশীর দেবতা গলিতে গলিতে কোনায় কোনায় তেল ঘি চবচবে কচুরি-পুরির সম্ভার সাজাইয়া রাখেন যাহাতে সেই সব আধাময়লা থান পরা অপুষ্টিতে ক্ষীণ ভূতগ্রস্ত মহিলারা এই সব রন্ধনবাষ্প নাসিকা দিয়া গিলিয়া লইতে পারে। দুর্গা তাই মহানন্দে চলেন, সম্মোহিতের প্রায়। এই বজবজে ড্রেন, অলিতে-গলিতে বদ্ধ বায়ুু, পায়ের ফাটায় লাগিয়া যাওয়া ক্লেদ, সবের পরে গঙ্গা, যেন উঁহার নিজের। বরং না তাকাইয়া দুর্গা এক ঘটি হইতে অন্য ঘটিতে লস্যি ঢালিবার শব্দ শুনেন। আর কল্পনা করেন, ফেনিল।
ঠেলা দেয় অন্য বিধবারা। এ ভাবে গেলে অবেলায় ক’জন ভিক্ষে দেবে? তুমি হাঁ করে গিলচ দাঁড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! কথকঠাকুর এসে যে শুরু করে দেবে পাঠ।
লোকটিকে দেখিয়া বার বার চোখে জল আসে দুর্গার। বাবাও কী এই রকম পাঠ পড়াইতে আসিতেন? আর স্নান সারিয়া গামছা গায়ে জড়াইয়া ঘটিটি গঙ্গাজলে ভরিয়া ওই রকম হাঁটিয়া উঠিয়া আসিতেন ঘাট বরাবর, তার পর লোকটির মতোই ডাইনে বাঁকিয়া ওই দিকে ওই নিচু দরোজায় মাথা হেঁট করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেন? ওই দরোজার ও-পারে কী? উঠান? মা কি উঠানের প্রান্তে রান্না করিতেন? এই লোকটির বউয়ের মতো? ওখানে কি অপু বসিয়া আছে, দোত-কলম দপ্তর সাজাইয়া? এত স্পষ্ট অপুকে দেখিতে পাইয়া দুর্গা প্রায় কড়া নাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন দরোজার, কিন্তু না, ফিরিয়া আসিলেন।
একের পর এক পা ঘাটের দিকে যাইতে থাকে। দেখিলেই দুর্গা বুঝিতে পারেন, কে এল কুমড়ার ছক্কা আর ডাল রাঁধিয়া, আহা কাহাদের বধূটি চলিতে পারে না, আর কে ফিরিয়া গিয়া খাইবে ঘি আর শাকভাজি। দুগ্গা ইন্দিরঠাকরুনই। কেহ যাচে না, কেহ পোঁছে না, দীন চরণের শব্দ উঠে কি উঠে না। দুর্গা গঙ্গার দিকে তাকান, সেখানে কাহারও বাধা নাই, বাধ্যবাধকতা নাই। ঝিক ঝিক কাচের লহরী। বা কষ অন্ধকার। কিন্তু দুর্গা জানিতেন, এ সকল তাঁর। সকলই তাঁর।
এক দিন একখানা পোস্টকার্ড আসে। দুর্গাসুন্দরী দেবীর নামে। কথকঠাকুর পড়িতে থাকেন। অপু লিখিয়াছে, শোকে সমাহিত সে অবশেষে শান্তি পাইয়াছে গঙ্গার উৎসস্থলের নিকটে যাইয়া। সেথা যেন বা মহাদেবের ধূম্রজটা হইতে নির্গত হইয়া কলকলরোলে সমগ্র ভূমণ্ডল ধৌত করিয়া নামিতেছে পতিতোদ্ধারিণী। তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি পায়ে হেঁটে, রেল থেকে, ব্রিজের উপর গুমগুম শব্দে, ইঞ্জিনের ধূম উদ্গিরণে।
মাঘী পূর্ণিমার দিনশেষে রাত্রি হইতে দুরন্ত মাঘের শীত উপেক্ষা করিয়া লোকে ঘাটের দিকে ছুটিতেছে। জুটিতেছে বিধবার পাল। কিন্তু দুর্গাসুন্দরী হাঁটিতেছেন উলটা দিকে। সকাল সাতটা দশে গয়াকাশীর ইস্টিশানে ট্রেন দাঁড়াইবে পাঁচ মিনিট। এ বার হরিদ্বার। ডিসট্যান্ট সিগনালের আলো দূরে মিলাইয়া যায়।
epsita.halder@gmail.com
বিনোদনের ব্যাকরণ বদল
ঘরে ঘরে শালগ্রাম শিলা সদৃশ কালো টেলিফোন তখন কৌলীন্য হারাচ্ছে। ক্ষণিকের অতিথি ‘পেজার’কে ভাতে মেরে সেলফোন এসে গেছে, মূলত বিত্তবানদের হাতে। তখনও ইনকামিং কল চার্জেব্ল কিনা! গানের জগতে সুমন, নচিকেতা, অঞ্জন, শিলাজিৎ নব্বই দশকের প্রথমার্ধে সবার ঝুঁটি ধরে নেড়েছেন, সেকেন্ড হাফে বাংলা ব্যান্ডের নবজন্ম হচ্ছে। কলকাতার হলিউড-ভক্তরা ধর্মতলায় চুটিয়ে ইংরেজি ছবি দেখে যাচ্ছে সেই সব সিনেমা হল-এ, যেগুলো আর বছর দশেকের মধ্যেই জামাকাপড়ের দোকান বা হোটেল হয়ে যাবে।

বাংলা কমার্শিয়াল থিয়েটার বা বোর্ড থিয়েটারে তখন অমাবস্যা নামছে ধীরে ধীরে। উত্তর কলকাতায়, শ্যামবাজারের থিয়েটারপাড়ায়, ক্যাবারে-কণ্টকিত বড়দের এবং স্টার-কেন্দ্রিক পারিবারিক অথচ পেশাদার নাটক আইসিইউ-তে ঢুকে পড়ছে ক্রমশ। দক্ষিণ কলকাতায় তখন এই বোর্ড থিয়েটার হত শুধুমাত্র ‘নহবত’ খ্যাত তপন থিয়েটারে। বাংলা চলচ্চিত্রের দিকপালরা অনেকেই গত, আর বাংলা ছবির দুঃসময়ের সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের ন্যাচারাল ডেথও প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কারণ, চলচ্চিত্রের চরিত্রাভিনেতারাই তাঁদের সুনামে ও প্রতিভায় থিয়েটারপাড়ার বেশিটা ভরিয়ে রাখতেন।
যদিও টেলিভিশনের মাধ্যমে অভিনেতাদের স্টারডম পাওয়ার শুরু আশির দশকে, প্রথম টেলিভিশন সুপারস্টার সব্যসাচী চক্রবর্তীর হাত ধরে, কিন্তু দূরদর্শনের বাইরে বেসরকারি চ্যানেলের পদার্পণ এই দশকেরই মাঝামাঝি। ভারী একটা রেষারেষিও চালু ছিল। সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল, প্রথম দিকে তাদের মূল শিল্পীদের অন্য চ্যানেলে রিপিট করতে চাইত না। কেব্ল চ্যানেল শহর ছেড়ে মফস্সল, এবং আরও গভীরে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অভিনেতারা বড় পরদার ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ ইমেজ ছেড়ে, মানুষের বসার ঘরের সঙ্গী হয়ে উঠলেন। তাঁদের প্রতি মানুষের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বদলে গেল আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি অন্তরঙ্গ ভালবাসায়।
আর এই সময় থেকেই সিনেমা, টেলিভিশন, স্টেজ— এই তিন ভিন্ন বিনোদনমাধ্যম সম্বন্ধে, অভিনেতা এবং দর্শকদের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আর আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণাটা আবছা হয়ে আসতে লাগল। অর্থাৎ, কিছু সিনেমায় এবং বেশির ভাগ টেলিভিশনের কাজে একটু অতিনাটকীয় অভিনয় সাড়া ফেলতে লাগল। আর নাটকের ক্ষেত্রে একটু সিনেম্যাটিক অভিনয় জায়গা করে নিল।

নব্বইয়ের দশকের বিখ্যাত নাটক ‘দায়বদ্ধ’র একটি দৃশ্য। প্রযোজনায় ‘সায়ক’ নাট্য দল।
আর, সাধারণ থিয়েটার-কর্মীদের সামনে রোজগারের রাস্তা হিসেবে খুলে যেতে লাগল টিভির খিড়কি-দুয়ার। আর হয়তো সে কারণেই, গ্রুপ থিয়েটারও অ্যাদ্দিনের প্রথা ভেঙে এ বার দলের বাইরে থেকে অভিনেতা নেওয়া শুরু করল। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। শুধু তত্ত্বে আর আদর্শে দল চালানো শক্ত হচ্ছিল। তবে এর ফলে অনেক দলেরই পেশাদারিত্ব বাড়লেও, স্বতন্ত্র জীবনদর্শন অদৃশ্য হচ্ছিল।
এক দিকে শহরতলির যে দর্শকরা বোর্ড থিয়েটার দেখতে আসতেন দলে দলে, টেলিভিশনের নব সুস্বাদ তাঁদের অলস আর বিমুখ করতে লাগল। অন্য দিকে কমার্শিয়াল থিয়েটারে স্টারদের সামলানোর খরচা টিকিট বিক্রির চেয়ে বেড়ে যাওয়ায়, সিনে-অভিনেতারা ‘ওয়ান ওয়াল’ বলে একটি নতুন ধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলেন। এটা আসলে যাত্রা-ই। শুধু নক্ষত্রখচিত। কিন্তু চারদিক নয়, তিন দিক খোলা। নিখাদ গ্রামীণ যাত্রাশিল্প পড়ল বিপাকে। নতুন ধরনের উন্নত আলো, সাউন্ড সিস্টেম এবং টেকনিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রথাগত যাত্রাশিল্পীরা হিমশিম খেতে লাগলেন।
এর পর এল সেই অমোঘ মেগাসিরিয়াল। জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনেতা ও কলাকুশলীদের স্থিতিশীল আর্থিক নিরাপত্তার রমরমা। এ ভাবেই, গোটা নব্বই দশক জুড়ে বিনোদন জগতের অর্থনীতির একটা বিবর্তন ঘটতে লাগল নিঃশব্দে।
এই নব্বইয়ের দশক আমার কাছে এসেছিল ‘মুক্তির দশক’ হিসেবে। ’৯০-এর ডিসেম্বর মাসে পেট চালাতে একটা অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরি বাগিয়েছিলাম। ’৯৩-এর সেপ্টেম্বরে সেটা ছেড়ে দিলাম, কোনও আর্থিক নিরাপত্তা বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াই। বড় অভিনেতা হওয়ার আশায় নয়, শুধুমাত্র অভিনয় করে কোনও মতে পেট চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। কারণ তত দিনে এটুকু বুঝেছি, আমি জীবনে আর কিছুই ভালবেসে করিনি কখনও। ম্যানেজার চোখ পাকাবেন বলে হেড অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে, সেটা খেতে খেতে রেজিগনেশন লেটার লিখে ওঁর হাতে দিয়ে এলাম। এর পর একে একে পেরোলাম বোর্ড থিয়েটার, ওয়ান ওয়াল, মেগাসিরিয়াল। পায়ের তলায় প্রথম জমি পেলাম ‘পারমিতার একদিন’-এ। মানে, আমার অভিনীত প্রথম যে ছবি বাণিজ্যিক সাফল্যের মুখ দেখল। সেটা ২০০০ সাল। স্বপ্নহীন, পরিকল্পনাহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ইভোলিউশনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পা রাখলাম পরের শতাব্দীতে। নিরাপত্তাহীনতার দশ দশটা বছর। নব্বইয়ের দশক তার সমস্ত ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে, ইনসিকিয়োরিটির উৎসবের মধ্য দিয়ে আমায় জীবন্ত রেখেছিল।
বহু বোহেমিয়ান তালেবরকে এই দশকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। বোহেমিয়ান হওয়ার আনন্দে এবং রোম্যান্টিসিজমে যাঁরা কলকাতা শাসন করেছেন সেই সময়। এর পরবর্তী দশকের সবাই কিন্তু তাঁদের বাল্যলীলা থেকেই অনেক বেশি ফোকাস্ড। পরিকল্পনা, কেরিয়ার, স্বপ্ন, উচ্চাশা সম্বন্ধে অনেক বেশি দায়িত্বশীল। মাধ্যমিকের পর সিনেমা দেখার লিস্ট না বানিয়ে, তারা সফ্টওয়্যার কোর্স করে ফেলে। ছুটিতে বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে যায়।
তেমন দিকপাল বাউন্ডুলে কোনও দিনই ছিলাম না আমি। কিন্তু উচ্চাশাহীন জীবনের এই কার্নিভাল যাঁরা বিনা অনুতাপে কাটাতে পেরেছেন, তাঁদের কুর্নিশ করার সশ্রদ্ধ বোকামিটা ছিল আমাদের অনেকেরই। এবং, যদিও, কিন্তু... নব্বইয়ের দশকই সম্ভবত সে মূর্খতা উদ্যাপনের শেষ দশক।
অবশেষে ভারতকে লিজার্ড ফ্লু মহামারী থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত ৪ জানুয়ারি দেশে প্রথম এইচ সিক্স এন সিক্স ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি অসুখটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার পর গত আড়াই মাসে দেশে অন্তত ৫০ কোটি মানুষ মারা গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্ছ্বাসের সীমা নেই। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হৃষ্ট চিত্তে জানিয়েছেন, এই মহামারী এসে যেহেতু দেশের প্রবল জনসংখ্যা এক ধাক্কায় কমিয়ে দিয়েছে, তাই আমাদের বেকার সমস্যা ধুয়ে মুছে সাফ। সমীক্ষা জানাচ্ছে, দেশের বেকার জনসংখ্যার ৮০% এই ফ্লুয়ে সাবাড় হয়ে গিয়েছে। ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রায় ৬০% ও নামীদামি সংস্থার চাকুরেদের প্রায় ৪০% ফ্লুয়ে জীবন হারিয়েছেন। কারণ, বেকাররা অনেক ক্ষণ ক্লাবে আড্ডা দেন বা মাঠে-ঘাটে-পার্কে উদ্দেশ্যহীন ঘোরেন।

এ সব জায়গায় টিকটিকি-গিরগিটি বেশি। তাই সংক্রমণের আশঙ্কাও বেশি। ঠিক তেমনই ছোট অফিসের দেওয়ালে টিকটিকি ঘুরলেও, দামি অফিসে চড়া এসিতে টিকটিকি থাকে না। তবে, এত মানুষ এক সঙ্গে মারা যাওয়ায় অনেক পদ খালি হয়েছে। এখন অবশিষ্ট জনসংখ্যার বেকারদের সে সব পদে উচ্চ বেতনে নিয়োগের পরেও বহু পদ খালি পড়ে থাকবে। সেগুলি কবে পূরণ হবে, কম কর্মচারী দিয়ে কাজ করলে দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হবে কি না, সরকারই গ্রাম-শহরে অসুস্থ টিকটিকি ও গিরগিটি ছড়িয়ে ইচ্ছে করে রোগের সৃষ্টি করেছিল কি না— সাংবাদিক ও বিরোধীদের এই সব প্রশ্ন ও অভিযোগ নস্যাৎ করে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাতৃভাষায় বলেন, ‘সরকার লাভ ও ক্ষতি দুটোকেই ওয়েলকাম করে।’ এবং জানালেন, এই বিশেষ সময়ে লেখা তাঁর উপন্যাস ‘টিকটিকিদের সন্ধানে’র ইংরেজি অনুবাদটি নোবেল পুরস্কার পাবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি মৃতদের আত্মার শান্তিকামনা করে জীবিতদের উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছেন।
লিখে পাঠাতে চান ভবিষ্যতের রিপোর্ট? ঠিকানা: টাইম মেশিন, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১। অথবা pdf করে পাঠান এই মেল-ঠিকানায়: robi@abp.in