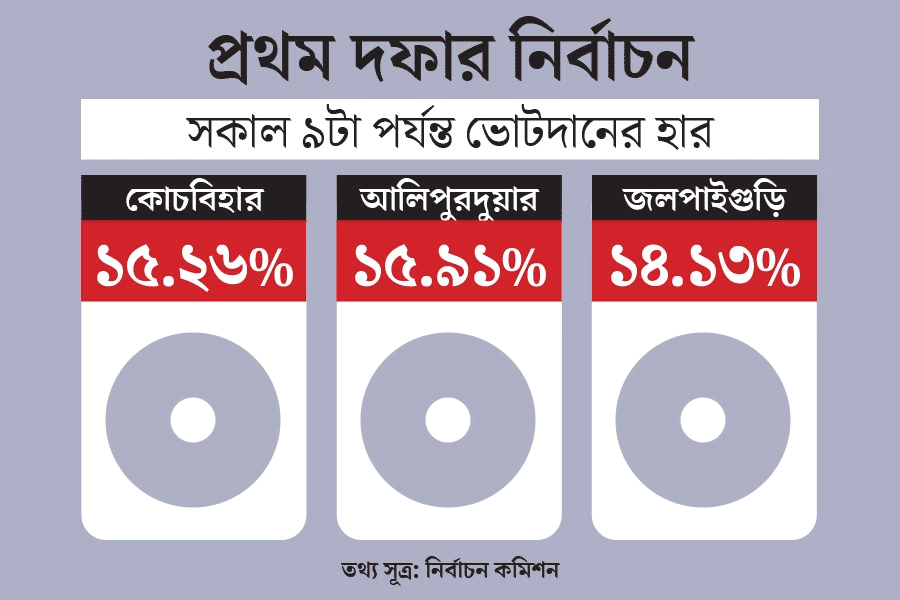লীলাবতী
অগণিত কোমল কাহিনির জন্মদাত্রী হয়েও তাঁর জীবন কাঠিন্যে ভরা! গত রবিবার ছিল লীলা মজুমদারের মৃত্যুদিবস। শ্রদ্ধার্ঘ্যে শ্রীজাত।‘অক্ষত হৃদয়ে আমার তেইশ বছর বয়স হয়নি। ... আমার একজনকে ভালো লাগত। এবং আমাদের বাড়ির সকলেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। খুব যা-তা ছিল না সে, মাথায় লম্বা, রং ফর্সা, ব্যবহার মিষ্টি, সুকুমার, কমনীয়, সাহিত্যানুরাগী, সদ্বংশজাত, আমার চেয়ে দু-বছরের বড়। আমি মনে মনে মুগ্ধ। ... কিন্তু যতই দিন যায় ততই বুঝি সে বড় ছেলেমানুষ, ব়ড় কোমল, আমার আরো কড়া ওষুধ দরকার।’ ডাইরি আরও বলছে, ‘চলে না গিয়ে উপায় ছিল না। ... ট্রেন ছেড়ে দিল, আমি আমার পুরনো জীবন থেকে শিকড়গুলো উপড়ে নিলাম।’ সেদিনকার সেই সুপরিণত, আত্মবিশ্বাসী, বেপরোয়া মেয়েটিই লীলা। লীলা মজুমদার। শিকড় উপড়ে নেবার খেলায় জীবন যাকে কোনও দিনও হারিয়ে দিতে পারেনি। কারণ এমন কাজ তাঁকে একবার নয়, বহুবার করতে হয়েছে।

আকাশবাণীতে। ছবি: পরিমল গোস্বামী।
ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম থেকে... জানলায় দেখা যাচ্ছে বছর তেইশের এক যুবতীর মুখ, প্রত্যয়ী, অথচ বিষণ্ণ। খুব দ্রুত কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া প্রয়োজন তার।
এই শহরটা বার বার তাকে ব্যথা দিচ্ছে। আর এবারের ব্যাথার উপশম বোধহয় বিচ্ছেদেই লুকনো।
মেয়েটির ডাইরি বলছে, ‘অক্ষত হৃদয়ে আমার তেইশ বছর বয়স হয়নি। ... আমার একজনকে ভালো লাগত। এবং আমাদের বাড়ির সকলেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। খুব যা-তা ছিল না সে, মাথায় লম্বা, রং ফর্সা, ব্যবহার মিষ্টি, সুকুমার, কমনীয়, সাহিত্যানুরাগী, সদ্বংশজাত, আমার চেয়ে দু-বছরের বড়। আমি মনে মনে মুগ্ধ। ... কিন্তু যতই দিন যায় ততই বুঝি সে বড় ছেলেমানুষ, ব়ড় কোমল, আমার আরো কড়া ওষুধ দরকার।’ ডাইরি আরও বলছে, ‘চলে না গিয়ে উপায় ছিল না। ... ট্রেন ছেড়ে দিল, আমি আমার পুরনো জীবন থেকে শিকড়গুলো উপড়ে নিলাম।’
সেদিনকার সেই সুপরিণত, আত্মবিশ্বাসী, বেপরোয়া মেয়েটিই লীলা। লীলা মজুমদার। শিকড় উপড়ে নেবার খেলায় জীবন যাকে কোনও দিনও হারিয়ে দিতে পারেনি। কারণ এমন কাজ তাঁকে একবার নয়, বহুবার করতে হয়েছে।
আপাতত ট্রেন তাঁকে নিয়ে চলেছে কলকাতা থেকে দূরে... কোথায়? তার উত্তর নয় পরে জানা যাবে।
এই মুহূর্তে এ-ঘটনার বেশ কিছু বছর পরে চলে যাওয়া যাক, যেখানে লীলাকে আবারও নিজের ভিত খুঁড়ে ফেলতে হচ্ছে শক্ত হাতে।
যে-মানুষটির উপস্থিতি রীতিমতো উপভোগ করতেন তিনি ছোটবেলায়, যে-মানুষটির রসবোধ চারিয়ে নিতেন নিজের মধ্যে, সবচাইতে ভালবাসার কয়েক জনের তালিকায় উপরের দিকে, সেই মানুষটির সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ তো বন্ধই। সেই মানুষটিই মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর তিনিও সাধলেন না বিশেষ। মানুষটি স্বয়ং তাঁর পিতৃদেব প্রমদারঞ্জন রায়।
তখন তিনি লীলা রায়। আর রায় থেকে মজুমদার হয়ে ওঠার কালেই এই বিপত্তি, যা প্রমদারঞ্জনের জীবৎকালে ঘোচেনি।

তখনকার নাম করা ডাক্তার সুধীন কুমার মজুমদার, পারিবারিক মেলামেশায় গোড়া থেকেই তাঁকে মনে ধরেছিল যুবতী লীলার। পছন্দ অবশ্য উভয় দিকেই ছিল। কিন্তু পাত্র হিন্দু। বেঁকে বসলেন গোঁড়া ব্রাক্ষ্ম প্রমদারঞ্জন। সম্ভবত তিনি বোঝেননি, তাঁর মেধাবী, গৃহকর্মনিপুণা, সুলেখনীর অধিকারী কন্যাসন্তানটি তাঁরই মতো জেদি। হয়তো-বা তাঁর চেয়েও কিছু বেশি।
বিয়ে হল সই করে, সেদিনকার লীলা রায় হয়ে উঠলেন সকলের লীলা মজুমদার আর সেইসঙ্গে বন্ধ হল বাবার মনে যাতায়াত করার রাস্তা।
লীলা লিখছেন, ‘বাবা আমাকে ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে সব কথা ভুলে দুজনে গেলাম বাবাকে প্রণাম করতে। তিনি আমাদের দেখেই ঘর থেকে উঠে চলে গেলেন। শুধু ঘর থেকেই নয়, আমার জীবন থেকেই সরে পড়লেন। তারপর আঠারো বছর বেঁচে ছিলেন, কখনো আমার বা আমার ছেলে-মেয়ের দিকে ফিরে চাননি।... আঠারো বছর পরে যখন তিনি চোখ বুজলেন, আমি এতটুকু ব্যক্তিগত অভাব বোধ করিনি। যে অভাব, যে বেদনা ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে টের পেলাম।’
এই ছিলেন আদত মানুষ লীলা। নীতিবোধ আর আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যিনি কখনও কোন আপস করেননি। কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নয়, এমনকী, যেমন দেখা গেল, নিজের বাবার সঙ্গেও নয়।
যেটা ভাবায়, তা হল এই যে, যে-শিল্পীর কলম থেকে এত পেলব, এত কল্পনাপ্রবণ, এত আদুরে আর এত ফুরফুরে সমস্ত লেখা বেরিয়েছে, তাঁর ভেতরকার ভিতটা যে এইরকম পোক্ত আর অনড় হতে পারে, অনেক সময়েই তা আমরা ভেবে উঠতে পারি না। তাঁর অন্তঃকরণের সমস্তটুকুকে তাঁর সৃষ্টি দিয়েই মাপতে চাই।
সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের সৃষ্টি তাঁর চারিত্রিক পেলবতারই প্রতিফলন, তাঁর স্বপ্নময় ভাবনারই প্রকাশ। কিন্তু তার আড়ালে এই রকম কঠোর নীতির একজন মানুষ লুকিয়ে আছেন, তাঁর জীবনকে না-জানলে সে-কথা বোঝার রাস্তা নেই।
কিন্তু এসব তো অনেক পরের কথা। আমরা যারা আমাদের সক্কলকার ঠাকুমার মুখটি বসিয়ে নিয়েছি লীলা মজুমদারের মুখে আর আবাল্যকাল হাঁ করে তাঁর কাছ থেকে একের পর এক মজাদার আজগুবি সমস্ত গল্প শুনেছি, তাদের সেই আদরের পাতানো ঠাকুমার রূপকথার ভিতটা কোথায় তৈরি হয়েছিল?
তাঁর নিজের জীবন নিয়ে নিজের-বলা গল্প পড়লে বোঝা যায়, শৈশবের শিলং শহরের বাস, সে-শহরের বেড়ে ওঠার দিনগুলো তাঁর পিছু ছাড়েনি কোনও দিনও। তিনি ছেড়ে এসেছেন সে-শহর, হয়ে গিয়েছেন কলকাতার, খানিকটা শান্তিনিকেতনেরও বটে। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ দীর্ঘায়ু জীবনে পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট সাহেবি কেতার শহরটিকে বরাবর মনে রেখে দিয়েছেন তিনি।
‘পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে কাঁকড় বিছানো পথ দিয়ে নেমে বারান্দায় পৌঁছতে হত। একহারা লম্বা বাংলো, সামনে টানা বারান্দা, তার কাঠের রেলিং। বাড়ির তিনদিক ঘিরে বৃষ্টির জল যাবার জন্য নালা কাটা। তার ওপর দুটি চ্যাপ্টা পাথর ফেলা। তার ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। বারান্দার ছাদ থেকে তারের বেড়ায় অর্কিড ফুল ঝুলত। তাদের তলায় সবুজ কাঠের বাক্সে জেরেনিয়ম ফুল ফুটত। লোকে এমন বাড়ি স্বপ্নে দেখে।’
এই ছিল শিলং-এ ছোট্ট লীলা আর তার দাদা-দিদির স্বপ্নের বাড়ি ‘হাই উইন্ডস’। ভাড়া নিয়ে সপরিবার এই বাড়িতেই কর্মসূত্রে আট বছর কাটিয়েছিলেন প্রমদারঞ্জন, ১৯১১ থেকে ১৯১৯। সেই আট বছরে লীলার মনে তৈরি হয়ে যায় রূপকথার রাজ্যের এক নিজস্ব ছক, সারাজীবন যার নকশা বুনে গিয়েছেন তিনি।

মেম শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে ফিরিঙ্গি বান্ধবীদের সঙ্গে ক্লাস করা, পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে দিদির সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরা, বর্ষা থেকে শীতে পাল্টাতে থাকা শিলং-এর আশ্চর্য রূপ, বাড়িতে কাজ করতে আসা খাসিয়া মেয়েদের মুখ থেকে সুযোগ পেলেই আজগুবি সব গল্প শোনা, লাইব্রেরি আর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে একরাশ ইংরেজি বই জড়ো করে এনে গোগ্রাসে পড়া আর এসবের বাইরে একা একা ঘুরে বেরিয়ে প্রকৃতির ছোটখাটো মজা আর ভাললাগা কুড়িয়ে বেড়ানো। এই ছিল ছোট্ট লীলার সেই আট বছরের রোজনামচা।
গল্পের ভূত তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেখানেই, মাথাতেই বাঁধতে শুরু করল মজার মজার সব গল্প। ভাইবোনদের, দাদাদিদিদের শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন। পাশাপাশি লুকিয়ে লুকিয়ে একটা খাতায় লিখেওছিলেন কয়েকখানা। কিন্তু ফাঁস হয়ে যেতেই অভিমানে ছিঁড়ে ফেলে দেন।
অবশ্য আবার তাঁকে ফিরে যেতে হয় খাতার কাছেই এবং শিলং-এ থাকাকালীনই, ওই ছোট বয়সেই সম্ভবত তিনি টের পেয়েছিলেন, তাঁর সারা জীবনের কাজ হতে চলেছে এই লেখালিখি। আর হ্যাঁ, যে-ভাষায় তিনি ছোট থেকে সড়গড়, সেই বিলিতি ইংরেজিতে নয়, তাঁর মায়ের মুখের ভাষা, বাবার মাটির ভাষা বাংলাতেই।
শিলং-এর আরও একটি বিকেলবেলা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। আর সেই বিকেলে যে সম্পর্কের সূত্রপাত, তার চিহ্ন তিনি বহন করেছিলেন আমৃত্যু।
সেই মানুষটি সম্বন্ধে লীলা এক কথায় লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় এমন সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছে।’ তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি সপরিবার শিলং বেড়াতে গিয়েছিলেন যখন, বাবার হাত ধরে ছোট্ট লীলাও গিয়েছিল কবিকে দেখবে বলে।
সেই তাঁর রবীন্দ্র-সংসর্গের শুরু। পরবর্তীতে খোদ কবিই তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, সে কাহিনি সকলেরই জানা।
শান্তিনিকেতনের কাজে মেতে থাকা, পরে মন-না-লাগায় সে-কাজ ছেড়ে চলে আসা, ফের শান্তিনিকেতনেই পাকাপাকি থাকার জন্য বসতবাটি তৈরি করা... মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতনের তৎকালীন নির্ঝ়ঞ্ঝাট প্রাকৃতিক আশ্রয়ের ছায়া তাঁকে বার বার টেনেছিল।
রবীন্দ্রনাথের বিশালতার সঙ্গে সারল্যের যে-অভাবনীয় মিশ্রণ, তা লীলার ভাল লাগত প্রথম দিন থেকেই। আর টেনেছিল নীতির পথে অবিচল থাকবার পণ। লীলার ভিত তৈরিতে সেও কিছু কম কাজে লাগেনি।
তবে এসবের অনেক আগে দুটি মানুষের প্রভাব ও একটি কাগজ লীলার মজ্জায় ও মননে চিরস্থায়ী রূপ নেয়। ইতিমধ্যেই কিশোরী লীলা ঢুকে পড়েছেন তাঁর গল্প বুনে চলার নেশায়।
লীলা। লীলা রায়। সম্পর্কে যিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাইঝি আর স্বয়ং সুকুমার রায়ের ছোট বোন। এহেন মানুষের ভবিষ্যৎ বোধ হয় জন্মেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।
লীলার শৈশবে মা’র চিকিৎসা করাতে বাবা সকলকে নিয়ে এসে উঠেছিলেন গড়পাড়ের বিখ্যাত বাড়িটিতে। একতলায় প্রেস, দিনরাত লোকজনের যাওয়া আসা। গম্ভীর অথচ সুরসিক মেজ জ্যাঠামশায়ের কাগজ নিয়ে মেতে ওঠা, যে-কাগজের নাম ‘সন্দেশ’।
লীলা মজুমদারের কথায়, ‘নিচে প্রেস চলত, তার একটানা ঝমঝম শব্দ কানে আসত, মনে হত বাড়িটা বুঝি দুলছে, যে কোন সময় পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাবে। সে বাড়ির রোমাঞ্চের কথা মুখে বলার সাধ্যি নেই আমার’।
সেই সময়েই একদিন ‘সন্দেশ’-এর প্রথম সংখ্যা হাতে করে ভিতরমহলে ঢুকে এলেন উপেন্দ্রকিশোর। অজান্তেই শুরু হয়ে গেল বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়, পরে লীলা যার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়বেন।
অমন সুন্দর পত্রিকা দেখে লেখার লোভ খুবই হয়েছিল তাঁর, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। ওই যে, আত্মমর্যাদা বোধ! ছোট থেকেই তা বড় তীব্র ছিল লীলার।
চারপাশে দেখা জীবন আর তার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে ছোটদের জন্য এক নতুন পৃথিবী গড়ছিলেন তিনি তখন। মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলেন, লিখলে ছোটদের জন্যই লিখবেন, ছোটদের জন্যই বাঁচবেন। আর এইখানেই বোধহয় পারিবারিক ঐতিহ্য কাজ করেছিল।
রায়চৌধুরী পরিবারের এতদিনকার পরম্পরা বোঝার আগেই জড়িয়ে ফেলেছিল তাঁকে। নইলে ওই বয়সে এমন সিদ্ধান্ত নেয় কী করে মানুষ?

শেষমেশ লেখা হল সন্দেশ-এ। বড়দা সুকুমারের নির্দেশে একখানা ছোট গল্প লিখে দিলেন, ছাপাও হল। নিজে নাম দিয়েছিলেন ‘লক্ষ্মীছাড়া’, বড়দা বদলে রাখলেন ‘লক্ষ্মী ছেলে’। ব্যস, শিশুদের জন্য ছাপার হরফে নতুন এক ভালবাসার মানুষের আবির্ভাব হল, যার নাম তখন ছিল লীলা রায়।
সন্দেশে লেখা বেরনোর পরপরই এ-কাগজ সে-পত্রিকা থেকে ছোটদের জন্য গল্প লিখে দেওয়ার আর্জি আসতে লাগল লীলার কাছে, তিনিও হাসিমুখে লেখার কাজে লেগে পড়লেন রীতিমতো। তৈরি হতে লাগল একের পর এক অবাক-করা সমস্ত চরিত্র, যাদের নানান কীর্তিকলাপ চিরকালীন হয়ে থাকার দাবি নিয়েই এল।
কিন্তু জীবন বরাবরই লীলাকে স্থিতি থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর গত হওয়ার পর সুকুমারের হাত ধরেই দিব্যি এগোচ্ছিল সন্দেশ, সেই তরুণ সুদক্ষ লেখক-সম্পাদকও লীলার হাত ছাড়িয়ে পালালেন।
১৯২৩ সাল, লীলা তখন ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ার বাড়ি ছেড়ে সবেমাত্র রসা রোডের জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের বাসায় এসে উঠেছেন, সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুতে থমকে গেল সন্দেশ। লীলাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দেবার মানুষটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। শুধু সন্দেশ পত্রিকাই নয়, রায় পরিবারের ব্যবসাও ডুবল দেনার দায়ে, এমনকী গড়পারের প্রিয় সেই ভিটেও ছেড়ে দিতে হল তাঁদের। প্রায়-যুবতী লীলা আবারও এসে দাঁড়ালেন লেখালিখির এমন এক রাস্তায়, যেখানে কোনও ছায়া আর নেই তাঁর জন্য। কিন্তু তাঁর মনে পড়ে গেল, এক দুপুরে আবোল-তাবোলের ছবিতে তুলি লাগাতে লাগাতে বড়দা লীলাকে বলেছিলেন, ‘তুইও এসব করবি, কেমন?’
বহু পরে লীলা মজুমদার লিখছেন, ‘সেদিন আমার পনের বছর বয়স, স্কুলে পড়ি। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম বড়দা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই আমার পথ। আমাকে দিয়ে অন্য কোনো কাজ হবে না।’ নিজের হাতের মশলাটা এভাবেই যোগ্য হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সুকুমার রায়।
এর পর কয়েকটা বছর এগিয়ে গেলেই দেখতে পাব, এক গ্রীষ্মের দুপুরে নতুন গল্পের নকশা মাথায় বুনতে বুনতে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের ছায়ায় হাঁটছেন ছিপছিপে লীলা। শান্তিনিকেতন তাঁর ভারী ভাল লেগে গিয়েছে। সেইসঙ্গে পরম পাওয়া প্রিয় কবির সান্নিধ্য। কিন্তু আগের দৃশ্য থেকে এ-দৃশ্যে লীলাকে আসতে হয়েছিল বেশ খানিকটা ঘুরপথেই। কলকাতা-দার্জিলিং-শান্তিনিকেতন।
আপাত-স্থির এই মানুষটির মন কিন্তু শান্তি খুঁজে পেত না কোথাও। থিতু হয়ে গেলেই সে-মনের মনে হত, আটকা পড়েছি বোধহয়। তাই নতুন ঠিকানার খোঁজ শুরু হত। কলেজ শেষ করবার পর লেখালিখি পুরোদমে চললেও, নিজের সঙ্গে বেঝাপড়ার প্রয়োজনেই কলকাতা ছাড়া দরকার, এমনটাই মনে হয়েছিল তাঁর।
যেমন ভাবা তেমনি কাজ। নিজেই চিঠি লিখে দার্জিলিং-এর মহারানি গার্লস স্কুলে শিক্ষিকার পদে যোগ দিলেন। সে-সময় স্কুলটি চালাতেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার, লীলার হেমমাসিমা। তিনিই আদর করে ডেকে নিলেন।
এই লেখার গোড়ায় কলকাতা ছেড়ে একটা ট্রেন চলে গিয়েছিল ধোঁয়া উড়িয়ে... সেই ট্রেন আসলে গিয়ে থেমেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার রোদ্দুরে। স্কুলের চাকরি নিয়ে নতুন জীবনের প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছিলেন তেইশের লীলা।
কিন্তু সেখানেও বেশি দিন মন লাগল না। পালাবার পথ খুঁজছিলেন, সে-পথ নিজেই এসে ধরা দিল। দার্জিলিং বেড়াতে এলেন রবীন্দ্রনাথ, লীলা গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। তদ্দিনে লীলার লেখালিখি, ছোটদের প্রতি তাঁর উৎসাহ, এ সবই রবীন্দ্রনাথের গোচরে এসেছে।
শান্তিনিকেতন ফিরে গিয়ে লীলাকে একটি চিঠিতে লিখলেন তিনি, ‘আশা অধিকারী শিশু-বিভাগ পরিচালনা করেন, তিনি এক বছরের ছুটি নিচ্ছেন, তুমি এসে এক বছরের জন্য তাঁর জায়গা নাও।’
তখন সেটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাজ। প্রস্ফুটিত বিশ্বভারতীকে নানান রঙের যোগ্য মানুষজনে সাজিয়ে আরও বিকশিত করে তোলা। চিঠি পাওয়ামাত্রই লীলা ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলমলে বরফের দিন ঘুচল, সামনে লাল মাটির বিস্তীর্ণ পথ।
শান্তিনিকেতনের সেই চাঁদের হাটে লীলাকে ঘিরে থাকল এক আশ্চর্য জ্যোৎস্না। আর পাশাপাশি মোমের মতো এক বিস্ময়কর মানুষের আলোও। কিন্তু বেপরোয়া মনটির বেশিক্ষণ জ্যোৎস্না সইবে কেন?
বিশ্বভারতী বা অধ্যাপনা, কোনওটিই তাঁর মনকে সেই শান্তি দিতে পারল না, যার খোঁজে এতগুলো বছর হেঁটেছেন তিনি। বিশ্বভারতী বিষয়ে লীলা মজুমদারের একটি বাক্যই তাঁর হতাশাকে বুঝিয়ে দেয়- ‘মোমবাতির ঠিক তলাটিতে অনেকখানি জমানো অন্ধকার’।
কবিগুরু যখন বিদেশে, শান্তিনিকেতনের পাট চুকিয়ে লীলা ফের কলকাতায় চলে এলেন। দেশে ফিরে তাঁর ইস্তফা পত্র হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন, ঠিক কেনখানটিতে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে গিয়েছেন লীলা। উত্তরে বিশ্বভারতীর মলিনতার কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি লিখলেন, ‘তোমার যখন খুশি, যদি এসো, তাহলে দেখবে তোমার জন্য রয়েছে তোমার যথার্থ স্থান’।
বহু বছর পর শান্তিনিকেতনে অনেক আকাঙ্ক্ষার বসতবাটি তৈরি করে ফিরেই গিয়েছিলেন লীলা মজুমদার। তখন তাঁকে ঘিরেও বহু মানুষের সমাবেশ, অনেক অনুরাগীর পরিসর। জীবনসঙ্গীর প্রয়াণ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের নিভৃত বাড়িটিই ছিল তাঁর শান্তির ঠিকানা। কখনও হয়তোবা কলকাতার জন্য মন কেমন করত, কিন্তু দূর থেকে শুনতে পাওয়া সমুদ্রের গর্জনের মতোই কলকাতাকে ভাবতেন তিনি।
শান্তিনিকেতনের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দাটিতেই শেষমেশ সৈকত খুঁজে পেয়েছিলেন ভ্রাম্যমাণ এই মানুষটি। রাঁধতে ও খাওয়াতেও ভারী ভালবাসতেন। তাঁর হাতের খুন্তি-কড়াইয়ে নিত্যনতুন পদের ঝালমশলার ঝাঁঝ লেগেই থাকত। ‘হলদে পাখির পালক’ বা ‘টংলিং’-এর লীলা মজুমদার তো আমাদের কবেকার চেনা।
কিন্তু ‘রান্নার বই-এর মতো উপাদেয় রন্ধনপুস্তক আর ক’টি লেখা হয়েছে এ-ভাষায়?
সংসার তাঁকে দিয়েছে অনেক, তাঁর কাছ থেকে নিংড়েও নিয়েছে বহু কিছু। তিনি অভিমান করেননি, ওইটি তাঁর ধাতে ছিল না। বরং এগিয়ে গিয়েছেন পরের ধাপের দিকে, কেবল একটুকরো বিশ্বাস আর জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে সঙ্গী করে।
ভাবলে মনে হয়, কী আশ্চর্য রঙিন :আর কর্মময় একটি জীবন! কত রকমের অভিজ্ঞতা, যেন এক কোঁচড়ে কুড়িয়ে রাখা নানা রঙের নুড়ি। যখন যে-কাজটি করেছেন, ছাপ রেখে যাবার চেষ্টায় মেতে থেকেছেন। সেই পর্যায়ে সম্ভবত সবচাইতে বেশি সৃষ্টিশীল থেকেছেন তিনি।
অনবদ্য শিশুসাহিত্যের বেশির ভাগই তাঁর কলমে এসেছে তিনি আকাশবাণীতে কর্মরত থাকাকালীন। খানিকটা হয়তো কেজো তাগিদেই লিখতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু সে-লেখার মান প্রশ্নাতীত হয়েই থেকেছে। শেষমেশ এক কর্তাব্যক্তির কথায় মনে আঘাত লাগায় সেই যে কাজ ছেড়েছিলেন, দিল্লির দফতর থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকের অনুরোধও তাঁকে ফেরাতে পারেনি।
তবে এর পর যে-কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সম্ভবত সেইটেই ছিল তাঁর সবচাইতে ভাললাগার কাজ, পছন্দের ভূমিকা। বড়দা’র সুপুত্র মানিক ও উপেন্দ্রকিশোরের নাতনি নলিনী দাশের সঙ্গে ‘সন্দেশ’-এর সম্পাদনা। ১৯৬১ থেকে খোদ সত্যজিৎ রায়ের উদ্যোগে ফের বেরোতে লাগল সন্দেশ, তাঁরই আর্জিতে তাঁর আদরের ‘লিলুপিসি’ সম্পাদনায় হাতে হাত মেলালেন।
তখন তাঁর দুই মেয়ে কলেজ যাচ্ছে, সংসারের কাজকর্মও বিশেষ নেই। নিজের লেখালিখির পাশে বাকি সময়ের সবটুকু সন্দেশকেই উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি।
যে-পত্রিকা দিয়ে তাঁর গল্প লেখার শুরু, সেই পত্রিকারই পাতা এবার সেজে উঠতে লাগল তাঁর নিপুণ সম্পাদনার গুণে। ২০০৪ পর্যন্ত প্রাণ ঢেলে এই কাজটি করে গিয়েছেন লীলা। শেষমেশ ৯৭ বছর বয়সে পদত্যাগ করেছেন সন্দেশ থেকে।
আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, এই ভ্রাম্যমানতা, এই স্থিরতার খোঁজের সফর চলতে চলতেই দু’হাত ভরে তিনি লিখে গিয়েছেন অসামান্য, অবিস্মরণীয় লেখা। সেসব নিয়ে কথা বলবার লেখা এ নয়, তার উপযুক্ত মানুষও আমি নই। কিন্তু একজন সফল শিল্পী বোধহয় এই রকমই হন। হাজার ঝড় আর ঢেউয়ের ঝাপটা থেকে তিনি অনায়াসে বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা বাতিটিকে আগলে রাখতে পারেন, সারাক্ষণ। যেমন রেখেছিলেন লীলা মজুমদার।
শেষ জীবনটা কলকাতাতেই কেটেছিল। পাঠক থেকে আত্মীয়ের ভিড়ে, লেখালিখি আর সম্পাদনার ব্যস্ততায়। একেবারে শেষ দিকে স্মৃতি প্রতারণা করেছিল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে আপামর বাঙালির স্মৃতিতে শতায়ু লীলার চিরকালীন আসনটি পাতা হয়ে গিয়েছে।
লীলা মজুমদার আসলে ক্যালেইডোস্কোপের ডাকনাম, যা চোখে লাগিয়ে ঘোরাতে থাকলে অগুনতি রঙিন কাচের নকশা ফুটে ওঠে আজও।
আমাদের সক্কলকার ঠাকুমাকে আসলে তো লীলা মজুমদারের মতোই দেখতে। যাবার আগে আমাদের প্রত্যেকের ঘুমের পাশে, বিছানার মাথার কাছে তিনি টাঙিয়ে রেখে গিয়েছেন তাঁর সেই ঝুলি, যা থেকে আজও আশ্চর্য সব গল্প বেরিয়ে আসে আর ঘুম পাড়িয়ে দেয় আমাদের।
ওঁদের কাছে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নবনীতা দেব সেন
বাংলা কেন, যে-কোনও সাহিত্যেই মেয়েদের লেখায় ব্যঙ্গরস, ব্যঙ্গকৌতুক খুব কম। তাই লীলা মজুমদারের লেখা বিশেষ ভাবে ভাল লাগত, এখনও লাগে। তাঁর শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা, প্রাণময়, সুস্থ রসিকতার কোনও তুলনা হয় না। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর, সেই কারণেই রসিকতার মধ্যে দিয়েও প্রতিবাদ করতে পারতেন।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
লীলা মজুমদার ছিলেন অদ্ভুত ধরনের এক লেখক। ছোটদের জন্য লেখায় যে-মজা তিনি আনতেন, যা তিনি বোধ করি তাঁর পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন, আমাকে বরাবর খুব টানত। তাঁর বড়দের জন্য লেখাও আমি সমান আগ্রহে পড়েছি। আভিজাত্য বজায় রেখে রসকে উত্তীর্ণ করা, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।
বাণী বসু
লীলা মজুমদার নামটা শুনলেই মন আনন্দে ভরে ওঠে। সাহিত্য থেকে জীবনে একজন মানুষ আনন্দকে এতখানি মূল্য দিয়েছেন, এর উদাহরণ কমই আছে। সকলেই তো দুঃখ নিয়ে লিখতে ব্যস্ত। ছোটদের গল্পে যে-শব্দচয়ন বা নামকরণ, তারও জুড়ি নেই। গুপী বা পদিপিসি শুনলেই মাথায় একটা ছবি তৈরি যায়। ছোটদের মনটা উনি খুব ভাল বুঝতেন।
-

কর্নাটকে কংগ্রেস নেতার কন্যাকে কলেজের মধ্যেই পর পর কোপ! খুন করে পালালেন প্রাক্তন সহপাঠী
-

আচমকাই নাক-মুখ দিয়ে রক্তপাত! ভোটের আগের রাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের রহস্যমৃত্যু কোচবিহারে
-

সকাল ৯টা পর্যন্ত বাংলার তিন আসনে ভোটের হার ১৫.০৯ শতাংশ, সবচেয়ে বেশি আলিপুরদুয়ারে
-

ইরানে প্রত্যাঘাত করল ইজ়রায়েল, ক্ষেপণাস্ত্র হানা ইসফাহানে, নিশানায় বিমানবন্দর, পরমাণুকেন্দ্র?
Share this article
CLOSE- One number & One character
- Minimum 6 character
-
Forgot Password
Or
By continuing, you agree to our terms of use
and acknowledge our privacy policy