প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশের সাম্প্রতিকতম বইটি শুধু একটি জীবনীগ্রন্থ নয়। ৭০০ পৃষ্ঠার এই কাহিনি পারসিক কার্পেটের মতো অসংখ্য গল্পচিত্র দিয়ে খচিত। সে সব সংগৃহীত শুধু মেননের নিজস্ব সংরক্ষণশালা থেকে নয়, দূর-দূরান্তের আর্কাইভস থেকে। মেননের স্বহস্তে গড়ে তোলা ইন্ডিয়া লিগ, যার অভিপ্রায় বিলেতে স্বাধীনতাকামী ভারতের বাণী প্রচার— তার সূত্রেই বেঙ্গালিল কৃষ্ণন কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে বয়সে সাত বছরের বড় জওহরলাল নেহরুর (ছবিতে দু’জনে) পরিচয়। সেই পরিচয় নিমেষেই পরিণত বন্ধুত্বে ও গভীর নির্ভরতায়।
এই জন্য ধরে নেওয়া হয়েছিল, তিনিই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণাদাতা, বা কু-মন্ত্রণাদাতা। সে জন্য এই বামপন্থী বাক্পটু মানুষটি অনেক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। ‘রাসপুতিন’, ‘মেফিস্টোফিলিস’ কী না নিন্দা তার প্রতি বর্ষিত হয়নি! অথচ ১৯৭৪ সালে তিনি দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর বন্ধুকন্যা (তখন প্রধানমন্ত্রী) ইন্দিরা গাঁধী বলেছিলেন, “আ ভলক্যানো হ্যাজ় বিন এক্সটিঙ্গুইশড।” কথাটির মধ্যে মেশানো ছিল গভীর শ্রদ্ধা।
মেনন ছিলেন বাগ্মী, সুপণ্ডিত এবং তিরিশের দশকের ‘নতুন যুগের’ মানুষ। নতুন যুগ, কারণ সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তখন অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ব্রিটেনের তরুণ সমাজ। মেননের চিন্তাধারায় ছিল মার্ক্সবাদের সঙ্গে উপনিবেশবাদ বিরোধিতার মিশেল। সে কারণেই মেনন সুদূর ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন অসংখ্য ব্রিটিশ তরুণ-তরুণীকেও। নেহরুও ঠিক এই পরিমণ্ডলের মানুষ— কেমব্রিজের বামপন্থী ভাবনার জলবায়ুতে বেড়ে ওঠা দেশপ্রেমিক। স্বাধীন ভারতে দুই বন্ধু যখন কাজে নামলেন, তখন বোঝা গেল যে নেহরুর কংগ্রেসি সহকর্মীরা দেশপ্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু বামপন্থা সম্পর্কে হাড়-চটা। অথচ নেহরুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সাহস কারও নেই। ফলে মেনন হলেন ‘নন্দ ঘোষ’।
আ চেকার্ড ব্রিলিয়ান্স: দ্য মেনি লাইভস অব ভি কে কৃষ্ণ মেনন
জয়রাম রমেশ
৯৯৯.০০
পেঙ্গুয়িন ভাইকিং
১৯৪৮-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেলের কথোপকথনের মাউন্টব্যাটেন-কৃত নোট আজও রয়েছে তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহশালায়, যা জয়রাম ব্যবহার করেছেন। পটেল বলেছিলেন, সরকারের ‘মারাত্মক ভুল’— কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কৃষ্ণ মেননকে ব্রিটেনে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ; এবং ব্যারিস্টার আসফ আলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, কারণ তাঁর পত্নী অরুণা আসলে কমিউনিস্ট (আসল গন্ডগোলের কারণ হয়তো তাঁদের মুসলমান-হিন্দু বিবাহ, আজকের ভাষায় ‘লাভ জিহাদ’)।
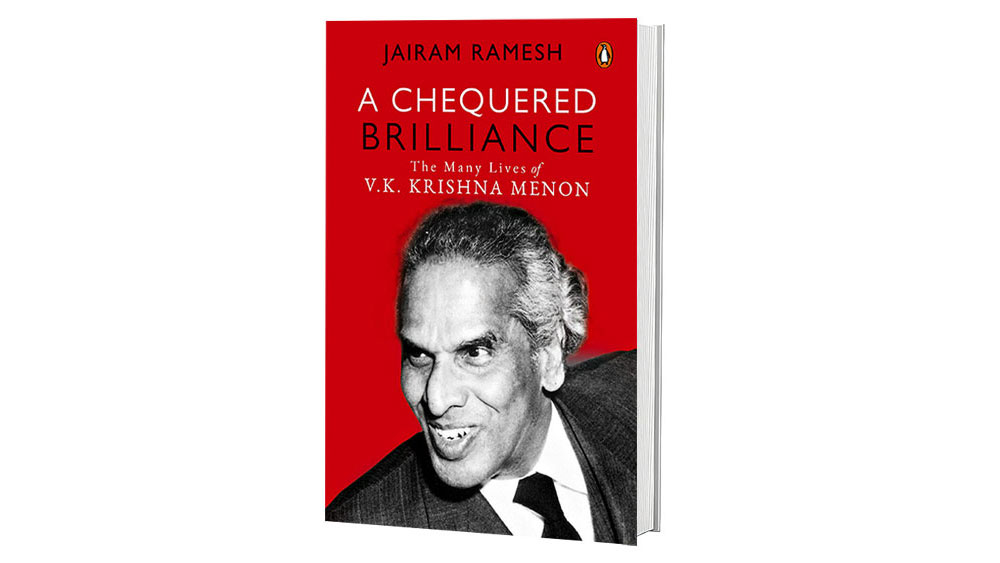

সোজা কথা, দলের অভ্যন্তরে নেহরুর নিন্দুকের অভাব ছিল না— দলের দ্বিতীয় স্তম্ভ সর্দার পটেল ছিলেন তাঁদের সেনাপতি। তা ছাড়া, যে স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন নিয়ে নেহরু ও মেনন তাঁদের ভাবাদর্শ রচনা করেছিলেন, তার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেছিল কংগ্রেস। মেনন ও নেহরু, দু’জনের সঙ্গেই পটেলের ব্যবধান ছিল। তবে নেহরুর মনোভাব ছিল প্রচ্ছন্ন, আর মেনন কোমর থেকে পিস্তল চালানোয় বিশ্বাসী।
পটেলের মৃত্যুর পর মেনন লেখেন বন্ধু মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কৌর-কে: “হি ওয়াজ় আ গ্রেট ম্যান অফন উইথ স্মল উইকনেসেস, অ্যান্ড আই ফিয়ার সামটাইমস দ্যো নট অফন আ স্মল ম্যান উইথ গ্রেট উইকনেসেস।”
জয়রামের বইটি মেননের জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছরের অসংখ্য প্রসঙ্গ ও ঘটনায় ঠাসা। সত্যিই কি মেনন কমিউনিস্ট ছিলেন, যেমন তাঁর সমালোচকেরা বলতেন? জয়রাম খোলাখুলি কিছু না বললেও একটি কৌতূহলজনক প্রসঙ্গ এনেছেন এই সূত্রে। মেনন ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও (লেবার দলের সদস্য) দুই প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হ্যারি পলিট ও রজনী পাম দত্ত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৩৫ সালে নেহরু সুইৎজ়ারল্যান্ডে তাঁর চিকিৎসাধীন স্ত্রী কমলাকে রেখে সকন্যা লন্ডনে আসেন, আলাপ হয় মেননের সঙ্গে। দত্ত তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এরও (কমিনটার্ন) বড় নেতা। ভারতের ভাবী নেতা নেহরুকে তিনি দেখছিলেন মেননের চোখ দিয়ে। কমিনটার্ন চাইল, দত্ত সরেজমিন দেখুন এ বার।
দত্ত হাজির হলেন লস্যানের স্বাস্থ্যনিবাসে। কোনও এক ছুতোয় নেহরুর সঙ্গে হল দীর্ঘ আলাপচারিতা। তার পর কমিনটার্নে দত্তের সুদীর্ঘ রিপোর্ট ‘প্রফেসর’ (নেহরুর গোপন নাম) সম্পর্কে। দত্তের জীবনী থেকে জয়রাম উদ্ধৃত করেছেন সেই গোপন প্রতিবেদন, যার মধ্যে দু’টি জিনিস ফুটে ওঠে। নেহরুর তীব্র ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব, পার্টিসর্বস্ব কমিউনিস্টের দৃষ্টিতে নেহরুর উদারবাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। প্রায় দু’দশক পরে, যখন নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শুরু হচ্ছে ‘ঠান্ডা যুদ্ধ’, মস্কোর কর্তারা হয়তো ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের রূপরেখা আঁকতে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন পুরনো প্রতিবেদনটি।
চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এনলাই-এর সঙ্গে মেননের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চৌ তাঁকে নিমন্ত্রণ করে চিন নিয়ে যান। মেননের তখন আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার জন্য খুব নামডাক। সেই সময়ে চিন কর্তৃক গ্রেফতার হওয়া কিছু মার্কিন গুপ্তচর বৈমানিককে উদ্ধার করতে আমেরিকা তৎপর, মেননের দৌত্যে চার জন বৈমানিক মুক্তি পান। তবে শুধু সেই কাজটির জন্যেই কি মেননকে নিমন্ত্রণ? জয়রাম মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের দূত হিসেবে কিসিঙ্গারের পাকিস্তান হয়ে চিনে গোপন যাত্রা, তার পর স্বয়ং নিক্সনের বেজিং-এ আবির্ভাব, সূচনা নতুন যুগের। হয়তো চিনের ধুরন্ধর নেতা সেই ১৯৫৫ সাল থেকেই খুঁজছিলেন কোনও এক মধ্যস্থ, যে আমেরিকাকে দাঁড় করাবে চিনের পাশে। কারণ, চিন তো কোনও দিনই নিজেকে বিশ্বশক্তি ব্যতীত আর কিছু ভাবেনি।
পরবর্তী কালে চিন যখন ভারত আক্রমণ করে, মরমে মরে গিয়েছিলেন মেনন। তবে তাঁর সম্পর্কে অপবাদ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনও রকম যুদ্ধের প্রস্তুতি নেননি— এ যে একদম ভুল, সে কথা জয়রাম তথ্য-সহ প্রমাণ করেছেন। চিনকে ঠেকাতে মেনন চেয়েছিলেন মোট ৮৭ কোটি টাকার বাজেট বহির্ভূত বরাদ্দ, তার মধ্যে ১৪ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রায়। কিন্তু অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই বললেন, যুদ্ধের জন্য এত খরচ কেন বাপু? নেহরুও কিছু করতে পারেননি।
বোঝা যায়, নেহরু কত দ্রুত কংগ্রেসে শক্তি হারাচ্ছিলেন। শেষে চিন ঘাড়ে এসে পড়ার পর ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে মোরারজি দিয়েছিলেন মাত্র ৪২ কোটি টাকা, বিদেশি মুদ্রায় শুধু ৪৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু মেননের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে ‘ডিআরডিও’, যা আজ ভারতীয় সমরযন্ত্রের প্রাণ। তাঁরই প্রয়াসে মিগ-২১’এর চুক্তি হয়।
নেহরুর সমাধিতে শেষ সমিধটি নিক্ষেপ করেছিলেন মেনন। কিন্তু সে-ই তো ভারতের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের অবসান। তার পরেও কেন তিনি এক দশক রইলেন ভারতে, জিতলেন নির্বাচন? কেন ফিরে গেলেন না লন্ডনে তাঁর পাড়া ব্লুমসবেরিতে; কিংবা সেন্ট প্যানক্রাসে, যেখানে বহু কাল তিনি ছিলেন বরো সদস্য? আসলে পাল্টে গিয়েছিল মেননের চেনা পৃথিবীটাই।
জয়রাম রমেশ অবশ্যই বইটি একটু স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাখলে পাঠক খুশিই হতেন। কিন্তু এই লকডাউনের বাজারে এতখানি ইতিহাসের উপাদান সরাসরি হাতে পাওয়া কম কথা নয়।









