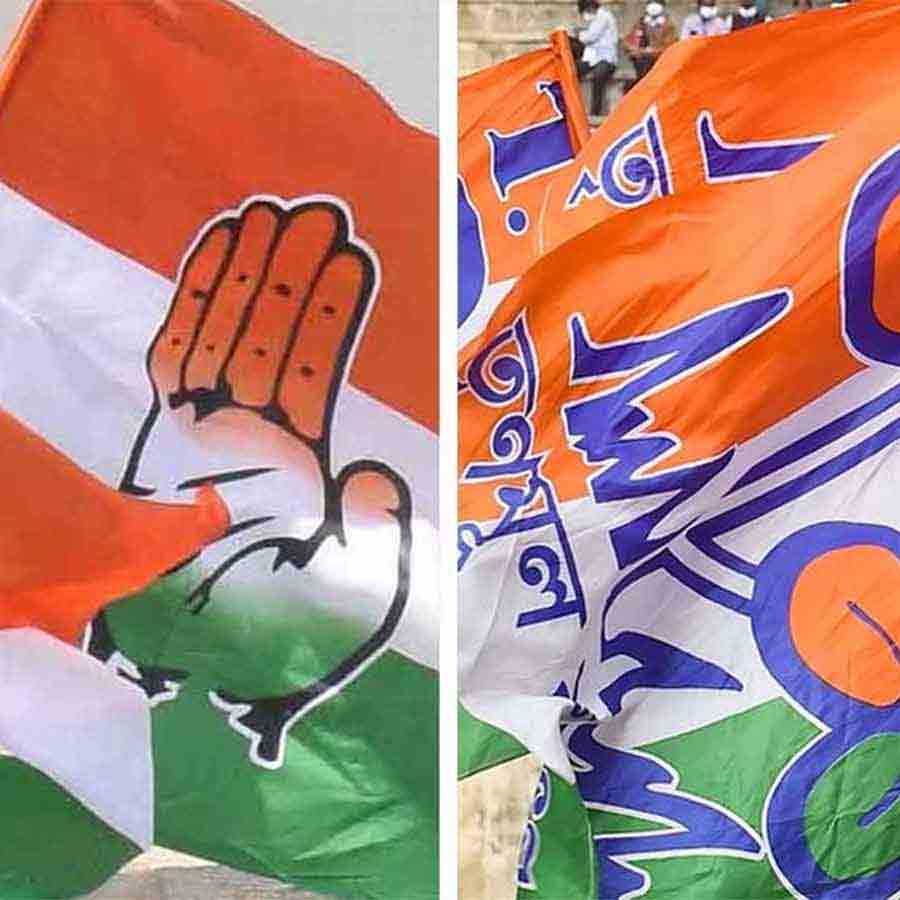বৈশাখ জুড়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের আয়োজন এখন ক্রমবর্ধমান। বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চলও লেগে থাকে সারা বছরই। যদিও এই চল আর উৎসবকে প্রকৃত অর্থে ‘রবীন্দ্রচর্চা’ বলা যায় কি না তা ভেবে দেখার। সর্বজনীন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের দীর্ঘ সত্তর-আশি বছর পরও বাঙালির জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা একাত্ম ভাবে যুক্ত হয়েছে কি না সেই প্রশ্নও আসে। কখনও ভেবে দেখা হয় কি, বাঙালির দৈনন্দিন প্রাদেশিক ও ব্যক্তিক সঙ্কীর্ণতা বা গণ্ডিগুলোকে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনদর্শনের দ্বারা অতিক্রম করতে পারা গিয়েছে কি না? তিনি তো সমাজজীবনের সমস্যাগুলোকে, সমস্ত সংশয় সঙ্কটকে সত্যের আলোকে সহজে গ্রহণ করার পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। মানুষের খাটো হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ যখন তার চার পাশের আর দশ জনের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারে না, মিলতে পারে না, তখনই সে ছোট হয়ে যায়। এই ক্ষুদ্রতা অন্যের কাছে যেমন, নিজের কাছেও তাকে পরাজয় বলে মেনে নিতে হয়।
বেশ কিছু দিন ধরে চার পাশে শুধু ভাঙার খেলা দেখা যাচ্ছে। কখনও তা ধর্মের নামে, কখনও ভাষার নামে, কখনও রাজনৈতিক দলের নামে মানুষকে ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে রেখে ক্ষুদ্র করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তাতে এক মানুষ আর এক মানুষের থেকে দূরে সরে তো যাচ্ছেই, বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়ে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চরিত্র খুব ভাল বুঝতে পেরেছিলেন। ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে বলেছেন, “বাংলা দেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগতে বেশিক্ষণ লাগে না।” তাঁর দেখা বিশ শতক থেকে আজ একুশ শতকে পৌঁছেও খুব একটা ফারাক চোখে পড়ে না। আজও বাঙালি জাতি কোনও সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। বাঙালির হাতে এখন মারণাস্ত্র চোখে পড়ে, বিদ্রোহের নামে এখানে ভ্রাতৃহনন হয়।
অথচ বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কম নয়। তাঁর মতে, যদি অন্য কোনও বাঁধনে মানুষকে বাঁধা না যায়, শুধু ধর্মের মিলেই মানুষ মানুষে মেলে, তবে সে দেশ বা জাতি হতভাগ্য। “সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে নিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ,” এমন আশঙ্কা তিনি বার বার বলেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-নির্মাণের প্রয়োজন এ দেশে অনেক বেশি। কারণ এই সমাজে ধর্মে, ভাষায়, আচারে মানুষের বিভাজন ও বিভাগ অন্তহীন; একই পাড়ায় বা এলাকায় বাস করে, পাশাপাশি কাছাকাছি থেকেও মনের মিল হয় না, প্রতি পদে সংঘাত লেগেই থাকে। কবির ভাষায় এটা ‘বর্বরতার লক্ষণ’। এই বর্বর পরিণতির দিকে জাতি বা দেশ যে যাবে তা তাঁর কল্পনাতীত।
রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার দু’টি প্রধান বৈশিষ্ট্য— এর বিশ্লেষণ বা দার্শনিক দিক, আর সামাজিক সমস্যার সমাধানের তথা ব্যবহারিক দিক। তিনি কখনও সমাজ এবং সে সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োগকে আলাদা করে দেখেননি। সমাজচিন্তায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন শিক্ষায়। তাঁর আজীবনের ভাবনা— শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমেই সমাজ সক্রিয় সচল থাকতে পারে। ইদানীং শিক্ষাক্ষেত্রেও ঘুণ ধরেছে। আটাত্তর বছর যে দেশ স্বাধীন, তার শিক্ষাব্যবস্থায় উচিত ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের জীবনদর্শনের প্রসার। জাতি নির্মাণে রবীন্দ্রভাবনা বিস্তারের কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাংলায় কখনও রচিত হয়নি। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট কিছু উৎসবে তাঁকে পূজার ছলে ভুলে থাকার ব্যবস্থায় অবশ্য ফাঁক থাকেনি, ফাঁকি যতই থাক।
বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এত আবেগ সত্ত্বেও কেন তাঁর অনুরোধ, উপদেশ, ভাবনাগুলি নীরবে নিভৃতে কাঁদছে? রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুল প্রচারে তো জাতিগঠনে সহায়তা হওয়ারই কথা ছিল, আদৌ তা হচ্ছে কি? কেন বাংলার মাটিতে আজও ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, গোষ্ঠীতে এত হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংঘাত? নিজের শুভবুদ্ধিকে না মেনে সব বিষয়ে পরশক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া, পরের ভাবনা ও কাজের গোলামি করা বাঙালির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলার এমন স্বভাবের উদাহরণ দিয়েছিলেন ‘শিক্ষার মিলন’-এ। একটি গ্রামের উন্নতিকাজ করতে গিয়ে গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে দিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি না কেন? তারা বলল, “কপাল!” তিনি বললেন, “কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?” তারা বলল, “আজ্ঞে কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।”
এ কথা শুনে কবির স্বগতোক্তি ছিল, আগুন লাগানোর বেলায় দেবতা, আর জল দেওয়ার ভার কোনও এক কর্তার! এরা কোনও একটা দলের কর্তা পেলেই বেঁচে যায়; এদের আর যত অভাবই থাক, কোনও কালেই কর্তার অভাব হয় না। সেই কর্তাভজা রাজনৈতিক নেতারাই আজ চার পাশে নানা খণ্ডিত গোষ্ঠীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সেখানে কে রবিঠাকুর, কী-ই বা তাঁর ভাবনা, নেতা কিংবা জনতার কারও কিছুতে যেন যায় আসে না।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)