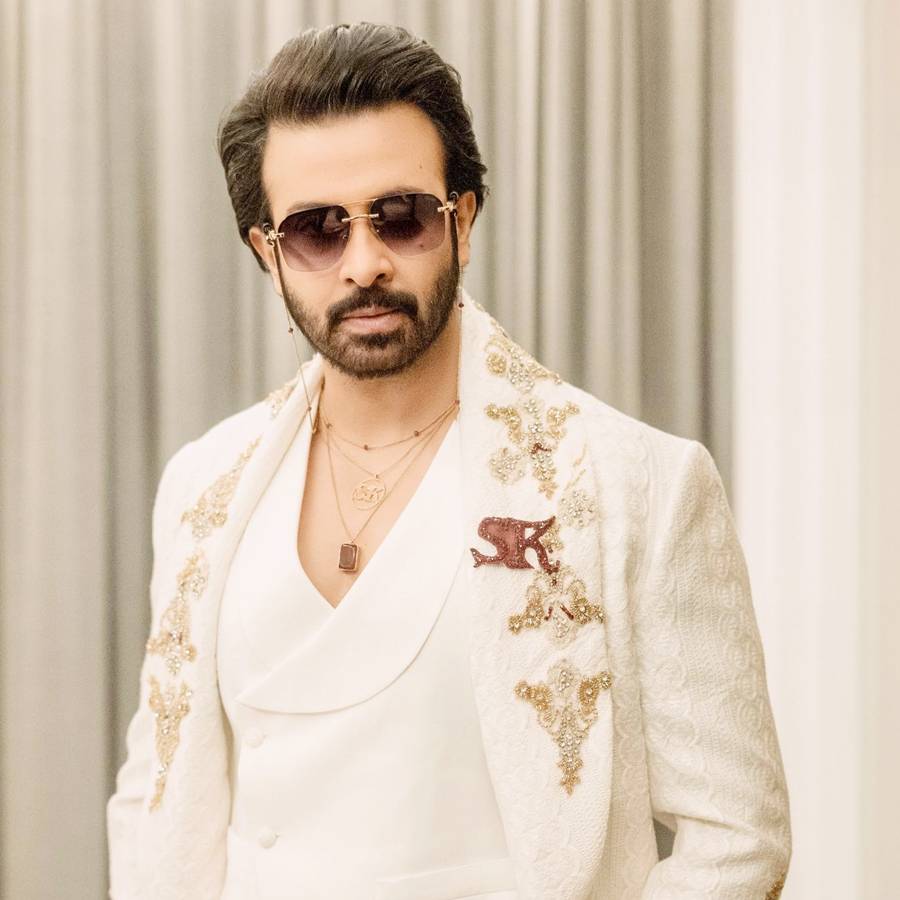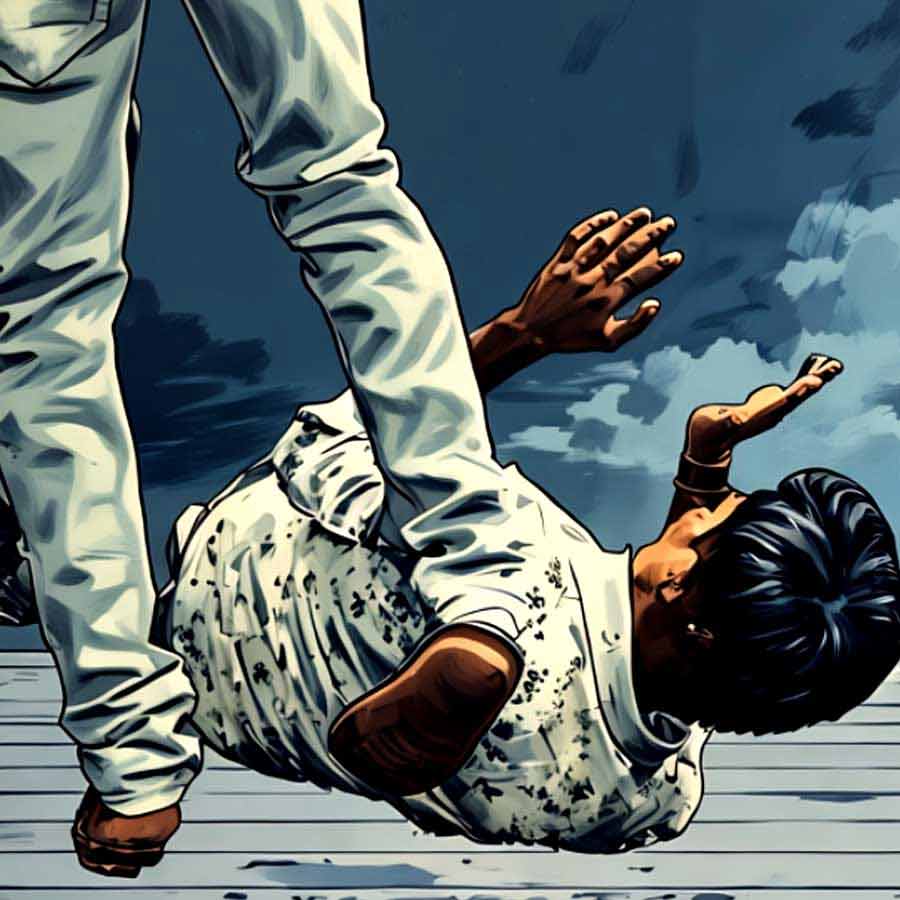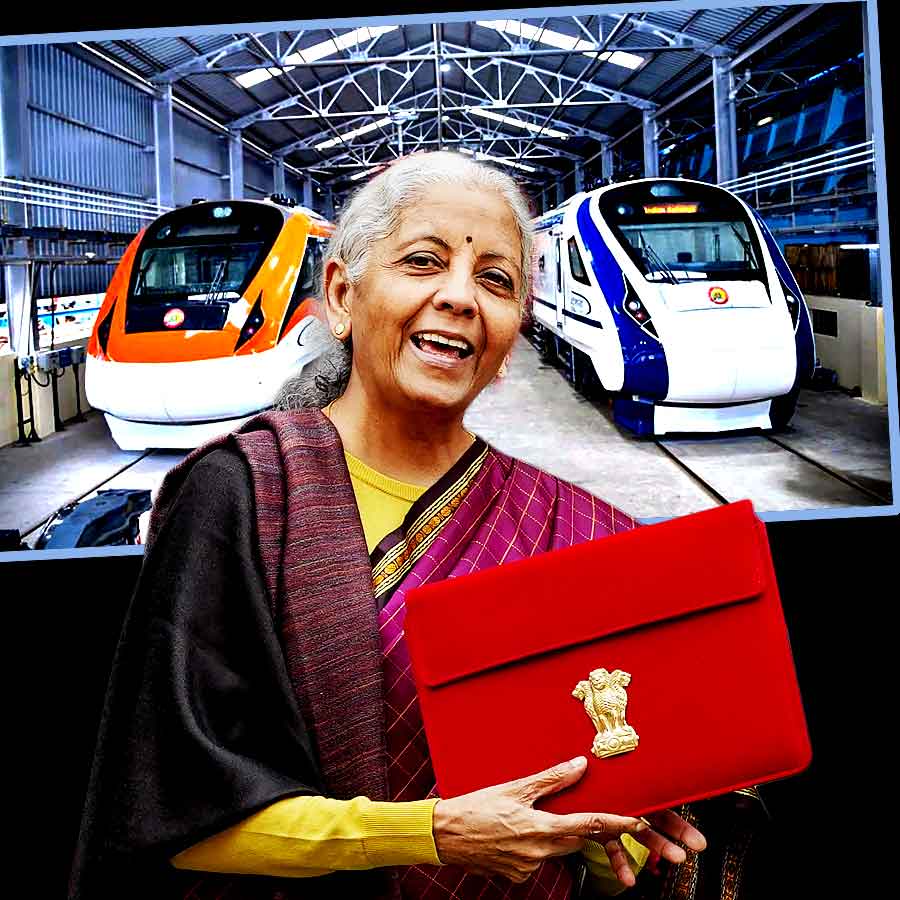গত ডিসেম্বরে দিনতিনেকের জন্য বেজিং যেতে হয়েছিল— ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় আর সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল নলেজ অন ডেভলপমেন্ট-এ একাধিক মিটিংয়ে ঠাসা ছিল সেই তিন দিনের সময়সূচি। ভাগ্যক্রমে, বেজিংয়ে তখন আমার কর্নেল ইউনিভার্সিটির জনাকয়েক প্রাক্তন ছাত্রও উপস্থিত ছিল, ফলে সরকারি কর্তা আর অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি তারা আমায় নিয়ে শহরের এ দিক-ও দিক ঘুরল একটু। হাতে বেশি সময় ছিল না। ওদের বললাম, আমায় কোনও একটা হুটং-এ নিয়ে যেতে। হুটং হল সরু গলি, যার দু’পাশে চিনের সনাতন ধাঁচের বাড়ি, বেশির ভাগেরই সামনে সামান্য খোলা জমি— এমন অলি-গলি-পাকস্থলীর ভিতরেই তো চোখে পড়ে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা।
এমনই এক হুটংয়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। বগলে ক্রাচ। হেসে জানতে চাইলেন, আমি কে? এর মধ্যেই তাঁর স্ত্রী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। তিনিও কথা বলতে আরম্ভ করলেন। জানালেন, কী ভাবে তাঁর স্বামী পা ভেঙেছেন। আমাদের কথা শুনে আরও কয়েকটা বাড়ির দরজা-জানলা খুলল, আমিও তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। আমার ছাত্রদের অবশ্য দোভাষীর কাজ করতে হল। সেই গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে আমার মনে পড়ল কলকাতার কথা, সেই শহরের পাড়ায় পাড়ায় থাকা সহজে মন খুলে কথা বলতে পারা মানুষদের কথা— বেলেঘাটায় আমার পিসিমার বাড়ির পাড়ার কথা, সেখানে যে কোনও বাড়ির দরজা-জানলা খুললেই কথা হত কোনও সহাস্য মানুষের সঙ্গে।
আমি প্রায় আট বছর পরে চিনে গেলাম। এমনিতে কোনও দেশের পক্ষে সেটা খুব লম্বা সময় নয়, কিন্তু চিন এত দ্রুত গতিতে বাড়ছে যে, আট বছরে অনেকখানি পাল্টে যাওয়া চোখে পড়ে। বেজিং এক অতি আধুনিক শহর— দুনিয়ার সব আধুনিক শহরের মতোই সেখানে আকাশচুম্বী বাড়ির সারি, যত্ন করে গড়ে তোলা সব পার্ক, চওড়া রাস্তা, এবং সেই রাস্তায় নিঃশব্দ দ্রুতগামী ইলেকট্রিক গাড়ির সারি। কিন্তু, আগের বারের সঙ্গে এ বারের সবচেয়ে বড় ফারাক, বেজিংয়ের বাতাসের চেহারা পাল্টে গিয়েছে। আকাশ এত পরিষ্কার হয়েছে যে, কয়েক বছর আগেও তা কল্পনার অতীত ছিল। মনে পড়ল, আগে যখন বেজিংয়ে এসেছি, তখন প্রবল বায়ুদূষণ গোটা শহরের উপরে কম্বলের মতো বিছিয়ে থাকত।
বেজিং থেকে সরাসরি ভারতে এলাম— প্রথমে কলকাতায়, তার পর গেলাম দিল্লিতে। দূষণের ছবিতে ফারাক এত প্রকট যে, খেয়াল না-করা অসম্ভব। পঞ্জাব থেকে অসম, গোটা উত্তর ভারতে বায়ুদূষণ মারাত্মক। এই দূষণে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, নিতান্ত বাড়াবাড়ি না হলে এ ব্যাপারটা আর সংবাদ শিরোনামে আসে না— কিন্তু এখনই এর প্রতিকার না-করলে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গতি স্তব্ধ করে দিতে পারে এই দূষণ।
ডিসেম্বরের শেষে যে দিন ভারতে নামলাম, সে দিন দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ৩২৮, চণ্ডীগড়ের ৩২৪, কলকাতার ২৮৬। যাঁরা ভাবেন যে, বড় শহরে এ রকমটা হবেই, তাঁরা মনে রাখতে পারেন যে, আমার ভারতে পৌঁছনোর দিনই নিউ ইয়র্কের একিউআই ছিল ৪৯, ওয়াশিংটন ডিসি-র ৩২, এবং বেজিংয়ের ৪৭। দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোয় দূষণের মাত্রা ছিল দিল্লি আর নিউ ইয়র্কের মাঝামাঝি স্তরে।
মোটামুটি ধরা হয় যে, একিউআই ৫০-এর কম হলে তা ‘গুড এয়ার’ বা ‘সুস্থ বায়ু’। সে হিসাবে, ২০২৪ সালে একটি দিনও দিল্লির ভাগ্যে ‘সুস্থ বায়ু’ জোটেনি। এই ধরনের দূষণে স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি হচ্ছে, তা বহু-আলোচিত। মানুষ হরেক কিসিমের শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। ২০১৯ সালে লান্সেট-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, ২০১৭ সালে ভারতে যত মৃত্যু হয়েছিল, তার ১২.৫% ঘটেছিল বায়ুদূষণ-জনিত কারণে— অর্থাৎ, প্রতি আট জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যুর কারণ বায়ুদূষণ। এই ধরনের দূষণ মানুষের মস্তিষ্কে কী কুপ্রভাব ফেলে, নতুনতর গবেষণায় তা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। এ বছর ১৪ জানুয়ারি নেচার-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র বলছে, চড়া দূষণের ফলে ডিমেনশিয়া, ডিপ্রেশন ও অ্যাংজ়াইটি সাইকোসিস-এর ঝুঁকি বাড়ে।
দূষণের এই প্রত্যক্ষ কুফল নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু, এই ধরনের চড়া দূষণ দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বৃদ্ধির উপরে কী প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে আলোচনা এখনও তুলনায় কম। গোড়ার দিকে এই প্রভাব তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু, এখনই সাবধান না হলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে তার ফল ভুগতে হবে।
যেমন অতীতে হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সিন্ধু সভ্যতার সূচনা হয়, এবং প্রায় দু’হাজার বছর ধরে তা ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সভ্যতা। কেন সেই সভ্যতার পতন হয়েছিল, সে বিষয়ে বহু অভিমত আছে। তার মধ্যে যে মতটি সবচেয়ে শক্তিশালী, তা হল, পরিবেশের ক্ষতির ফলেই ভেঙেছিল সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু উপত্যকার মানুষরা এমন ভাবে জল ব্যবহার করছিলেন যে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গিয়েছিল অনেক নীচে— জমি হয়ে উঠেছিল কৃষিকাজের অযোগ্য।
সিন্ধু সভ্যতার শাসকরা পরিবেশের এই ক্ষতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। কিন্তু আজকের পরিবেশের ক্ষতি বিষয়ে যে পরিমাণ গবেষণালব্ধ তথ্য রয়েছে, তাতে বর্তমান শাসকদের পক্ষে এ বিষয়ে অসচেতন থাকা অসম্ভব। কোন পথে হাঁটলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, সে কথাও তাঁদের জানা। দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গিয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন, জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের কথা বলেন— কিন্তু পরিবেশের যে সমস্যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে, আমরা সেগুলিকে নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করি।
বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে, বাস বা গাড়িতে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলি কোথায় অবস্থিত, কৃষকরা মাঠেই ফসলের গোড়া পোড়াচ্ছেন কি না, বাড়িতে রান্নার কাজে কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে— এই সব প্রশ্নের উত্তরই প্রভাব ফেলে দূষণের সমস্যায়। ভারতের এমন নীতি দরকার যা সাধারণ নাগরিকের কল্যাণকে চিন্তার ভরকেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করবে। বায়ুদূষণকে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের দ্বন্দ্বে পরিণত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, বায়ুদূষণ এক সর্বজনীন সমস্যা। বায়ুদূষণ প্রতিরোধের কাজে অর্থ বরাদ্দ করা, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করানো, তার থেকে অ্যাকশন প্ল্যান বানানো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে ফেলা সম্ভব। চিন সেই কাজ করে দেখিয়েছে।
সরকার এই কাজগুলি করলে তাতে সাময়িক ভাবে সরকারি ব্যয় বাড়বে। তার জন্য অবস্থাপন্ন নাগরিকদের থেকে দু’তিন বছরের জন্য বিশেষ প্রত্যক্ষ কর আদায় করা যেতে পারে। ভারতে জিডিপি-র অনুপাতে কর আদায়ের পরিমাণ লজ্জাজনক রকম কম। তার চেয়েও বড় কথা, ভারতের মোট কর রাজস্বের ৪০ শতাংশেরও কম আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে। যে-হেতু আয়ের নিরিখে পরোক্ষ করের বোঝা ধনীদের তুলনায় মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের উপরে অনেক বেশি পড়ে, এবং প্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতে হয় মূলত ধনীদের, তাই ভারতের করব্যবস্থা স্পষ্টতই রিগ্রেসিভ বা পশ্চাৎমুখী। বায়ুদূষণের সমস্যা দূর করার জন্য ধনীদের উপর কয়েক বছরের জন্য বিশেষ কর চাপানো সম্ভব, এবং সেই ব্যবস্থাটি ন্যায্যও বটে।
দূষণের সমস্যাটিকে ভারত এত দূর বাড়তে দিয়েছে, সেটাই যথেষ্ট লজ্জার। এখনও নিষ্ক্রিয় থেকে সে লজ্জা আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না।
ভূতপূর্ব মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক; ভূতপূর্ব মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ভারত সরকার
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)