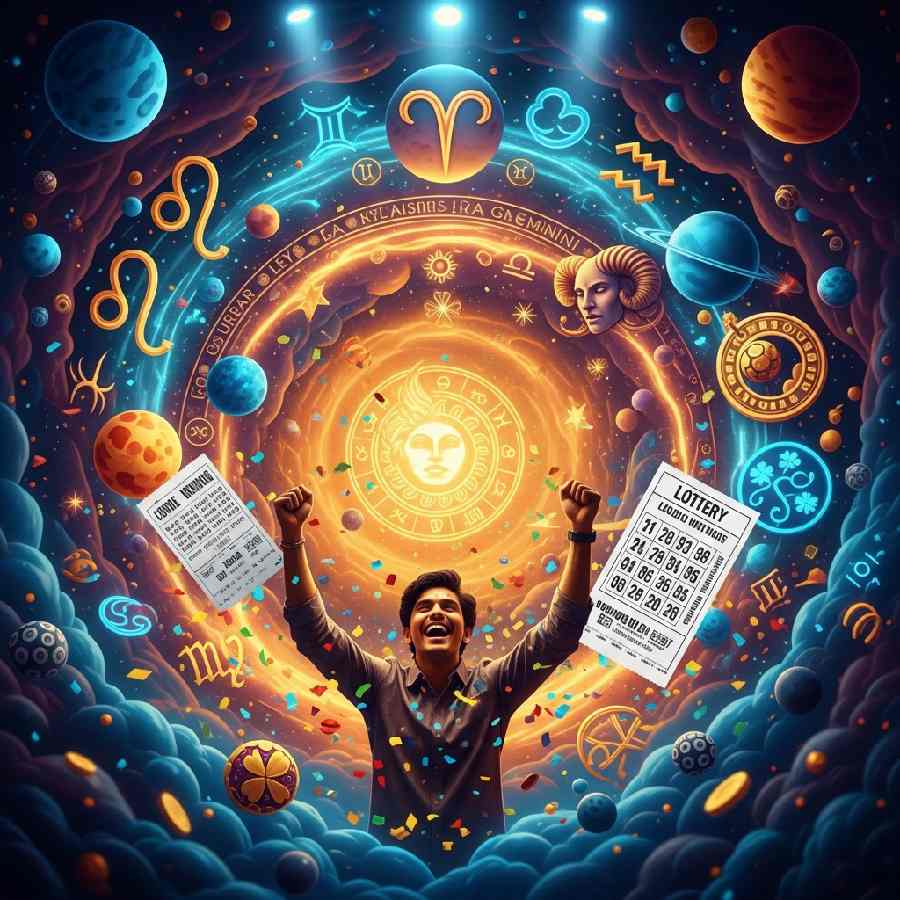যন্ত্রমেধা এসে সব প্রোগ্রামারের চাকরি খেয়ে নেবে, এমন একটা আশঙ্কা বাজারের হাওয়ায় ভাসছে গত দেড়-দু’বছর ধরে। সে কথাটি নিয়ে কতখানি আতঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন? যে কাজ একঘেয়ে, অথবা যে কাজ করতে অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাতে যন্ত্রের ব্যবহারের গুরুত্ব মানুষ বুঝেছিল প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগে, শিল্পবিপ্লবের আদি পর্যায়েই। পেশির মতোই মগজের কাজগুলিও যন্ত্র দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় কি না, সেই খোঁজের ইতিহাসও সওয়া শতাব্দীর— বিংশ শতকের গোড়া থেকেই গণকযন্ত্রের বেশ উন্নত মানের কাজ শুরু। ১৯৫০ সালে অ্যালান টুরিং লেখেন ‘কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স’ নামক এক গবেষণাপত্র। মাথার কাজ যে কম্পিউটার দারুণ ভাবে করবে এটা বুঝতে যেমন সময় লাগেনি, তেমনই বোঝা যাচ্ছিল তার সীমাবদ্ধতার জায়গাগুলোও। সেই শুরু। গত শতকের ষাট-সত্তরের দশক থেকে যে গণনা বিপ্লব (কম্পিউটিং রেভলিউশন) সামনে এল, তা এখন মধ্যগগনে।
দু’টি বিষয় এই সময়টাকে আরও অনেক বেশি পরিবর্তনশীল করে তুলেছে— যন্ত্রমেধা, এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। এই দুইয়ের ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির রূপায়ণ সফল হলে ঠিক কী কী যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে, সেই বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেও, সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির আঙিনায় এর অভিঘাত সম্পর্কে চিন্তাবিদরা কতটা অবহিত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এবং, আজকের পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কোনও সমাজচিন্তক বা দার্শনিক নেই, যাঁর প্রভাব ট্রাম্প-মাস্ক জুটির প্রভাবের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। বরং গোটা বিশ্বেই বুদ্ধিজীবীরা মোটের উপরে আপসের পথে হেঁটেছেন। সেইখানে এই পরিবর্তনশীল সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতার বিষয়টাকে অবজ্ঞা করার যে ঝোঁক, এবং তাই নিয়ে যে অগভীর বিশ্বাস, তা গোটা জগৎকে প্রভাবিত করছে।
সেই প্রভাবের চেহারা কী রকম? কিছু দিন আগে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান চরিত্র নাগবর রামরাও নারায়ণ মূর্তি হঠাৎ সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজ করার নিদান দিলেন। তা নিয়ে বিপুল হইচইও হল— যুক্তির পাহাড় জমল পক্ষে ও বিপক্ষে। কিছু দিনের মধ্যেই সদ্য কাজে যোগ দেওয়া কয়েকশো কর্মীকে ছাঁটাই করল নায়ারণ মূর্তির সংস্থা ইনফোসিস। এই প্রবণতা কিন্তু খুব ‘স্বাভাবিক’ নয়— ভারতের বড় বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়, যেখানে লক্ষাধিক মানুষ কাজ করেন, অর্থনীতির স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকলে সেখানে এ ধরনের ছাঁটাইয়ের খবর খুব বেশি শোনা যায় না। এই ঘটনাটিকে বুঝতে হবে মাস্ক-যুগের পুঁজিবাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে, নারায়ণ মূর্তিও যার প্রতিনিধি।
নারায়ণ মূর্তি বিলক্ষণ জানেন, তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় মানুষের গুরুত্ব কতখানি। ধরুন, কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে, যেগুলোকে ছোট থেকে বড় হিসাবে সাজাতে হবে। তেমন একটা প্রোগ্রাম লিখে ফেলা সহজ; আজকের দিনে চ্যাটজিপিটি বা ডিপসিককে বললে তা এই প্রোগ্রাম চট করে লিখে দিতে পারে। অন্য দিকে, একটা স্কুলের সব ক্লাসের পরীক্ষার ফলাফলকে পুরোপুরি একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে লিখে ফেলা তুলনায় পরিশ্রমের কাজ। সেই সফটওয়্যারে এমন অনেক বিষয় থাকে যে শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বানিয়ে ফেলা খুবই মুশকিল, প্রায় অসম্ভবও বলা চলে। এর কারণ আমাদের বাস্তব জীবনে যে কোনও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সামগ্রিক ভাবে রূপায়িত করতে গেলে সেখানে প্রচুর জটিলতা থাকে, এবং বিভিন্ন সময়ে সেই জটিলতা কাটাতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। নারায়ণ মূর্তি নিঃসন্দেহে জানেন যে, মানুষকে দিয়ে কাজ করাতেই হবে।
তাঁরা শুধু চান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি হয়ে আসবে ছাত্রছাত্রীরা। শুরুতে অল্প কিছু দিন শিক্ষানবিশ থেকেই এই পড়ুয়ারা একেবারে কাজে নেমে পড়বে। সেই সময়ে কেউ শিখতে দেরি করলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ আরও অনেক মানুষ সুযোগের অপেক্ষায়— এবং, কাজের বাজারে কেবলই বার্তা পৌঁছবে যে, সামান্যতম শ্লথতারও কোনও ক্ষমা নেই। যন্ত্র দিয়ে মানুষের কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, কাজ বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষকেই হয়ে উঠতে হবে যন্ত্রসম।
ইলন মাস্ক আরও এক কাঠি উপরে— তিনি স্কুল কলেজের শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী নন। বলে দিয়েছেন, যে কোনও লোকই সরাসরি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে নিজের করা সেরা কোডটি— সেই অনুযায়ী চাকরি দেবেন তাঁরা। অর্থাৎ, ডিগ্রি নিয়ে মালিকের মাথাব্যথা নেই। এই ভাবনা আরও সাংঘাতিক। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার দফারফা। ওঁর শুধু কাজের জন্য শ্রমিক চাই। মাস্কের সম্ভবত মনে হয় যে, ডিগ্রি না-থাকা প্রোগ্রামার বা মিথ্যে ডিগ্রি-থাকা রাষ্ট্রনেতা সামলানো অনেক বেশি সুবিধাজনক। শিক্ষাগত যোগ্যতা গুরুত্বহীন হলে কর্মীরা আরও বেশি নির্ভরশীল হবেন নিয়োগকর্তার উপরে— তাঁদের আদেশ মতো কোড করবেন, সৃষ্টি হবে পুঁজির। কর্মীরা সেই ব্যবস্থার নাটবল্টুমাত্র।
তবে লক্ষ করা ভাল যে, এঁরা কিন্তু দুর্দান্ত প্রোগ্রামার চাইছেন সব সময়। কারণ শুধু অগুনতি ঘণ্টা কাজ করার পেশিশক্তি নয়, এখানে মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন। শিল্পবিপ্লবের পরে এত যুগ কেটে গেলেও যেমন কৃষি বা শিল্পক্ষেত্র থেকে মানুষকে সরানো যায়নি, তেমনই সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও। অথচ আশঙ্কা— প্রোগ্রামারদের নাকি কাজ থাকবে না। আসল কথা, পুঁজিবাদীরা শুধু চাইছেন যেন গোটা দুনিয়া জুড়ে প্রোগ্রামারদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে নিম্নবিত্তের স্তরে নামিয়ে আনা যায়— আর্থিক দিক দিয়ে যদি না-ও হয়, নিরাপত্তা ও কাজের শর্তের দিক দিয়ে। সে জন্যেই যন্ত্রমেধার জুজু দেখানো হচ্ছে।
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও কথাই একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা মুশকিল। কিন্তু, এখনও অবধি আমরা যতটুকু জানি, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রোগ্রামারদের কাজ হারানোর সম্ভাবনা আদৌ সত্যি নয়। কিন্তু এই হাওয়া যদি তুলে দেওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে ভয় ধরবে প্রোগ্রামারদের মনে। অনেক কম বেতনে নিয়োগ করা যাবে তাঁদের। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তকে যতটা সম্ভব নিম্নবিত্তের শ্রেণিতে ঠেলে দেওয়ার যে সর্বজনীনতা, তার একটা বিশেষ উদাহরণ রূপায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়েই যদি প্রাণপাত করতে হয়, তা হলে অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না। মাস্ক-যুগের টেকনো-পুঁজিবাদ সেই ভাবনার সামর্থ্যহীন মজুর চায়।
একটি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির কথা বলে লেখা শেষ করি। শিক্ষক হিসাবে আমরা সাধারণত ছাত্রদের বলি, প্রোগ্রাম লেখার সময় চ্যাটজিপিটি-র মতো যন্ত্রমেধার সাহায্য না-নিতে— যাতে বোঝা যায়, ক্লাসে শেখানো বিষয়টা তারা কত দূর আত্মস্থ করতে পেরেছে। অন্য দিকে, এখন যাঁরা সফটওয়্যার ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁরা প্রোগ্রামের বেশির ভাগ অংশই পেয়ে যান ইন্টারনেটে খুঁজে, বা এআই টুল ব্যবহার করে। সেই উত্তর সব সময় ঠিক থাকে, এমনটা নয়। কিন্তু কয়েক বার চেষ্টা করলে, এবং নিজে বুঝে বার বার চ্যাটজিপিটিকে প্রশ্ন করে নিলে শেষ পর্যন্ত যন্ত্র এবং মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায় একটা চালু সফটওয়্যার দাঁড় করানো সম্ভব। অবশ্যই প্রোগ্রামারের বুদ্ধি লাগে এখানে। অর্থাৎ সেই টুলগুলোকে ব্যবহার করলে কোনও ক্ষতি নেই, বরং অধিকতর দক্ষতায় কাজটা হয়তো একটু কম সময়েই হয়। তাই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভাল ভাবে কাজ করতে গেলে এক দিকে যেমন নিজে ভাল প্রোগ্রাম লিখতে পারা জরুরি, তেমনই ডিপসিক বা চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ।
অন্য দিকে, সফটওয়্যার শিল্পের কর্তারা যদি মুনাফা বাড়ানোর তাগিদে ধরে নেন যে, চ্যাটজিপিটি দিয়েই প্রোগ্রামারের কাজ করে ফেলা যাবে, কর্মীদের আর প্রয়োজন নেই— সে ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের পায়ে নির্দ্বিধায় কুড়ুল মেরে যাচ্ছেন। গণকযন্ত্রের ব্যবহারে এখনও মগজাস্ত্রের প্রয়োজন।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)