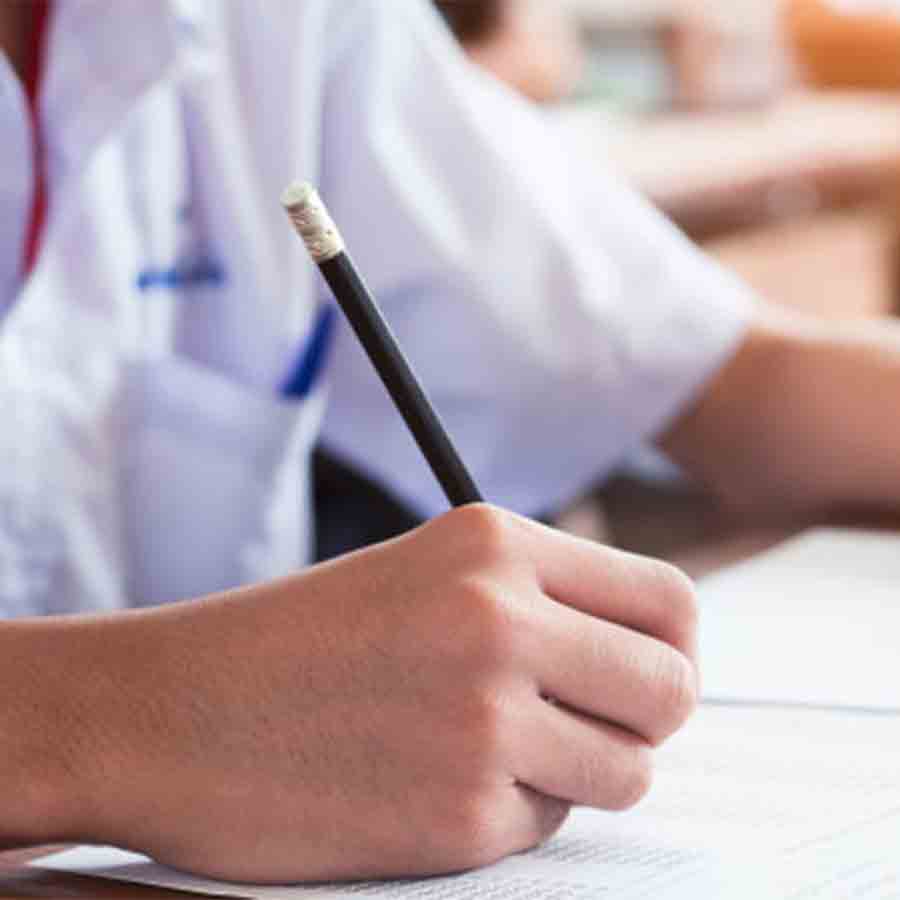চকচকে ফ্লেক্স, আলোর রোশনাই, নতুন বই আর কবিরাজি-কাটলেটের সুঘ্রাণ মিলেমিশে একাকার যেখানে, তার নাম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মেলায় ঢুকলেই একটা ফিল-গুড আবহাওয়া। নিজস্বী নিতে ব্যস্ত মানুষ, নানান ডেসিবেলের শব্দলহরি, স্টলে স্টলে সাজানো বই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় মানুষ বাংলা বই কিনছেন, হাসি ফুটছে কাগজ-বিক্রেতা, কম্পোজ়িটর, প্রুফ রিডার, বাইন্ডার, প্রচ্ছদশিল্পী, পুস্তক বিক্রেতা তথা প্রকাশকদের মুখে। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, সূর্য সেন স্ট্রিট, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো হয়ে একটু দূরের শ্রীমানী মার্কেট, এক কথায় কলেজ স্ট্রিট পাড়া একদা ছিল এশিয়ার বৃহত্তম বই বাজার। কত মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই বাজারের সঙ্গে যুক্ত তা জানার কোনও উপায় নেই, কারণ বইপাড়া আজও চরিত্রগত ভাবে অসংগঠিত। তবে খোঁজখবর নিলে জানা যায় যে সেন্ট্রাল পার্কের ভিতরটা যতই চকচক করুক, বাংলা বইয়ের বাজার ভাল নয়। কলকাতা বইমেলা এবং প্রতি বছর সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হাজারো বইমেলা পারছে না বাংলা বই বিক্রির হতশ্রী অবস্থা ঢেকে রাখতে।
এক সময় অনেককে সখেদে বলতে শুনেছি বাংলা বই মানেই গল্প-উপন্যাস আর দিস্তে দিস্তে কবিতা। এখন কিন্তু ছবিটা পাল্টেছে। কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় কাজ হচ্ছে, নন-ফিকশন আর ব্রাত্য নয়। কিন্তু ঠিক কী পরিমাণে ছাপা হচ্ছে বাংলা বই! এখানেই গন্ডগোল। প্রিন্ট অন ডিমান্ড প্রযুক্তিতে এখন বই ছাপা হয়। এক তরুণ প্রকাশক জানালেন, এই প্রযুক্তিতে গোটা কুড়ি বই ছাপিয়ে প্রকাশকরা হাজির স্টলে। লেখক খুশি, প্রকাশকের টাইটল-সংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু মার খাচ্ছে ব্যবসা। গুটিকয় বড় প্রকাশক বাদ দিলে এ ভাবে বই প্রকাশই আজ দস্তুর, কারণ প্রকাশকের আর্থিক দুর্বলতা। সঠিক বিপণন ব্যবস্থার অভাব, কী বই পাঠকেরা পড়তে চাইছেন সে বিষয়ে না জানা বা বোঝা বিষয়টাকে আরও জটিল করছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এক নতুন ‘স্কিম’ যার মূল কথা: লেখকের পয়সায় প্রকাশক বই ছাপবেন। বছরখানেক আগে এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁর কবিতার বই বেরিয়েছে। টাকা তাঁর, পরিবর্তে প্রকাশক তাকে পঞ্চাশটা বই দিয়েছেন। এখন তিনি সেই বই নিজেই বিক্রি করে কিছু টাকা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছেন। গল্পগুলো জানা, কিন্তু সঙ্কটের বহুমাত্রিকতা উপলব্ধির কোনও চেষ্টা নেই।
একটা সময় কলেজ স্ট্রিটের ব্যবসার ভরকেন্দ্র ছিল পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় সব বই এবং নবম-দ্বাদশ শ্রেণির কিছু বই সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তাই এই ক্ষেত্রটির ব্যবসা এখন সহায়িকা-নির্ভর। সেখানে বাজারের নিয়ম মেনে তুলনায় বড় প্রকাশকরা অনেকটা এগিয়ে, কারণ আজকাল সহায়িকার ভাল-মন্দ বিচার হয় চিত্রতারকা বা ক্রিকেটারের বিজ্ঞাপনে। একই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বভারতীয় বোর্ডগুলোর ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠলেও, তার জন্য প্রয়োজনীয় বই এখনও দিল্লি বা অন্য রাজ্যের প্রকাশনা-নির্ভর। এই বাজারে কেন কলেজ স্ট্রিট ঢুকতে পারছে না, তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। এ কথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে ডিজিটাল ব্যবস্থার ক্রম-অগ্রগতি ও প্রযুক্তির কল্যাণে মাগনা পিডিএফ বই-ব্যবসার অকল্পনীয় ক্ষতি করছে, কিন্তু একে পতনের একমাত্র কারণ ভাবলে ভুল হবে। এই চ্যালেঞ্জের মুখেও বিভিন্ন দেশে প্রকাশনা শিল্প চলছে, নিয়মিত বই প্রকাশ হচ্ছে।
বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এ রাজ্যে স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে গ্রন্থাগারগুলো। আজ তাদের দৈন্যদশা। লাইব্রেরিয়ান ও অন্যান্য কর্মীর পদ শূন্য, অবসরপ্রাপ্তদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। আগ্রহী পাঠক গেলেও ক্যাটালগ, বসার ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাঁরা দ্বিতীয় বার আসার উৎসাহ হারান। বই কেনার সরকারি বাজেটের অপ্রতুলতার কারণে প্রকাশকদের বিধি বাম। এ দেশে বাংলা-সহ প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষা দুয়োরানি। হিন্দির প্রতি সরকারের অকৃপণ সহযোগিতার কারণে শুধু দিল্লি নয়, পটনা, ইলাহাবাদ-সহ বিভিন্ন জায়গার হিন্দি ভাষার প্রকাশকরা অনেক বেশি সুবিধা পান।
এই প্রতিকূল অবস্থায় যথেচ্ছ ছাড় দিয়ে বই বিক্রির মরণপণ চেষ্টা আত্মঘাতী। বই বিক্রির বিষয়ে নতুন ভাবনার সন্ধানে অনেকেরই অনীহা। অতিমারির সময় অনলাইনে বই বিক্রি কী ভাবে করা যায় তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তাতেও ভাটা পড়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুখাপেক্ষী না হয়ে কলেজ স্ট্রিটকেই ভাবতে হবে, কী ভাবে বই বিক্রির বাংলা প্ল্যাটফর্মগুলোকে আরও সচল করা যায়। আকাশছোঁয়া কাগজের দাম ও অন্যান্য মূল্যবৃদ্ধির কারণে বইয়ের দাম স্বাভাবিক ভাবেই বেড়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাঙালি পাঠকের প্রতিক্রিয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। বইয়ের দাম নিয়ে তাঁরা বড় স্পর্শকাতর।
বইপাড়াকে বাঁচাতে হলে তার কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। বই প্রকাশনাকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। বইপাড়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা অস্বচ্ছতা। এই শিল্পে যাঁরা শ্রম দেন তাঁদের বেশির ভাগই অসংগঠিত, ন্যূনতম মজুরি মেলে না। বইপাড়ায় অজস্র প্রকাশক, বইয়ের প্রতি তাঁদের ভালবাসা নিয়ে প্রশ্ন নেই, কিন্তু শুধু আবেগে চিঁড়ে ভিজবে না। জানতে হবে প্রকাশনা শিল্পের বনিয়াদি কথাগুলো, হতে হবে পেশাদার। এ ক্ষেত্রে গিল্ডের মতো সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।
লেখক পাণ্ডুলিপি জমা দিলেন, প্রুফ রিডার বানান দেখে দিলেন, আর প্রচ্ছদ করে দিলেন এক জন: এই বাঁধা গতে চলবে না। বেশির ভাগ প্রকাশনা আজও চলছে কোনও ‘বুক এডিটর’ ছাড়াই, তাই ভাল বই হয়ে উঠছে না। লিটল ম্যাগাজ়িনকে এই আলোচনার বাইরে রাখছি, কারণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য অন্য। তবে যত দিন যাচ্ছে লিটল ম্যাগাজ়িনও আদতে বই হয়ে উঠছে, তাঁদের অনেকেই আজ প্রকাশক। বই পাড়ায় অস্বচ্ছতার আর একটা বড় প্রমাণ, গুটিকয় প্রকাশক ছাড়া অন্যদের লেখকদের রয়্যালটি দিতে অনীহা। লেখক জানতেই পারেন না ক’টা কপি বিক্রি হল। এত সব সত্ত্বেও বইপাড়া চলছে। আশার কথা, এক নতুন প্রজন্ম বইয়ের প্রকাশনায় আসছেন। তাঁদের চোখে স্বপ্ন আছে, নতুন কিছু করার ইচ্ছেও। বইপাড়ার খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার এটাই সেরা সময়।
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)