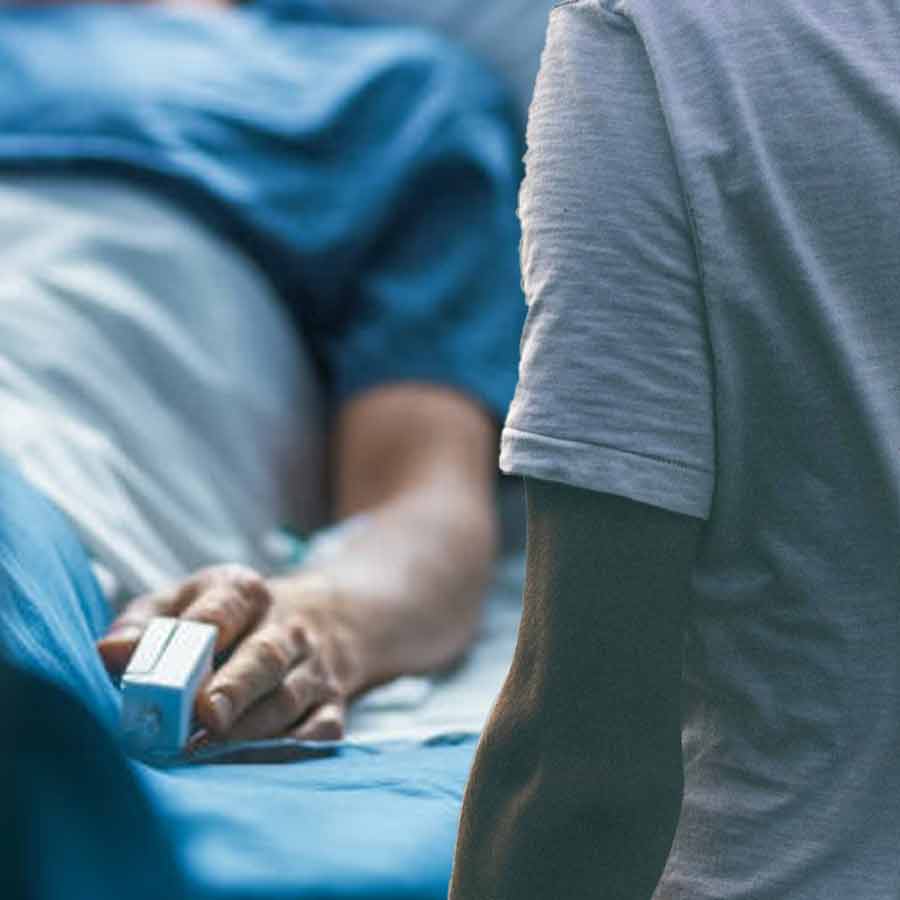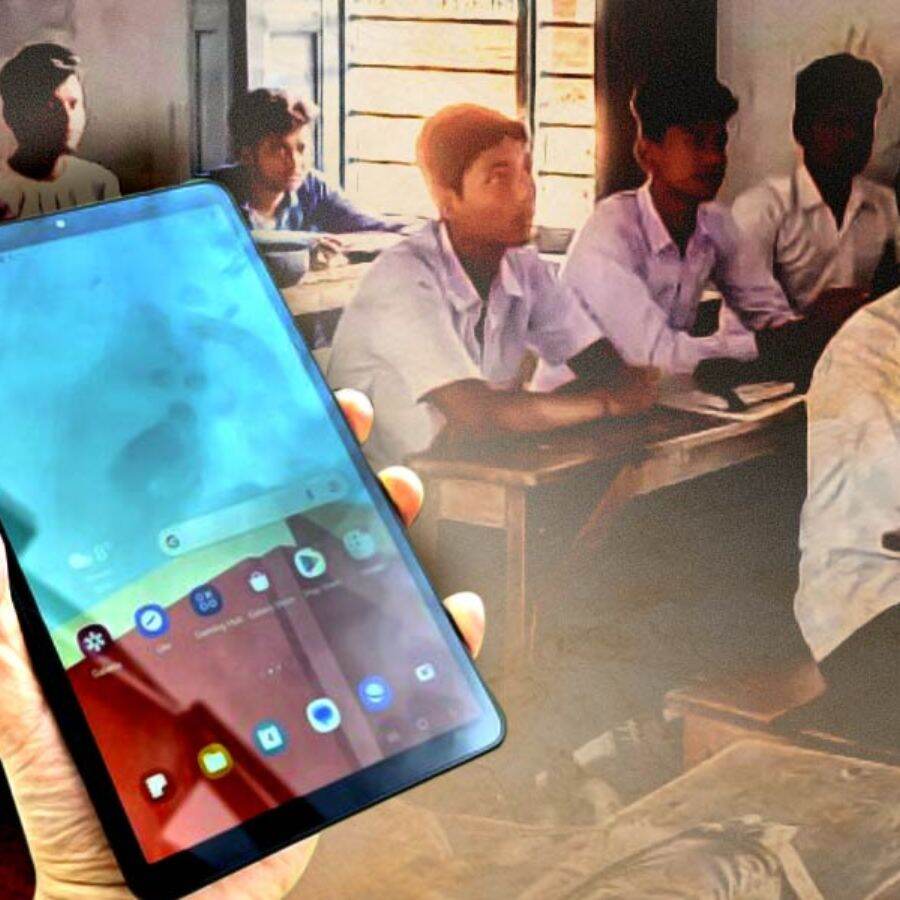‘নিলামে বুদ্ধের অস্থি, গয়না’ (৫-৫) প্রতিবেদন থেকে অবগত হলাম যে, গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ এবং তার সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মূল্যবান পাথর, সোনার গয়না নিলামে উঠতে চলেছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, নেপালের সীমান্তবর্তী উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পিপরওয়া নামের ছোট্ট গ্ৰামের এক বিশালাকার স্তূপের নীচে এই সম্পদ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৮ সালে ক্ল্যাকস্টন পেপে এটি আবিষ্কার করেন। এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত এবং চরিত্রগত দিক থেকে অনেকটাই সম্রাট অশোকের শিলালিপির মতো দেখতে ছিল। এই অভিলেখটি নাকি প্রাক্-অশোক যুগের। অভিলেখটি একটি পাত্রের ঢাকনার ধার বরাবর গোল করে লেখা ছিল। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও স্পষ্ট ছিল।
লিপির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, এই চিতাভস্মের আধারটি শাক্যবংশীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান বুদ্ধের। যেটি সুকিতি, তার ভাই-বোন ও তাদের স্ত্রী-পুত্র দ্বারা শুভ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বিভিন্ন সময়ে এই অর্থ নিয়েও পণ্ডিত মহলে বিভ্রান্তি তৈরি রয়েছে। কারও মতে অভিলেখতে উল্লিখিত এই সুকিতি হলেন স্বয়ং বুদ্ধ। পালি দীঘনিকায়ে মহাপরিনির্বাণ সুত্তে কপিলাবস্তুর শাক্যদের বুদ্ধের আত্মীয় বলা হয়েছে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর শাক্যরা বুদ্ধের চিতাভস্মের অংশ দাবি করে বলেন, ভগবান অমহাকং (আমাদের) জ্ঞাতি সেটঠো (শ্রেষ্ঠ)। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ আমাদের জ্ঞাতি শ্রেষ্ঠ ও শাক্যরা তাদের নিজস্ব অঞ্চলে বুদ্ধের চিতাভস্মের অংশ স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর চিতাভস্ম আট ভাগে ভাগ করা হয়,তার পর এটি বিবিধ রাজ্যের রাজবংশের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই আটটি ভাগের মধ্যে শাক্যদের একটি ছিল, সেটিই এই পিপরওয়া স্তূপের অংশ। সে দিক থেকে এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিস্ময়কর ভাবে এতগুলি বছর পরে আবিষ্কর্তার পরিবারের পক্ষ থেকে এই মূল্যবান সামগ্রী নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত অনৈতিক, অনভিপ্রেত। অতীতেও এককালীন বৌদ্ধ ভারতের এমন বহু নিদর্শন হাতছাড়া হয়েছে। এখনও তো বৈশালীর নাগরিকদের প্রদত্ত উপহার ভিক্ষাপাত্র অন্য দেশে (কাবুলের জাদুঘরে, কন্দহরে) সংরক্ষিত রয়েছে, ভারতে ফেরেনি। বহু আবিষ্কৃত নিদর্শন আবিষ্কর্তাদের নিজস্ব সংগ্ৰহে রয়েছে।
পবিত্র এই ধর্মীয় সামগ্ৰীর সঙ্গে সমগ্ৰ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িত। তা ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন বৌদ্ধ অনুরাগীরা। ভারত সরকার ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের কাছে নিবেদন, নিলাম নয়, হোক উপযুক্ত সংরক্ষণ। পূর্বে ও বুদ্ধের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মোগ্গলায়নের দেহাবশেষও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কলকাতায় বিশালকার সমাবেশে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এই অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন আজও কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। আলোচ্য স্তূপ হতে প্রাপ্ত এই ঐতিহ্যবাহী প্রত্নসামগ্ৰীও ভারতে ফিরিয়ে আনতে ও যথাযথ সংরক্ষণ করতে উদ্যোগ গ্ৰহণ করা হোক।
ইন্দ্রনীল বড়ুয়া, কলকাতা-১৫
প্রাণের বাঁধন
পীতম সেনগুপ্তের ‘জীবনের সঙ্গে জুড়ল কই’ (৮-৫) প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। খুব দুঃখজনক যে বাঙালির কাছে বৈশাখ মাসের তারিখ মানেই ১ বৈশাখ আর ২৫ বৈশাখ। বৈশাখ মাসের পরিচিতির ইতি হয় এখানেই। অথচ প্রকৃত রবীন্দ্রচর্চা আজকাল দেখাই যায় না। হ্যাঁ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখন পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করে। কিন্তু এই উৎসবের মধ্যে কি রবীন্দ্রচর্চা হয়? কে রবীন্দ্রনাথ আর কী-ই বা তাঁর ভাবনা, এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব দেখা যায় সমাজের প্রতি পরতে।
এর কারণ, আমাদের চিন্তার অভাব। অথচ প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি ক্ষণে আমাদের জীবনে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমাদের অবস্থা যেন খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর।
আজকের যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা ক্রমশ আটকে পড়ছি, সেই ধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য।” আজ থেকে কত বছর আগে তিনি বলেছিলেন এ কত বড় সর্বনেশে বিভেদ-বর্বরতার লক্ষণ! তিনি মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। বর্তমানে চার পাশের এই যে ধর্মীয় উন্মাদনার বাতাবরণ, সাম্প্রদায়িকতা, একনায়কতন্ত্র সর্বোপরি ফ্যাসিবাদের নানান চিত্র ভেসে বেড়াচ্ছে, সেই সম্পর্কে তিনি খেদ প্রকাশ করে গিয়েছেন পূর্বেই।
তিনি মনপ্রাণ দিয়ে সমাজ গড়ার কথা ভাবতেন। আর সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন শিক্ষায়। আজ সেই শিক্ষার কী হাল সেই বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই।
ভাববাদী, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবল ভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী ভয়াবহ রূপ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তাঁর লেখা ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লন্ডন থেকে। ১৯২৭ সালে বিখ্যাত ফরাসি মনীষী ও সাম্যবাদী নেতা রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে মত বিনিময় করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ও গুণিজনদের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। কবির সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থে ‘চলতি ছবি’ কবিতায় স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা, ছবি ফুটে উঠেছে।
পরিশেষে বলি, শুধু ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উৎসব পালনই যথেষ্ট নয়। দরকার প্রকৃত ‘রবীন্দ্রচর্চা’। এই চর্চা স্কুলে কলেজে কিংবা পাড়ার ক্লাবে সপ্তাহে দু’-এক দিন করাই যেতে পারে। এই চর্চা শুরু না হলে তিনি আমাদের জীবনের সঙ্গে আর জুড়ে থাকবেন না। জন্মদিনের ফুলের মালা যেমন ক্রমশ শুকিয়ে যাবে ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা আস্তে আস্তে হৃদয় থেকে হারিয়ে যাবে।
তমাল মুখোপাধ্যায়, ডানকুনি হুগলি
পিছিয়ে চলেছি
অনুরাধা রায়ের লেখা ‘এ বার কি উল্টো বিবর্তন?’ (১২-৫) খুবই প্রাসঙ্গিক। মানবতার এই চরম দুর্দিনে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য মহান ধর্মনিষ্ঠ নেতারা বর্তমানকে উপেক্ষা করে ২০৪৭ সালে ভারতকে বিশ্বের শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিণত করার স্বপ্ন দেখান, অথচ এঁদের শাসনযন্ত্রের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হয়ে ক্রমশ পিছনের দিকেই হাঁটছেন।
যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই বেছে নেবেন। সম্প্রতি জঙ্গিহানার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার যে প্রয়াস নিয়েছিল ভারত, তাতে কোনও ভারতবাসীরই বিরুদ্ধমত ছিল না বলেই মনে হয়। অথচ ভারত ও পাকিস্তানের মতৈক্যের ভিত্তিতে যখন দু’পক্ষই গোলাগুলি চালানো থেকে বিরত থাকবে বলে ঘোষণা করলেন ভারতের বিদেশ সচিব, তার পরই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন তিনি ও তাঁর পরিবার। দু’দেশের মধ্যে শান্তির দাবিতে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার জন্য আক্রমণ করা হয়েছে বামপন্থী মহিলা কর্মীদের, যুদ্ধ-বিরোধী মিছিলে মানবাধিকার কর্মীরাও আক্রান্ত হয়েছেন।
কিছু নেতা-কর্মীর এই ধরনের যুদ্ধবাজ আচরণ আঘাত করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়কেই, যা আমাদের দেশের পিছিয়ে থাকার দিকেই ইঙ্গিত করে। প্রবন্ধে খুব সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে রামমন্দিরের পাল্টা হিসাবে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কথা। মনে রাখা উচিত, সরকারি অর্থে এই নির্মাণ কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হতে পারে না। আর সেনাবাহিনীকে রাজনীতির আবহে টেনে আনার যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে ইদানীং, তাও খুবই উদ্বেগজনক বিষয়।
অশোক দাস, রিষড়া, হুগলি
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)