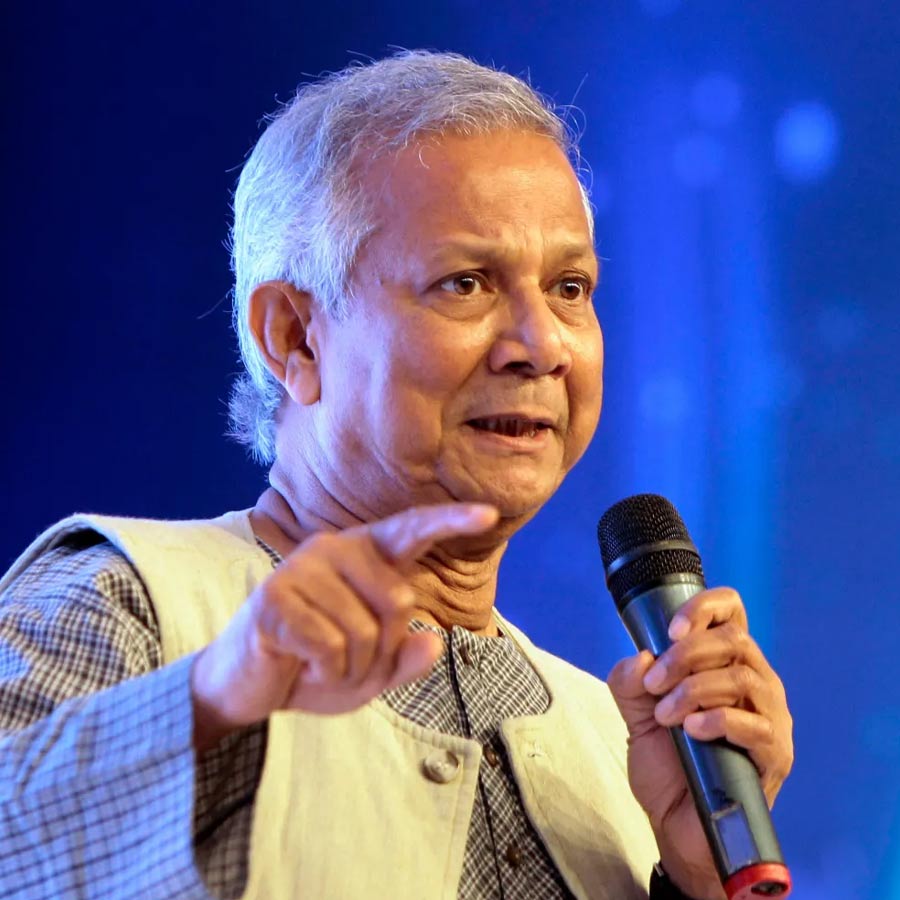‘ছুটির অনুদান’ (৫-৫) শীর্ষক সম্পাদকীয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। জনমানসে প্রশ্ন উঠছে, এত ছুটি কেন? আমরা গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যের বাসিন্দা। উত্তরের চারটি জেলা ছাড়া বাকি সব ক’টিতেই মে মাসে গরম থাকে। তাপপ্রবাহ এ রাজ্যে নতুন কোনও ঘটনা নয়। সে কথা মাথায় রেখেই স্কুল কলেজে গ্রীষ্মকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। সেই অবধি ঠিক থাকলেও, সমস্যা হয় ছুটি দীর্ঘায়িত হলে। সরকারের যুক্তি, এতে তাপপ্রবাহজনিত ক্ষয়ক্ষতির ভয় থাকে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। তবে এর পরোক্ষ লাভও কম নয়। স্কুল ছুটি থাকলে পর্যটন লাভবান হয়। তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়ে বাঙালিরা সামর্থ্য অনুযায়ী বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। এবং আশ্চর্য ভাবে, সেই বেড়ানোয় গরমের কোনও প্রভাব পড়ে না। দ্বিতীয় লাভটি আসে মিড-ডে মিল থেকে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রী স্কুলে দুপুরের খাবার খায়। এর জন্য ত্রিশ দিনে যে বিপুল পরিমাণ খরচ হয়, তার ৬০ শতাংশ আসে কেন্দ্র থেকে এবং বাকি অংশ বহন করে রাজ্য সরকার। দীর্ঘ দিন ছুটি থাকার অর্থ এই বিপুল ব্যয়ভার থেকে খানিক অব্যাহতি পাওয়াও বটে।
কিন্তু এ লাভের চক্করে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা, যারা মূলত পড়াশোনার জন্য স্কুলের উপরেই নির্ভর করে, এবং যাদের গৃহশিক্ষকের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা নেই। সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে এখন রাজ্যের স্কুলপাঠ্য বইগুলিও বিপুল তথ্যে সমৃদ্ধ, এবং সেগুলি নিবিড় পাঠ ও অনুশীলনের দাবি রাখে, যা দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া রপ্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য। দীর্ঘ ছুটিতে তাই এই সব দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যাদের বাড়িতে নজর দেওয়া হয় বা দক্ষ গৃহশিক্ষক যাদের ভাগ্যে জোটে, তারাই কেবল সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে সক্ষম হয়।
এ দিকে, সরকারি দফতর থেকে বিদ্যালয়ে ‘সামার প্রোজেক্ট’-এর নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তা বেশ বিজ্ঞানসম্মতও। সেখানে দলবদ্ধ ভাবে কাজ, নেতৃত্বদান, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক সচেতনতা, বাস্তব জগতে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া— প্রভৃতি বিষয়ে সক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নিরন্তর নজরদারি ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব কি?
গত বছরের দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আরও পিছিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় ভুগতে হচ্ছে বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রী— সকলকেই। সরকারি ‘কম্পোজ়িট গ্রান্ট’ নিয়মিত ও যথাযথ না আসায় স্কুলগুলি ভীষণ ভাবে আর্থিক সঙ্কটে দীর্ণ। এই সমস্যা থেকে মুক্তির আপাত উপায় আছে দু’টি। প্রথমত, দুপুরের পরিবর্তে সকালে স্কুলের আয়োজন করলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা যেমন অব্যাহত থাকে, তেমনই তাপপ্রবাহ থেকেও সুরক্ষিত থাকতে পারে তারা। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপক ভাবে বৃক্ষরোপণ করলে তা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে ছায়ার শীতলতায় ভরিয়ে দিতে পারে। এমনই উপায় আছে আরও। চাই কেবল বাস্তবায়নের সদিচ্ছা।
পার্থ পাল, মৌবেশিয়া, হুগলি
পিছিয়ে রাজ্য
‘প্রশাসনিক সমীক্ষায় পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ’ (৩০-৪) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেয়ারএজ-এর বার্ষিক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রশাসনিক দক্ষতায় সারা দেশের ১৭টি বড় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৩। উল্লেখ্য, আর্থিক, সামাজিক, রাজস্ব ও আর্থিক শৃঙ্খলা এবং নতুন শিল্প স্থাপন-সহ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠির ভিত্তিতে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। তাতে মহারাষ্ট্র শীর্ষে, পরের চারটি স্থানে যথাক্রমে গুজরাত, কর্নাটক, তেলঙ্গানা এবং তামিলনাড়ু বাংলার চেয়ে অনেক এগিয়ে। প্রথম দশের মধ্যে ন’টি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্য। ব্যতিক্রম ওড়িশা। তবে সামাজিক সুরক্ষায় বাংলা সবচেয়ে নিরাপদ— তৃণমূল সরকারের এমন প্রচার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী, এই মর্মে তার স্থান পঞ্চমে। কেরল কিন্তু এ ক্ষেত্রে শীর্ষে। আর আর্থিক ক্ষেত্রে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে উপরের দিকে রয়েছে গুজরাত, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র। এ ব্যাপারে ১৭টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১৬-তে। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে বাংলা অষ্টমে। দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যের সরকার সম্পর্কে শাসক দল তৃণমূল যতই গালভরা প্রচার করুক না কেন, বাস্তব চিত্র কিন্তু তা নয়। বাংলা নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে।
তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গে কিছু উন্নতি হচ্ছে, তা হলেও তা আশানুরূপ নয়। বরং, শাসক দলের দুর্নীতির জেরে প্রতি পদে বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষার মান এমনিতেই নিম্নমুখী, পাশাপাশি এ রাজ্যে দারিদ্র বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যও, যা সামাজিক সহাবস্থান তথা সম্প্রীতি নষ্ট করছে।
এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যবাসীর স্বার্থেই এর প্রতিবিধান দরকার। অতি শীঘ্র পরিত্রাণের উপায় বার করা খুবই জরুরি।
কুমার শেখর সেনগুপ্ত, কোন্নগর, হুগলি
সমাধান কই
‘অনাবশ্যক’ (৬-৫) শীর্ষক সম্পাদকীয়টির সঙ্গে সহমত পোষণ করেই দু’চার কথা বলতে চাই। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ছাত্র মাত্র ২৬ বছর বয়স্ক রোহিত ভেমুলা বঞ্চনা ও বিদ্বেষমূলক বাতাবরণে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। সেই সময় দলিত তথা জনজাতি গোষ্ঠীর এক জন শিক্ষার্থীর এই পরিণতিতে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নানা নামের তদন্ত কমিশন এবং বিভিন্ন সংস্থার পর্যবেক্ষণে মেডিক্যাল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত-জনজাতি গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নানা ভাবে হেনস্থার প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছিল। এমনকি আইআইটিতেও ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে দলিত ও জনজাতি গোষ্ঠীর পড়ুয়াদের মধ্যে।
সম্প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্ণবৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কর্নাটক সরকার এক নতুন আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে, যার নামকরণ হয়েছে রোহিত ভেমুলা-র নামে। কথা হচ্ছে যে, আইনের খসড়া প্রকাশ অবশ্যই গঠনতান্ত্রিকতার ফসল। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ তফসিলি জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের উপর হয়রানির তদন্তের স্বার্থে ২০০৭ সালে গঠিত সুখদেও থোরাট কমিটি এবং ২০১২ সালে ডা. মুঙ্গেকরের সভাপতিত্বে গঠিত এক স্থায়ী কমিটি তাদের পেশ করা রিপোর্টে জানিয়েছিল যে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলিত ও জনজাতি গোষ্ঠীর পড়ুয়াদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। এ ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রস্তাবও জমা দেওয়া হয়েছিল। সেগুলির বাস্তবায়ন কিন্তু এখনও হয়নি। ফলে বছরের পর বছর নতুন নতুন নামে আইনের খসড়া ও কমিটি গড়ে তোলার কি প্রয়োজন আছে?
বিশ্বজিৎ কর, কলকাতা-১০৩
দুঃসহ যাত্রা
কলকাতা বিমানবন্দরের এক নম্বর গেট সংলগ্ন ভিআইপি রোডের অটো স্ট্যান্ড এলাকায় কিছু ক্ষণ জোরে বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে যায়। ফি বছরের মতো আসন্ন বর্ষাতেও এই দুর্ভোগ আরও প্রকট হবে। আবার, অটো স্ট্যান্ড লাগোয়া ফুটপাতে চায়ের ও খাবারের দোকানদারদের অবৈধ দখলদারির ফলে পথ চলা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, ফুটপাতগুলির অবস্থাও ভাল নয়। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
আহমদ মুসা, কলকাতা-১৩৬
এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন
5,148
1,999
429
169
(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)