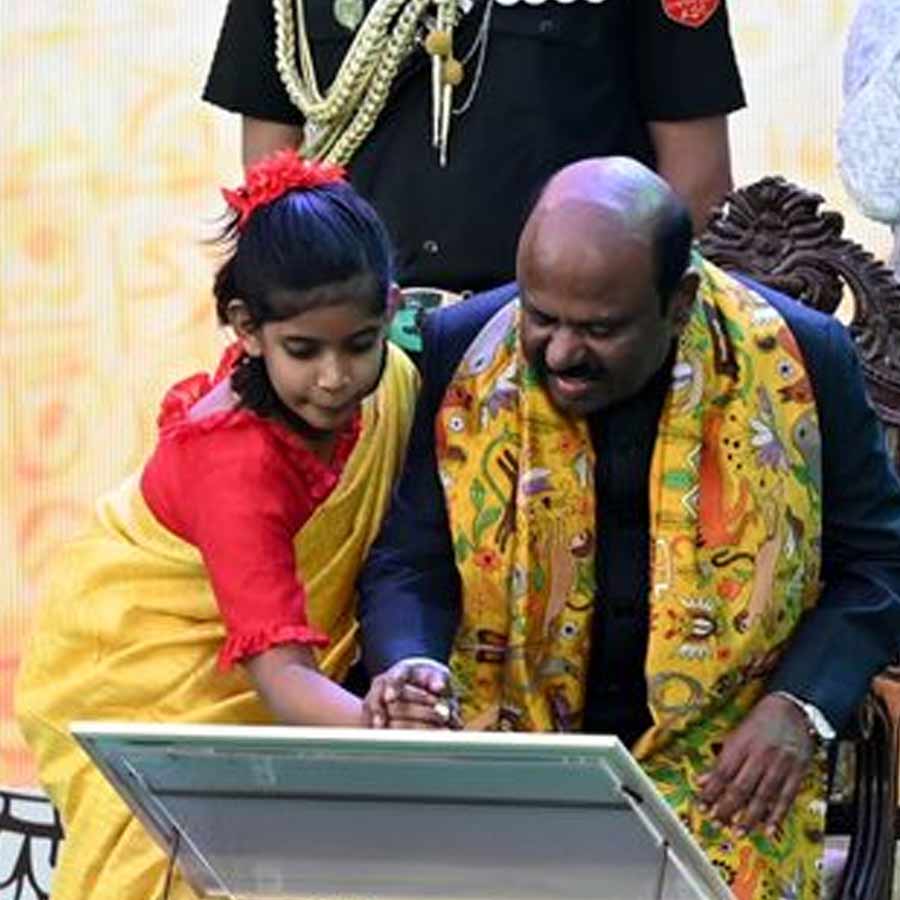খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছত্রিশে গ্রিস দেশের করিন্থ্ নগরে এক জন রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে-খাওয়া জীবনধারণকারী পথবাসী দার্শনিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সম্রাট আলেকজ়ান্ডার। এই দার্শনিকের নাম ডায়োজিনিস। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঠেলাগাড়ির নীচে বসবাসকারী সযুগ্বা বৈক্ব যেমন নানা দুরূহ বিদ্যার অধিকারী বলে খ্যাতিমান ছিলেন, সে রকম ডায়োজিনিসও ছিলেন প্রজ্ঞাবান হিসেবে স্বদেশে-বিদেশে পূজিত। শীতের সকালে রাস্তার মাঝখানে প্রায় দিগম্বর অবস্থায় রোদ পোহাচ্ছিলেন এই অকিঞ্চন, অনিকেত, অগাধ পাণ্ডিত্যশালী দার্শনিক। বর্মচর্মধারী সৈন্যসান্ত্রি পরিবেষ্টিত আলেকজ়ান্ডার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘‘আমি শুনেছি আপনি প্রকাণ্ড বিদ্বান। আমি বিদ্যার সম্মান করতে চাই। আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?’’ তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ডায়োজিনিস বলেছিলেন, ‘‘আপনি রোদটা আড়াল না করে একটু সরে দাঁড়াতে পারেন।’’ তাঁর বিদ্রুপ অ্যারিস্টটলের ছাত্রকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্যার ঐশ্বর্যের কাছে যুদ্ধশৌর্য, ধনমদ ও রাষ্ট্রশাসনের ঔদ্ধত্যকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল।
ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য (যাঁর বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ী ‘বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি হয় না, যা দিয়ে আমি অমৃতা হব না তা দিয়ে আমি কী করব?’ বলে সত্যিই অমৃতা হয়ে আছেন) তিনি কিন্তু অল্প বয়সে ডায়োজিনিসের মতো অতটা ধনসম্পদে বিমুখ বৈরাগী ছিলেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ‘ফিলোজ়ফার কিং’ রাজর্ষি জনকের সভাতে যখন ‘‘শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীকে সোনা বাঁধানো শিংওয়ালা একশো গাভি দান করা হবে’’ এই ঘোষণা করা হল, আর অন্য পণ্ডিতরা সভাস্থলে চুপ করে ছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে শিষ্যকে বলেছিলেন, ‘‘ওহে, এই গরুগুলোকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও’’— আমি ব্রহ্মজ্ঞানীশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করছি। আমার দরকার ওই গরুগুলিকে। ‘‘নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মঃ। গোকামা বয়ম্।’’ তার পরে অবশ্য অনেক শোরগোলের মধ্যে পর পর অনেক তার্কিক, প্রাশ্নিক, বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রশ্নের, আর সব শেষে বাক্পটীয়সী দুর্দমনীয়া গার্গীর খরশান দু’টি সওয়ালের জবাব দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের আত্মতত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যই হল দামি দামি গাড়িঘোড়া চড়া, এ কথা ডায়োজিনিস বা যাজ্ঞবল্ক্য কেউই মানতেন না। বিদ্যা ডায়োজিনিসকে ততটা বিনয় বা নম্রতা দেয়নি কিন্তু নির্ভীক ও নির্লোভ করেছিল। বিদ্যার ফলে যাজ্ঞবল্ক্যও হয়েছিলেন নির্ভয় এবং রাজার সঙ্গেও পরিহাসে অসঙ্কোচ।
আজ ভারতে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা। উৎকট অনাহার, অর্ধাহারের ও অশিক্ষায় অপুষ্টিতে তমসাচ্ছন্ন দেশ। নির্লজ্জ অতিধন, অতিভোগের সমাজে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিকরা হয় বেসরকারি দাক্ষিণ্য ও খয়রাতের প্রত্যাশী, নইলে ক্ষমতার কাছে সর্বদাই সুখহীন পরাধীন হয়ে দীনপ্রাণে ‘গ্রান্ট’ প্রত্যাশী। পিতামাতাও পুত্রকন্যাদের ভাল ‘আন্তর্জাতিক’ (=মার্কিন) ইস্কুলে পড়িয়ে, তদুপরি গৃহশিক্ষকের বিদ্যাদানে দিগ্গজ বানিয়ে কোটিপতি করার স্বপ্ন নিয়েই ‘মানুষ করে তোলেন’।
গ্রিস দেশের শহরগুলিতে এই রকম পরীক্ষা পাশ-করা, আইনজ্ঞ, রাজনীতিকুশল, বাণিজ্যসফল, ‘শিক্ষিত’ মানুষ কম ছিল না। তবু সেই জনাকীর্ণ শহরেও দিনের বেলা ডায়োজিনিস হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘুরতেন। বলতেন, ‘‘মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি।’’ আজ দিল্লিতে, কলকাতায়, মুম্বইয়ে, নিউ ইয়র্কে বা লন্ডনে থাকলেও ডায়োজিনিসকে লণ্ঠন হাতে ঘুরতে হত। হাতে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপের অত্যুজ্জ্বল পর্দার ঝলসানি সত্ত্বেও ঈর্ষা ও বিষাদের অবিশ্বাস ও অসহানুভূতির তমসায় এখানে এখন ‘দিনেতে অন্ধকার’। এই অবিদ্যার অন্ধকারে আমরা কোন বিদ্যাদেবীর আরাধনা করতে চলেছি?
লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদভঞ্জন
সরস্বতীর পূজা করা মানেই যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বা গ্রিক ‘সিনিক’ দার্শনিকদের মতো নিষ্কপর্দক ‘গরিব ব্রাহ্মণ’ হয়ে জীবন কাটাতে হবে তা নয়। ঋষি বিশ্বামিত্র, যিনি গায়ত্রীমন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা হয়েও বশিষ্ঠের গরুটার লোভে অনেক তপস্যা-টপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব ছেড়ে ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জন করেছিলেন বলে পুরাণ কথা আছে, তিনি সরস্বতী সম্বন্ধে বলেছেন, এই সরস্বতী আমাদের পবিত্র করেন। ‘‘বাজেভির্বাজিনিবতী’’ (ঋগ্বেদ ১-৩-১০)। এই জ্ঞানের সমুদ্রস্বরূপিনী বাগ্দেবী অনন্ত অপার সত্যের অধিষ্ঠান। তিনিই রাষ্ট্রী (অবশ্যই এই রাষ্ট্রশক্তি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ফুকো-কথিত গভর্নমেন্টালিটি নন)। বাগ্দেবী স্বয়ং দেবীসূক্তে বলেছেন, রুদ্রের ধনুকে টঙ্কার দিয়ে তিনিই সমস্ত ধন আহরণ করে আনেন, জনতার জন্য তিনিই সমরাঙ্গনে নেতৃত্ব দেন, তিনি আকাশ অন্তরিক্ষ দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপ্ত করে ঋত, সত্য, জ্ঞান রূপে বিরাজিতা। আবার এই সরস্বতীই বিশ্বরূপা, তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য কোথায় না যায়?
আসলে প্রাচীন বৈদিক দেবতা সরস্বতী যেমন জ্ঞান ও শব্দরূপা তেমনই নদীরূপা। অধুনা লুপ্তধারা সরস্বতী নদী রূপে তিনি উত্তরপশ্চিম ভারতকে একদা সরস করে প্রবাহিতা ছিলেন। তাই সতত পরিবর্তনশীলা সজীব ভাষারূপে, নদীরূপে, দেবীরূপে তিনি সব জননীর শ্রেষ্ঠা জননী। সব সমৃদ্ধির দাত্রী, সৎবুদ্ধির প্রেরণা দিয়ে সত্যের দিকে নিয়ে যান এই সর্ববিদ্যার শুক্লাভরণে মণ্ডিতা ‘অম্বিতমা’— সবার চেয়ে বেশি মা।
কোন বিদ্যা আমাদের ভয় থেকে অভয়ে নিয়ে যাবে? এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি সাম্রাজ্যশাসক মানবশরীরধারী মহিষাসুর, যার নামেই রয়েছে খেলা জিতবার অথবা যুদ্ধজয়ের সদম্ভ ঘোষণা। ছলচাতুরি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভেদনীতি, কাঞ্চনকৌলিন্যের উলঙ্গ উন্মাদনা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রোড়পতিদের গগনচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ— এটাই তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের ভিত্তি। আশ্চর্যের কথা হল যে ভারতে এবং আমেরিকায় যাঁরা সব থেকে বেশি মারকুটে হিন্দু এবং ‘বৈদিক সভ্যতা পুনরুদ্ধারের দ্বারাই ভারত জগৎসভায় নয় জগৎবাজারে শ্রেষ্ঠ আসন লবে’ বলে দৃঢ়নিশ্চয়, তাঁরাই এঁর পরমত অসহিষ্ণু ‘আসুরী সম্পদ’-কে সমীহ এবং শ্রদ্ধা করেন। এঁর একমাত্র বিদ্যা হল বাণিজ্যবিদ্যা এবং এঁর চরম শত্রু হল সব রকমের সৎসাহসী সাংবাদিকতা। ইনি প্রায় সব বাস্তব সংবাদকে ‘‘জাল খবর’’ বলে উড়িয়ে দেন। সব সমালোচনা ও বিতর্কের কণ্ঠরোধ করে যুক্তরাষ্ট্রকে একটা দেওয়ালঘেরা দুর্গে পরিণত করবার স্বপ্ন দেখেন। শান্তি ও পরমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি ভেঙে ফেলে, খ্যাপা মহিষের মতো ‘খুরক্ষুণ্ণ মহীতলঃ’ প্রতি দিন প্রত্যুষে টুইটে নানাপ্রকার রণহুঙ্কার ছাড়েন।
এঁর এবং এঁর সমর্থকদের বিষয়েই ঈশ উপনিষদ বলেছে, ‘‘অবিদ্যাতে যারা রত থাকে তারা অন্ধতমিস্রায়— ঘোর আঁধারে— প্রবেশ করে।’’ আসলে এটা পূর্বপশ্চিম বা আমেরিকা বনাম ভারতের বৈপরীত্যের ব্যাপার নয়। ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতিও এখন চিন ও আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অল্প বেতনে শ্রমিক খাটিয়ে বেশি মুনাফার ‘উদ্বৃত্ত আয়’-এর দিকে ঝুঁকেছে। দারিদ্র দূর না করে আসুরী সম্পদেই ‘উন্নয়ন’-এর পথে এগিয়েছে।
ভয় থেকে অভয়ে
কিন্তু পাশ্চাত্যেও প্রজ্ঞা ও যুক্তিপরায়ণ সমাজকল্যাণচিন্তক আদিবিদ্বান সক্রেতিসকে মানা হয়। আজও সমস্ত লিবারেল আর্টস কলেজে এবং শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানপ্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদেরও অন্তত একটি ক্লাসে সক্রেতিসের কথোপকথন ও মৃত্যুদণ্ডস্বীকৃতি ‘জবানবন্দি’ পড়তে হয়। তেমনই প্রাচ্যে— ভারতের সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ে বি এসসি, বি কম, বি এ, বি টেক— পাঠ্যক্রমে অন্তত এক বার কঠোপনিষদের নচিকেতার কাহিনি পড়ানো উচিত। সক্রেতিস ও নচিকেতা, দু’জনের কেউই লৌকিক অর্থে ‘বিদ্যাবারিধি’ (আজকাল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ‘পিএইচ ডি’-কে এই অনুবাদ করা হয়) ছিলেন না। কিন্তু প্লেটোর মাস্টারমশাই আর বাজশ্রবার কিশোর পুত্রের মধ্যে তিনটি খুব বড় বড় মিল খুঁজে পাই।
প্রথম মিল হল এই যে দু’জনেই প্রশ্ন করতে ভালবাসেন। আর প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো না পাওয়া পর্যন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে থাকেন। নচিকেতা বাবার কথায় দুঃখ পেয়ে সোজা যমের বাড়ি পৌঁছে জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পর মানুষের কিছু বাকি থাকে, না থাকে না? মৃত্যুদেবতা বার বার বলেছিলেন, ‘‘এ বড় শক্ত সওয়াল। দেবতারাও এ নিয়ে ধন্দে পড়ে যান। এই মরণের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটিয়ো না, অন্য কিছু জিগেস করো।’’ শুধু তা-ই নয়, মৃত্যুজিজ্ঞাসু নচিকেতাকে গাড়িঘোড়া নারী-নৃত্যগীত ঘুষ দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলেন যমরাজ। কিন্তু সক্রেতিস অনেক ক্ষমতাশালী শিষ্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও, অন্যায় ভাবে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পালিয়ে যাননি, বরং ‘শরীরের মৃত্যুর পরেও আত্মা মুক্ত হয়ে থেকে যায়’ এই দার্শনিক আলোচনা করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। নচিকেতা যমরাজকে স্পষ্ট বললেন, ‘‘আপনার গাড়িঘোড়া নাচগান আপনারই থাকুক। আসল আত্মবিদ্যা যদি আমি অর্জন করতে পারি, যশ অর্থ এমনিতেই আমার কাছে আসবে। ও সব আমাকে চাইতে হবে না।’’
দ্বিতীয় মিল হল এই যে ‘ন-চিকেতা’ নামটার মানেই হল, যে জানে যে; সে জানে না। ঠিক এই কথাটাই সক্রেতিস নিজের বিষয়ে বলতেন। ডেলফির দেবালয়ে দৈববাণী হয়েছিল যে আথেন্সে সব থেকে জ্ঞানী সক্রেতিস। তত্ত্ববিদ্যাগুরু তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, ‘‘আসলে আমি তো জানি আমি কিছুই জানি না, সে জন্যই দেবী আমাকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলেছেন।’’ এ একেবারে ‘কেন’ উপনিষদের প্রতিধ্বনি। তৃতীয় মহান সাদৃশ্য হল, আসল বিদ্যা জ্ঞানীকে দিয়ে করায় ‘জানার মাঝে অজানারই সন্ধান’। এঁরা দু’জনেই নিতান্ত নির্ভয়। সত্যের জন্য, সত্যানুসন্ধানের জন্য, নিজের স্বরূপ জানবার জন্য মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করে নিতে, অথবা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে মৃত্যুরই রহস্য জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাননি সক্রেতিস অথবা নচিকেতা।
আমি একুশ শতকের ‘প্রগ্রেসিভ’ বাঙালি বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসাশিল্প ম্যানেজমেন্টের ছাত্র এবং ইতিহাস, দর্শন, তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যেতাদেরকে কঠোপনিষদ পড়তে বলছি এই জন্য নয় যে, তাতে আত্মা এবং ওঁকারের তত্ত্ববিদ্যার চর্চা করে তাঁরা হিন্দুধর্ম, ভারতীয়তা বা বৈদিক সভ্যতার পুনর্জাগরণ করাবেন। মিশেল ফুকো সারা জীবন যৌনতার ও উন্মাদ রোগের এবং কারাগারের দণ্ড-নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করার পর, জীবনের শেষ দশকে প্রাচীন গ্রিসের বৌদ্ধিক ইতিহাস থেকে এই একটি চারিত্রিক গুণ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সেই গুণটির নাম ‘ক্ষমতার বিরুদ্ধে, মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করে, সম্পূর্ণ সত্য বলার অভ্যাস।’ গ্রিক ভাষায় এর নাম ‘প্যারহেসিয়া’ (Parrhesia) আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে সর্বোক্তি— কিছু না রেখেঢেকে সৎসাহসের সঙ্গে সব কিছু খুলে বলা। নচিকেতার গল্পে, জাবাল সত্যকামের গল্পে, উপনিষদের আরও নানা জায়গায়, আমরা এই নির্ভীক সত্যকথনের নৈতিক জীবনাদর্শ স্থাপনকারী আখ্যায়িকা পাই। ফুকোর দোহাই দিয়ে বোঝালাম কারণ বিদ্যার দ্বারা যে সত্য উদ্ঘাটনের সাহস এবং নির্লোভতা আসে তা কেবল সংস্কৃত বা বৈদিক কাহিনি দিয়ে বোঝালে শিক্ষিত বাঙালির মনে তাচ্ছিল্য বা সাংস্কৃতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার ভয় আসা স্বাভাবিক।
পাঠ্যক্রম ও বিদ্যা বিভাজন
ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ— এই চারটিকে বুঝে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য শীক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই ছ’টি বেদাঙ্গ, রাজনীতি ও দণ্ডনীতি বিষয়ক অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ- যুদ্ধবিদ্যা, গান্ধর্ববিদ্যা: নাচগানবাজনার শাস্ত্র, আর আয়ুর্বেদ তথা চিকিৎসাবিজ্ঞান— এই সব মিলে চতুর্দশ বিদ্যাস্থান। সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দেওয়ার সময়ে এই চোদ্দোটি ‘সাবজেক্ট’-এ যেন বুদ্ধি আমার বিকশিত হয়, সেই জন্য প্রার্থনা করা হয়, ‘বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।’ আর মন্ত্রের মানে না-বুঝে আউড়ে যাওয়া পুরোহিতকে ঠাট্টা করে বাঙালি বাবা-জ্যাঠারা পরীক্ষাভিতু ছাত্রছাত্রীদের ভুল উচ্চারণ করে বোঝাতেন, ‘‘বিদ্যাস্থানে ভয়ে ব চ।’’
দেবী সরস্বতী এই সব বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। শুধু লেখা-পড়া-গণিত নয়, বিদ্যার পুজো মানে সামাজিক, বিনোদন, ললিতকলা ও সাহিত্যের চর্চা করা। ঈশ উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইয়েরই প্রয়োজন বলা হয়েছে। অবিদ্যা মানে কর্ম বা প্র্যাকটিস। থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের, প্রজ্ঞা ও পেশার, উদ্ভাবনী প্রতিভা আর চিরায়ত শাস্ত্রের মধ্যে সুষম সমুচ্চয় (ব্যালান্স) করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।
এই হল সেই বিদ্যা, যা মানুষ তৈরি করে। বিশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা দার্শনিক লুডউইগ হ্বিটগেনস্টাইনকে এক ছাত্র প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনার দেখা ‘জিনিয়াস’-দের কথা বলুন।’’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘‘জিনিয়াস অনেক দেখেছি, মানুষ দেখেছি কম।’’ শুনিয়েছিলেন একটি গল্প। লন্ডনে ঘর ভাড়া করতে এক দিন হ্বিটগেনস্টাইন সারা দিন ঘুরছেন বিজ্ঞাপন হাতে, সর্বত্র শুনছেন ঘর ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। শেষ বাড়িটিতেও বিফল হয়ে যখন ফিরে আসছেন, তখন গৃহকর্ত্রী ডেকে বললেন, ‘‘এক কাপ চা খাবেন?’’ পিছনে বসেছিলেন গৃহকর্তা, খবরের কাগজের আড়ালে মুখ। সে ভাবেই বলে উঠলেন, ‘‘জিজ্ঞাসা কোরো না, চা দাও।’’ হ্বিটগেনস্টাইনের মতে, সেই মুখ না-দেখা ব্যক্তিই হল তাঁর দেখা মানুষ।
কিছু দিন পরই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দু’শো বছর পূর্তি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ মেতে উঠবে। তখন যেন আমাদের মনে থাকে, যে বিদ্যার জন্য তাঁর ‘বিদ্যাসাগর’ নাম হয়েছিল, সেই বিদ্যা তাঁকে ‘দয়ার সাগর’-এ পরিণত করেছিল। শুধু হোয়াটসঅ্যাপে নিজের মুখচ্ছবি তুলে তৎক্ষণাৎ পাঠানোর বিদ্যা, আর গুগল-নির্ভর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তথ্য আহরণ করে ব্যবসায়ে বা নির্বাচনে জেতা যেতে পারে, নিষ্ঠুরতার অসুখ সারে না।
ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক (স্টোনি ব্রুক)-এ দর্শনের শিক্ষক