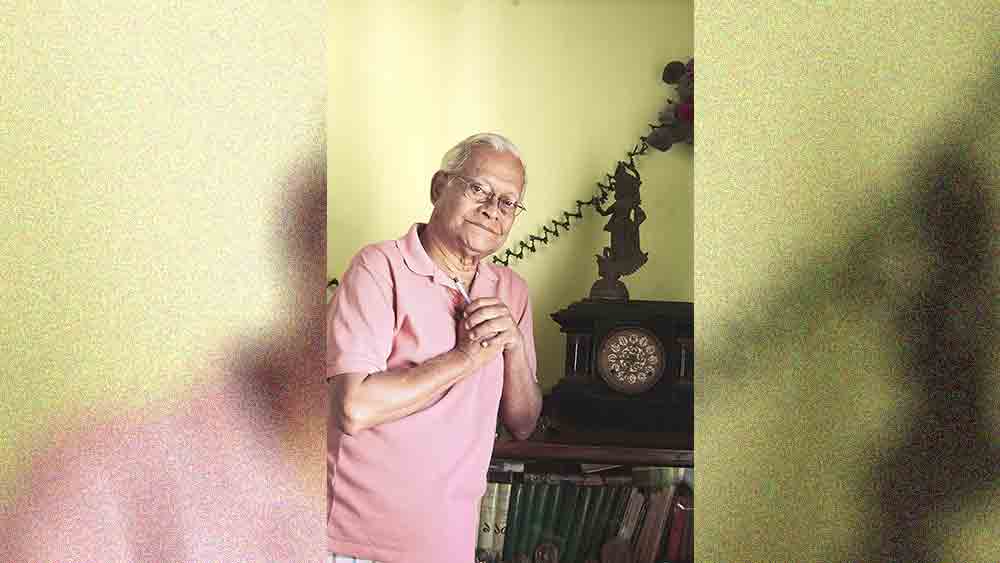মতি নন্দী বলেছিলেন, তিনি হিংসে করেন ক্রীড়াসাংবাদিক মতি নন্দীর জনপ্রিয়তাকে! খবরের কাগজে রোজ যাঁর বাইলাইন (নাম) দেখা যেত। এখন কাগজ খুললে সেই সাহিত্যিক মতি নন্দীকেই মনে পড়ে।
ঘোর গ্রীষ্মে জলকলের ঠাসাঠাসি লাইনের ছবিতে তাঁর ছোটগল্প (জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ)। চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ধাক্কায় বা নিজের বাড়ির স্বপ্নপূরণে মধ্যবিত্তের মরিয়া খরচ বাঁচানোর রোজনামচাতেও (কপিল নাচছে, চতুর্থ সীমানা) তাঁকেই পাই। তিনি তো আছেনই আদিবাসী মেয়ের ফেনা ভাত খেয়ে ফুটবলে মর্যাদা লাভের গল্পে। কিংবা ক্যানসারকে তুচ্ছ করে বিদেশি যুবার দুঃসাহসী সাইকেল অভিযানের নিউজ স্টোরিতে! মনে পড়ে, প্রায় পাঁচ দশক আগে আনন্দমেলার পুজোসংখ্যায় রিউম্যাটিক হার্ট ডিজ়িজ়ে কাবু কিশোরের অ্যান্ডি রবার্টস হওয়ার ব্যর্থ স্বপ্নের কথা লিখেছিলেন (অপরাজিত আনন্দ)। মহাকাব্যে রথের চাকা ডুবে যাওয়া পরাজিত নায়কের মতো যে নিজেকে, কল্পনায় জীবনের শেষ সুযোগের সামনে দাঁড় করায়। যে কোনও লড়াই, ঘুরে দাঁড়ানো, প্রতিকূলতা জয় করে আলোয় ফেরার গল্পে সাংবাদিক মাত্রেরই লোভ হয়, ‘ফাইট কোনি, ফাইট’টা গুঁজে দিই। অভিযোগ, মতি নন্দীর গল্প উত্তর কলকাতার গলি থেকে বেরোতে পারে না! কিন্তু কানাগলিতে ঠেকে গিয়েও তা অতল সমুদ্দুরের হদিস দেয়।
তারক চ্যাটার্জি লেনের লোকটা
২০১০ এর ৩ জানুয়ারি। কলকাতার এক মিঠে শীতের দুপুরে নিমতলায় যাওয়ার পথে শববাহী গাড়িতে শেষ বার তাঁর জন্মস্থানের গলিটায় গিয়েছিলেন। ঠিকানা, ২৫ নম্বর তারক চ্যাটার্জি লেন। সে-বাড়ির তেতলার ছাদ থেকে দেখা পৃথিবীটাই গল্প, উপন্যাসের খাতায় খোদাই করে গিয়েছেন। তাঁর তিন নম্বর প্রকাশিত গল্প ‘বেহুলার ভেলা’ বেরোয় ‘পরিচয়’-এর পুজোসংখ্যায়। তাতে গলির নিম্নবিত্ত সংসারে মাসের শেষে অপ্রত্যাশিত মাংস রান্নার অভিঘাত। পাঠকমনে এর পরেই পাকা হয়ে যায় মতির বসত। তেতলার ছাদের ঘরটা এর আগের অজস্র, জন্মেও না-জন্মানো ছিঁড়ে ফেলা গল্পের সাক্ষী।
এ গলির সঙ্গে জুড়ে থাকা বিভিন্ন গলির নকশা যেন অভিন্ন সত্তা মতির। মধ্যজীবনে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে এঁকেছেন হেদোয় স্কটিশ চার্চ স্কুল থেকে গলিপথে বাড়ি ফেরার স্মৃতিচিত্র! দর্জিপাড়ার ছেলে ‘নতুনদা’কে শরৎচন্দ্র কেন এত বদনাম করলেন ভেবে তখনও অভিমানাহত উত্তরের গলির শাবক। মতিদের গলিতে দু’জন পদ্মশ্রীর বাস। অবিনাশ কবিরাজদের বাড়ির বৌমা ইংলিশ চ্যানেলজয়ী আরতি গুপ্ত (সাহা) এবং গোষ্ঠ পাল। সুরশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমান মুখোপাধ্যায়ও সেই গলির সন্তান। বন্ধু বিমানের অনুরোধে তরুণ মতি গানও লিখেছেন।
পাশেই সোনাগাছি। মতি ভোলেননি, ঘোর শৈশবে জনৈক বারাঙ্গনার ঘরে ‘আঁটকৌড়ে’ তোলার আচার। আঁটকুড়েত্ব ঘোচার অনুষ্ঠানে ডাক পেয়ে গিয়ে বালক মতি পেয়েছিলেন একটি দু’আনি! “আমার প্রথম আয়।” এ দু’আনিটা মতিকে ‘অভিভুত’ করে রেখেছিল বহু দিন। তবে পরে ওটা চুরি যায়, যেমন চুরি গিয়েছিল তাঁর কিশোরবেলায় ৭২ জন ফুটবল তারকার ছবির অ্যালবাম! তাতে বিজয়দাস ভাদুড়ি থেকে হাফিজ রশিদ, জার্ডিন, করুণা ভটচাজদের মুখ।
১৯৮১তে উল্টোডাঙার ফ্ল্যাটে চলে যান মতি। তখনও চিরঅভিমানী বালকের মতো পুষে রেখেছেন, ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকির অপরাধে কন্ডাক্টরের অপমানের গ্লানি, গনগনে খিদে নিয়েও দর্জিপাড়ার ননীর দোকানে সন্দেশ কিনতে না-পারার যন্ত্রণা। উত্তর কলকাতা তাঁর চেতনায় আর গেঁথে দিয়েছিল, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে গলিতে অস্থিচর্মসার মৃতা নারীদেহ। এবং ছেচল্লিশে বাড়ির ছাদ থেকে দেখা দাঙ্গায় আক্রান্ত মুসলিম কিশোর কচিকে। সে খুন হয়েছিল। দু’দশক বাদে ‘দ্বাদশব্যক্তি’ উপন্যাসে চেতনায় মিশে যাওয়া কাঁকরের কথা লেখেন মতি। যা থেকে সারা জীবনেও রেহাই পাওয়া মুশকিল। কচি কাঁকর হয়ে মতির মগজে বসবাস করেছে।
‘আমার বুড়ি মা’কে
১৯৫৯-এ প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ‘নক্ষত্রের রাত’ মাকেই উৎসর্গ করেছিলেন মতি। একলা মায়ের সন্তান হওয়ার ছাপ স্পষ্ট তাঁর বহু লেখায়। মা মলিনাবালা বাবা চুণীলালের দ্বিতীয় পক্ষ। ১৯৩১-এ জন্ম মতিলালের। ষাটোর্ধ্ব পিতার শেষ সন্তান। ১৭ মাস বয়সে পিতৃহারা। মতি লিখেছেন, কোনও ওজনদার অভিভাবক বিনা ছাড়া গরুর মতো বড় হওয়ার কথা। তবে ডাক্তার বাবার সঞ্চয়ের টাকাতেই সংসার চলত। ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো বাবার সার্টিফিকেটে পঞ্চম জর্জের সই নিয়ে মায়ের কত গর্ব! অনেক পরে মতি বোঝেন, সই নয় ওটা শিলমোহর। মায়ের প্রতি মায়ায় মনটা ভরে উঠেছিল। প্রায় ৬০ বছরের বৈধব্য কাটিয়ে মলিনাবালা মারা যান।
মতির ‘রাস্তা’ গল্পটিতে খর মধ্যাহ্নের তপ্ত পিচ মাড়িয়ে মা ও ছেলের হাসপাতাল থেকে ফেরার কথা আছে। ছেলেটির কোলে, সদ্যোজাত ভাই। বাবার আসার কথা! কিন্তু আসেননি। এই উপস্থিত বা অনুপস্থিত বাবার সঙ্গে অদ্ভুত টানাপড়েন আরও বহু লেখায়, ‘দ্বাদশব্যক্তি’ থেকে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত ‘সাদা খামে’। বড় গল্প ‘বুড়ো লোকটি’র সম্পন্ন বাবা অসফল পুত্রকে অষ্টপ্রহর খোঁচা দেন। বিখ্যাত গল্প ‘শবাগার’-এ বাবার ব্যাভিচার দেখে ফেলে যুবক পুত্র। তবু কিছু মায়া থেকে যায়। ‘স্টপার’ কমল ও তাঁর সদ্য তরুণ পুত্রের সম্পর্কটা মতি লেখেন, ‘স্কুলে ভর্তি হওয়া নতুন দু’টি ছেলের মতো’!
লেখক হওয়ার গল্প
“আমার দেখা মতি ছিল ক্রিকেট নিয়ে তদ্গত! শ্যামপার্কে ক্লাব তৈরি করে আমরা তখন মণীন্দ্র কলেজের ক্রিকেট কিট দখল করে খেলছি! ও কোনও দিন সাহিত্যিক হবে, ভাবিইনি”, বলছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বয়সে সামান্য ছোট, পাড়ায় গন্যিমান্যি রুদ্রর ‘কোটা’তেই একটু বেশি বয়সে মণীন্দ্রয় বাংলা অনার্সে ভর্তি হন মতি।
তার আগে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করে বেলঘরিয়া ডিপোর চাকরি পেয়েও কম মাইনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। ময়দানে দ্বিতীয় ডিভিশনে ক্রিকেট খেলেন। এবং প্রধানত দুই কবি বন্ধু শিবশম্ভু পাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়দের আড্ডায় নিজের গল্প পড়েন। সম্ভবত এই আসরেই ‘ছাদ’ গল্পটি শুনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল, মতি তো আমাদের সবার চেয়ে ভাল লেখেন। ১৯৫৬’র ডিসেম্বরে তা ‘দেশ’ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত গল্প। তখনই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় মতির জীবনের মোড় ঘুরে গেল। শুনলেন ‘উল্টোরথ’ পত্রিকার মানিক স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতার কথা। যার বিচারক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদারেরা।
১৫০টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। তিন নম্বরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রীকে ছাপিয়ে মতিই প্রথম। জ্যোতি বসু, অশোককুমার সরকারের উপস্থিতিতে ৫০০ টাকা পুরস্কার ও সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। মতি বলেছেন, এ স্বীকৃতি তাঁকে লেখক হতে সাহস জুগিয়েছে। তবে বিজয়ীর নাম শ্রী মতি নন্দী দেখে অনেকেই ভাবেন, তিনি ভদ্রমহিলা।
মাঠ ময়দানে
পরের দশ বছর অবশ্য উপন্যাসে হাত দেওয়ার ফুরসতই পাননি। বিয়ে করেছেন, বাবা হয়েছেন। সুন্দরবনের হদ্দ গাঁয়ে মাস্টারি করতে গিয়েছিলেন। নিজে গিয়ে তাঁকে কলকাতায় ধরে আনলেন আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ। গল্প পড়ে জহুরির চোখে এই মোতিটিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। সন্তোষকুমারের নির্দেশেই মতির ক্রীড়াসাংবাদিকতার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। গ্রিফিথের বল নরি কন্ট্রাক্টরের মাথায় লাগল কেন বুঝতে পঙ্কজ রায়ের খুঁটিয়ে সাক্ষাৎকার নিলেন। আনন্দবাজারে সপ্তাহে সপ্তাহে বেরোত ‘মাঠ ময়দান’! গোটা পাতার জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ ‘কেয়ার অব মতি’। পেতেন অপরিসীম মূল্যের ৫০টি টাকা। এর জন্য নিয়মিত ব্রিটিশ কাউন্সিল অভিযান। খান পাঁচ-ছয় দেশিবিদেশি পত্রপত্রিকা কিনে আগাপাছতলা পড়া। বিদেশি সংবাদপত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগ। আর ক্রীড়া সাংবাদিকতার এক নতুন ভাষারও জন্ম। মতির পাতাতেই পেলেকে চিনেছে বাঙালি। আবার সাঁতার, দাবা, কবাডিও গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৬৯-এ আনন্দবাজারে পাকা চাকরির পরে ক্রীড়া সম্পাদক হন মতি। দায়িত্ব সামলান দেড় দশক। শীতগুলো সাধারণত টেস্ট কভারেজে ভারত ভ্রমণে কাটত।
সে যুগের ক্রিকেট, ফুটবলের সেরা ম্যাচগুলোর ফুটেজ নেই। কিন্তু মতির রিপোর্টের হিরে-মোতি পেলে এখনও ফেসবুকে হামলে পড়ে খেলাপাগলেরা। আটাত্তরের পুজোয় শ্যাম থাপার বাইসাইকেল কিক আলোয় দেখেছিল কলকাতা। তার চেয়েও উজ্জ্বলতর মতির বর্ণনা, ‘জোয়ারের টানে সাগরের ঢেউ যেভাবে পাকিয়ে ফুঁসে ওঠে এবং ঢেউয়ের মাথায় ঝকমকিয়ে জ্বলে ওঠে হিরের দ্যুতি, সেইভাবে ফুলে উঠলো মেরুন-সবুজ একটা ঢেউ… আর তার মাথার উপরে ঠিকরে উঠল একটা পা’!
মজার ব্যাপার, মতির বড় মেয়ে আনন্দরূপা বলেন, “আমাদের দুঃখ ছিল, ম্যাচ রিপোর্টে পক্ষপাতিত্ব আসার ভয়ে কোনও প্লেয়ারকে বাড়িতে ডাকত না বাপি! শুধু একটি বার সুভাষ ভৌমিক, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদারকে নেমন্তন্ন করেন।” ঋদ্ধিমান সাহা ও জনৈক সাংবাদিককে ঘিরে বিতর্কের যুগে অবশ্য তামাদি হয়ে গিয়েছে এমন চিন্তাভাবনা। খেলার চেয়ে খেলোয়াড়দের কেচ্ছায় সাংবাদিকতার ঝোঁক নিয়ে মতি লিখেওছেন তাঁর ‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’ উপন্যাসটি (১৯৮৬)। মতির অন্যতম মন্ত্রশিষ্য রূপক সাহা বলেন, “আমি এখনও মানি, টিভি, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনও ম্যাচ ছিবড়ে হয়ে গেলেও পরের সকালে টেক্কা দিতে পারে মতি নন্দীসুলভ ভাষার ম্যাচ রিপোর্ট!” ক্রিকেট লেখক নেভিল কার্ডাসের ভক্ত মতি শেষ জীবনেও একটি সাক্ষাৎকারে সদ্য কার্ডাসের আত্মজীবনী তৃতীয় বার পড়ার কথা বলছেন।
পাতালের স্বরলিপি
আনন্দবাজারের প্যাডের একটা পাতায় বড়জোর ৮০-৯০টা শব্দ। এক ধারে দীর্ঘ মার্জিন! সেই ফাঁকে আবার কয়েকটি শব্দে জ্যোতির্ময় বর্ণনা। সেটা গোল করে তির এঁকে মূল লেখার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। জয় গোস্বামীর চোখে ভাসে, মতি নন্দীর পাণ্ডুলিপি। সব কিছু যেন দু’বার রিভাইস করে পাঠানো। ব্যস্ত ক্রীড়া সাংবাদিক মতি দফায় দফায় ২৮, ২২ কি ১৫ পাতা করে পুজোর উপন্যাস পাঠাচ্ছেন। দেশ পত্রিকায় চাকরির সময়ে তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলছেন জয়। মতি নন্দীর কোনও কোনও বাক্য ছুরির মতো গেঁথে কোন অচেনা অন্তস্তলে স্পর্শ করে! জয়ের মনে হয়, এ পাতালের স্বরলিপি। ‘একটি পিকনিকের অপমৃত্যু’ গল্প বা উপন্যাস ‘বারান্দা’র সময় থেকে এটাই মতির ঘরানা। খোলামকুচির মতো মানুষ মরে! পিকনিকে শহুরে বান্ধবীরা খেলাচ্ছলেই মেরে ফেলে বোকাটে সঙ্গী শিবনাথকে। তাদের এলোপাথাড়ি ছোড়া ঢিলের মতো মাধ্যাকর্ষণের টানেই যেন শিবু নারকেল গাছ থেকে পড়ে মরে যায়। ‘বারান্দা’-য় কয়লা ভাঙা হাতুড়ির এক ঘায়ে মোহনের ঘিলু প্রকট। জয় বিমূঢ়, ‘কানাইলালের রেহাই’ উপন্যাসে একটি লোক আত্মহননের আগে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে স্বাভাবিক সব কাজ করছেন, এমনকি মৃত্যুলিপিতে দু’একটা বানান নিয়েও চিন্তিত। মতির প্রিয় লেখক, বন্ধু, ভায়রাভাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এটাকেই ‘উন্মোচন’ বলেছেন।
“মতি শক্তিশালী লেখক, কিন্তু ওর লেখায় বীভৎস রসের আমদানি মাঝেমধ্যে কৃত্রিম লাগে,” অভিমত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। ‘শবাগার’-এর শেষে ক্যানসারগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর সামনেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িওয়ালা প্রৌঢ় যৌন সংসর্গ করেন। শীর্ষেন্দু বলেন, “বাস্তবে এ ভাবে ঘটে না!” আবার বাংলা সাহিত্যের সিলেবাসে এই গল্পটি অপরিহার্য বলে তা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ঢুকিয়েছেন অধ্যাপক কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী।
মতির লেখার এই নিষ্ঠুর ভুবনের পিছনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জগদীশ ভট্টাচার্যের আভাস দেখেন অনেকে। ‘শবাগার’, ‘গলিত সুখ’, একটি মহাদেশের জন্য গল্পগুলি কিন্তু চারপাশের হিংসার আবহে অনিবার্য বলেই দাবি করেছেন মতি। বারবার নকশাল আমলের হত্যালীলার কথা পেড়েছেন তিনি। ক্রিকেটের দ্বাদশব্যক্তির গ্লানি, মতির লেখার একটি প্রধান দর্শন। তাদের ভবিতব্য, বেগার ফিল্ডিং খাটা। টিমে ঢুকে নায়ক হওয়া কপালে নেই। নায়ক হওয়ার নেশায় ঝুঁকি নিতে গিয়ে পিকনিকের শিবুর মতো অপমৃত্যুও ঘটে। অসফল দ্বাদশ ব্যক্তিরাই মতির নায়ক। ছোটদের জন্য ইনিই মজাদার কলাবতী-কাহিনি লেখেন! জয় বলেন, “১৯৭৪ ও ’৭৫ দু’বছরে পর পর আনন্দবাজারে ‘বারান্দা’, আনন্দমেলায় ‘কোনি’ কী করে লেখেন মতি! দু’জন কি একটাই মানুষ?”
ননীদা টু নারান
খেলা নিয়ে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসুরাও! “কিন্তু মতিকাকুর লেখাগুলো একেবারে জ্যান্ত অকৃত্রিম”, বলছিলেন মতির প্রিয়জন কৃষ্ণরূপ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্র, এই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। মতি নন্দীর দারুণ ভক্ত রাস্কিন বন্ডও। ‘স্টপার’, ‘স্ট্রাইকার’, ‘কোনি’ তিনিই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করান। মতির কিছু লেখা সারা দেশে স্কুলপাঠ্য। ময়দানি ক্রিকেটে ছোট ক্লাবে বছরের পর বছর ব্যবহৃত প্রাগৈতিহাসিক গ্লাভস, প্যাডের দুর্গন্ধ থেকে ফুটবলে ছোট দলের প্লেয়ার ম্যানেজ, কর্মকর্তাদের খেয়োখেয়ি হাড়ে হাড়ে চিনতেন মতি। আনন্দমেলায় ‘ননীদা নট আউট’ থেকে ‘কোনি’র পর পর সিদ্ধিলাভ তবু সাহিত্যিক মতির জন্যও কম চাপের ছিল না।
তিন মেয়ে আনন্দরূপা, অমৃতরূপা, অনন্তরূপাকে তাঁর ‘কোনি’ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু কোনি পূর্ব জার্মানির কর্নেলিয়া এন্ডারের ডাকনাম। মতি দেখেছেন, বাঙালির ক্রমশ ম্যাড়মেড়ে খেলার জগতে নায়ক কই! ইচ্ছাপূরণের রূপকথা বেশি দূর এগোবে না। আশির দশকে মারাদোনাকে দেখা বাঙালির জ??? ????????, ?ন্য ‘স্টপার’, ‘স্ট্রাইকার’-এর ফর্মুলা ফেরাননি। ‘কোনি’র দু’দশক বাদে তুলসী ট্রায়াথলন রপ্ত করে নিছকই খেলার কোটার চাকরির আশায়। পরিশ্রমী এই মেয়ের দোসর বডিশেমিংয়ের অপমান মুছে থলথলে থেকে ছিপছিপে, প্রবীণ কেরানি বলরাম।
এই ছক-ভাঙা রূপকথার মধ্যে মতির সবচেয়ে প্রিয় লেখা ‘নারান’। আনন্দবাজারের এক পিওন জীবন ঘোষের ধাঁচে নারান হালদারও জীবনযুদ্ধে এক ফোঁটা সময় নষ্ট করেন না। দূরপাল্লার দৌড়ে সর্বকালের সেরা এমিল জ্যাটোপেককে একলব্যের মতো পুজো করেন। নারানের মধ্যে হার না-মানা মনুষ্যত্বের জয়যাত্রা দেখেছেন লীলা মজুমদার। কিন্তু কাগজের কুসংস্কারগ্রস্ত সাব-এডিটর গোঁড়া মোহনবাগানি টোলুবাবুও ‘রোল মডেল’ এ উপন্যাসে। নারানকে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসেন। রাস্তায় খালি পায়ে দৌড়ে সেপটিক ঠেকাতে ডাক্তার দেখান, কেডস কিনে দেন। স্রেফ নিষ্ঠুরতা নয়, নিঃশব্দ কিন্তু তীব্র এমন ভালবাসার ছুরিতেই মতির মলম।

পরিবারের সঙ্গে মতি নন্দী
লেখা এবং লেখক
সন্তোষকুমার ঘোষ দেখেছেন, ধরাধরি মতির স্বভাবে নেই! মতি তাঁর লেখার মতোই খটখটে। ফলে অনেক ডাকসাইটে সম্পাদকের সঙ্গেই দূরত্ব ছিল। দ্রুত আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। তবে বেশি বড় উপন্যাস লেখা হয়নি। একবার আড্ডায় প্রিয় বন্ধু শক্তিকে বলেছিলেন, তুমিই শ্রেষ্ঠ কবি! শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বভাব বহির্ভূত ভাবে একটু ‘না-না’ করেছেন! শুনে মতি খেপে ঘুষিতে তাঁর চশমা ভেঙে দিলেন। ছিয়াত্তরের লিগে ইস্টবেঙ্গলের খেলার প্রশংসা লেখায় মোহনবাগান সমর্থকেরা বাড়ির দরজায় বোমাবাজি করল! মতি পরের দিন একটু ‘খেয়ে’ টেন্টে ধীরেন দে-কে দু’কথা শুনিয়ে এলেন। নীরেন চক্রবর্তী দেখেছেন, এই লোকটাই জড়োয়ার ঝুমকো থেকে মোতি বাছাইয়ের ভঙ্গিতে কচি পটল বাজার করেন। ধম্মোকম্মো, শ্রাদ্ধশান্তি মানেন না। তিনিই পোষা বেড়ালের মৃত্যুতে নির্ঘুম রাত কাটান।
বাপি চুল না-কাটলে মেয়েদের চুল কাটা হবে না! ব্যস্ত বাপিই তিন বোনকে বসিয়ে পড়াবেন। কিন্তু কখনও তাঁদের ব্যক্তিজীবনে খবরদারি করেননি। স্ত্রী নিতির সঙ্গে আলাপ ‘পরিচয়’-এর অফিসে। ভাব করার ইচ্ছে হলে মতি বলেন, “কফি খাওয়াবেন? তা হলে কফিহাউসে যাই!” বেকার দশায় পালিয়ে অসবর্ণ বিবাহ। বন্ধুতাময় দাম্পত্য অটুট থাকলেও তা পরে ঝড়ের মুখে পড়েছে। মতির জীবনে আর এক জন নারী আসেন। নানা সমস্যায় মতির অনমনীয়, ঋজু ব্যক্তিত্বও কিছুটা টাল খেয়েছিল। মেজ মেয়ে অমৃতরূপা বলেন, “জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে! কেউ পারফেক্ট নয়! তবু আমাদের বাপি একজন সত্যিকারের ভাল মানুষ! এমন বাবা ক’জনের হয়!”
কচি ও বিজলিবালা
কংগ্রেস সেবাদলের ভলান্টিয়ার মতি বেলেঘাটায় গান্ধীকে একেবারে কাছ থেকে দেখেন। তাঁর গায়ের গন্ধ পান! কলুটোলায় তখন স্লোগান দিচ্ছেন, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই/ ভুলো মৎ… কিন্তু মতির লেখায় মুসলিম চরিত্র গুটিকয়েক। যা দেখেন না, তা নিয়ে লেখেন না! লেখার নামে লেখার ভানও পারেন না! তবে মতির ‘স্ট্রাইকার’-এর পার্শ্বচরিত্র আনোয়ার প্রতিপক্ষ কিন্তু বন্ধু প্রসূনকে অন্যায় ফাউল থেকে বাঁচায়, গটআপের অপবাদের মোকাবিলা করে মাঠে বুক চিতিয়ে। আর মতির প্রায়ই মনে হয়, দাঙ্গায় আক্রান্ত কচি তাঁকে কী বলতে চেয়েছিল!
বেহুলার ভেলা-তেই মতি দেখেছেন, শোভাবাজার বাজারের মুসলিম বিক্রেতারা কোথায় অদৃশ্য! কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বাড়ছিল বিভাজন। তাঁর শেষ উপন্যাস ‘বিজলিবালার মুক্তি’তে (২০০২) এই ধর্মের দেওয়ালকেই মতির কশাঘাত। বেশ অসুস্থ তখন। লিখলে হাতে ব্যথা হয়! আনন্দ-র বই ‘বিজলিবালা’র প্রচ্ছদ করেছিলেন উত্তর কলকাতার অপূর্ব অন্ধকারের চিত্রকর গণেশ পাইন। উত্তরের গলির অতলস্পর্শী গদ্যশিল্পীর সঙ্গে সেই তাঁর যুগলবন্দি।
কোনির মতো বিজলিবালাও সিনেমা হয়েছে। গৌতম হালদারের পরিচালনায় রাখী বিজলির ভূমিকায়। চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পেলেও কোভিডের জন্যই থমকে এ ছবির মুক্তি। কচির বন্ধু মতি এ লেখায় একটা ‘রিলিফ’ পেয়েছিলেন! ভিনধর্মী ভাড়াটে যুগল, জ্যোতি ও হাসিনাকে দেখে বামুনের বিধবা ধার্মিক বিজলিবালা বোঝেন, ভালবাসলে ধর্মের ভেদ থাকে না! বিজলির এই বোধের কাছেই মুক্তি খুঁজছে ২০২২-এর ভারতবর্ষও।
ঋণ: নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান (মতি নন্দীর সাক্ষাৎকার সংকলন), প্রশান্ত মাজী (সম্পাদক: প্রতিবিম্ব), কল্যাণ মজুমদার, মতি নন্দীর কন্যারা)