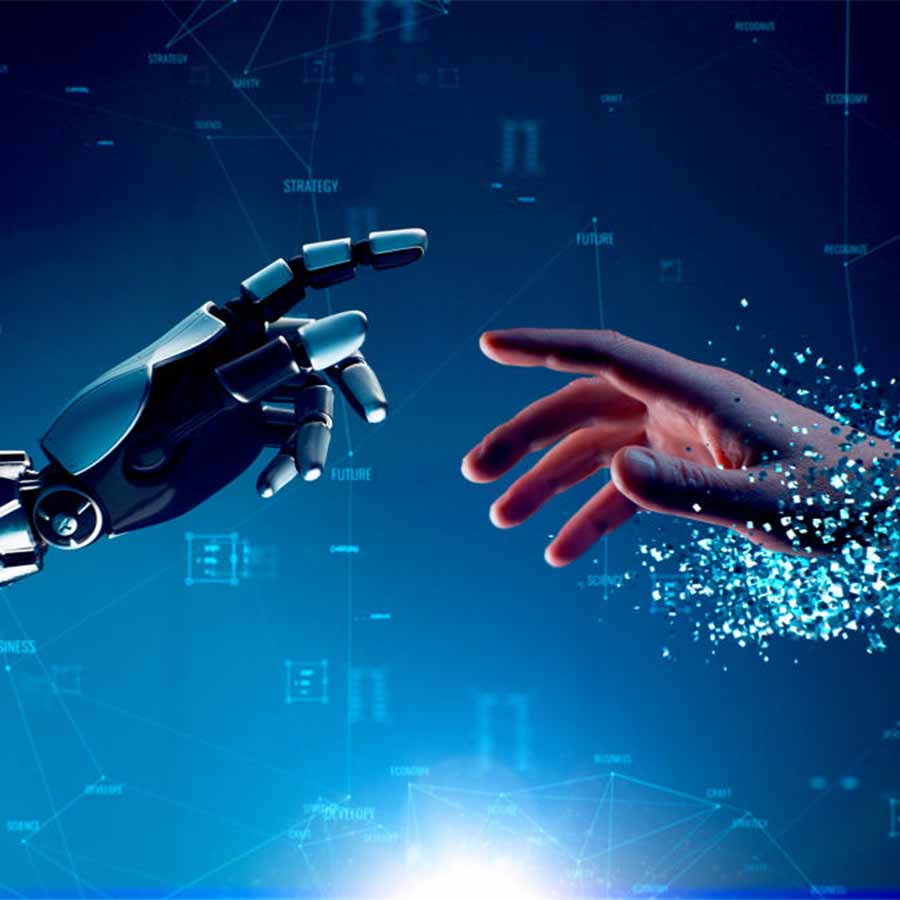বেঙ্গল স্কুলের অবহেলিত নক্ষত্র
এক সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে যেতেন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। ১৯১৬-য় বিচিত্রা ক্লাবে ‘ফাল্গুনী’ নাটকে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন (বাঁ দিকের ছবি)। মণীন্দ্রভূষণ ছিলেন শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলাল বসুর গোড়ার দিকের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথ বেঙ্গল স্কুল শিল্প-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে প্রাচ্য ভাষার কথা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তা পরবর্তীতে লালিত হয়েছিল নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্রদের হাতেই।

পুরাণ কাব্যের আধারে ভারতবর্ষের সামগ্রিক চরিত্রকে খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তখন। সেই যাত্রার অনেক নক্ষত্রই আজ অবহেলিত। এ রকমই এক জন শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ (১৮৯৮-১৯৬৮)। এগারো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। প্রতি বছর মাঘোত্সবের সময় মণীন্দ্র অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যেতেন জোড়াসাঁকোয়। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ তাদের আঁকা ছবি দেখে পরামর্শ ও উত্সাহ দিতেন। ১৯১৬-য় ওরিয়েন্টাল আর্টস কাউন্সিল একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলে সেখানে প্রথম বার মণীন্দ্রভূষণের চারটি ছবি প্রদর্শিত হয়। ঢাকায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কলেজের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ১৯২১-এ মণীন্দ্র কলাভবনে যোগ দেন। সেখানে দ্বিতীয় বর্ষে তিনি হিন্দু পুরাণের ছবি এঁকে প্রথম হন। তিনিই প্রথম স্লেট এনগ্রেভিং শুরু করেন। শ্রীলঙ্কার আনন্দ কলেজের নতুন ফাইন আর্টস বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে ১৯২৫-এ মণীন্দ্রভূষণ শ্রীলঙ্কায় যান। সেখানে সিগিরিয়া (ডান দিকের ছবি) ক্যানডি, অনুরাধাপুর ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি বহু প্রাচীন ফ্রেসকো অনুলিপি করেন ও ভাস্কর্যের ছবি আঁকেন। আকারপ্রকার আর্ট গ্যালারিতে সম্প্রতি শুরু হয়েছে তাঁর ছবির প্রদর্শনী। অপ্রদর্শিত নানা ছবি দেখা যাবে এতে। সেই সঙ্গে থাকছে মণীন্দ্রভূষণের একটি অ্যানাটমি স্টাডির খাতা। পাশ্চাত্য ধারার এমন স্টাডি বেঙ্গল স্কুলে দুর্লভ। থাকছে নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা মণীন্দ্রভূষণের প্রতিকৃতি। তা ছাড়া মণীন্দ্রভূষণের হিমালয় সিরিজের যে সব ছবি দেখে নিকোলাস রোয়েরিখ তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, রয়েছে তারও বেশ কিছু। প্রদর্শনীটির কিউরেটর দেবদত্ত গুপ্ত, এটি চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত (রবিবার বাদে রোজ ২-৭টা)।
লোক-ঐতিহ্য
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির যে মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন, সেখানেই ২১-২২ অক্টোবর বিকেলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্য গমিরা আর গ্রামীণ নাটক খন। প্রায় তিরিশ বছর পর। ১৯৮৬-তে রাজ্য আকাদেমির উদ্যোগে এ ধরনের নাটকের সমারোহ হয়েছিল জোড়াসাঁকোয়, তার পর এই বার। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সাহায্যে দক্ষিণ দিনাজপুরের মোখা শিল্পী গুরু মধুমঙ্গল মালাকার নিয়ে আসছেন তাঁরই তৈরি চণ্ডী মোখা অবলম্বনে গমিরা নাচ। আর উত্তর দিনাজপুরের গুরু গণেশ রবিদাস উপস্থাপন করবেন লোক সাংবাদিকতা এবং লোকনাট্যের অন্যতম প্রাসঙ্গিক আঙ্গিক খন। যে আঙ্গিক অবলম্বনে কলকাতার প্রসেনিয়াম মঞ্চে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছিল মাধব মালঞ্চী কইন্যা। এই দুটি আঙ্গিককে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে উপস্থাপন করতে সাহায্য করেছেন জয়া মিত্র। উদ্বোধনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী। থাকবে কুনোরের পোড়ামাটি শিল্পের প্রদর্শনী।

বিশেষ সংখ্যা
‘আমি চাই শুধুই দূরে চলে যেতে। মার কাছ থেকে, ভাইবোন-ঠাকুরদা-বড়োমার কাছ থেকে, বাবার স্মৃতির কাছ থেকে, ছাইবেড়িয়া গ্রামের নক্ষত্রখচিত অন্ধকার রাত্রিগুলির কাছ থেকে দূরে চলে যেতে।’—এক আশ্চর্য গদ্যে ‘গতজন্মের কথা’ (তিরপূর্ণি-তে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ) লিখেছেন এ কালের বিশিষ্ট কবি কালীকৃষ্ণ গুহ। সে গদ্য ফিরে পড়া যাবে অণুমাত্রিক-এর (সম্পা: দীপকরঞ্জন ভট্টাচার্য) ‘কালীকৃষ্ণ গুহ বিশেষ সংখ্যা’য়। গত বছর সেপ্টেম্বরে কবির সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ সংখ্যা প্রস্তুতির কারণ হিসেবে সম্পাদকীয়’তে জানানো হয়েছে ‘‘গত চারদশক জুড়ে প্রতিটি দিনই তিনি নতুন কোনো কবিতা লিখে চলেছেন নীরবতার সৌন্দর্যে... ‘অণুমাত্রিক’ তাঁর সেই পরিব্রাজন ও অক্ষর-যাত্রাকে এই অবসরে ফিরে দেখবার কথা ভেবেছে।’’ এতে বিশিষ্ট জনের নিবন্ধাদি তাঁর সৃষ্টির নানা দিক চিনিয়ে দেবে পাঠককে। রয়েছে তাঁর আলোকচিত্র, কথোপকথন, চিঠিপত্র, গ্রন্থপঞ্জি, গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও একগুচ্ছ কবিতা।

শতবর্ষে
দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অঞ্চলের কালীপুজো আকার আদল বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতায় চোখে পড়ার মতো। হাজার হাত, ছিন্নমস্তা, রক্ত চামুণ্ডা, চামুণ্ডা, শ্বেত, দশমুণ্ড আরও কত বিচিত্র প্রতিমার দেখা মেলে কালীপুজোর রাতে। এখানকার সব থেকে পুরনো পুজো ‘চেতলা সর্বসাধারণের কালীপুজো: ২৪ পল্লী’র এ বার শতবর্ষ। পরিচালনায় দশমহাবিদ্যা পুজো কমিটি। অমাবস্যায় কালী আর ছট পুজোর আগের রাতে কার্তিক মাসের পঞ্চমী তিথিতে হয় দশমহাবিদ্যার পুজো। পাশাপাশি উদ্যোক্তারা দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও নানা সামাজিক দায়দায়িত্বও পালন করেন।
চারবঙ্গের লোকগান
গ্রামেগঞ্জে ঘুরে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। তিনি আকাশবাণী ও রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের লোকসঙ্গীত শিল্পী। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন। অন্য দিকে লোকসঙ্গীতে জাতীয় স্কলারশিপ পেয়েছেন দেবলীনা সিংহ রায়। রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমিতে এই বছর রাজ্যস্তরে লোকসঙ্গীতে প্রথম হয়েছেন তিনি। দুজনেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকসঙ্গীতে স্নাতকোত্তর করে বর্তমানে গবেষণা করছেন। ২৭ অক্টোবর আব্বাসউদ্দিনের জন্মদিনের প্রাক্কালে ২৬ তারিখ ৪ এলগিন রোডে বৈতানিকের আখড়ায় সন্ধে ছ’টায় ‘চারবঙ্গের লোকগান’ অনুষ্ঠানে এই দুই শিল্পীর গান শোনাবে বাংলা নাটক ডট কম।
অব্যাহত
ষষ্ঠীর দিন শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চাগুলো। নতুন জামা হয়নি। দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল পাড়ার যুবকদের। দু’দিনের মধ্যে চাঁদা উঠেছিল ৩০৭ টাকা। সে দিন সেই টাকা ফেলনা ছিল না। অষ্টমীতে এলাকার দুঃস্থ পরিবারের বাচ্চাদের নতুন জামা কেনা হয়েছিল সেই টাকায়। সেটা ১৯৬৪ সাল। পঞ্চাশ বছর পরও বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগর, তিন নম্বর রেলগেটের বাসিন্দাদের এই প্রয়াস অব্যাহত। সে দিনের উদ্যোগী যুবকদের প্রধান শঙ্কর মুখোপাধ্যায় এখনও এই কাজের প্রধান হোতা। তাঁর চেষ্টাতেই পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণরা মিলে তৈরি করেছেন একটি সংগঠন। মহালয়ার দিন বাসুদেবপুর শিবতলা পল্লীমঙ্গল সমিতির পুজোপ্রাঙ্গণে দুঃস্থ শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জনের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন নতুন পোশাক।
রেপার্টরি
পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি থিয়েটার রেপার্টরি? যেখানে ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম শিখবে, শিখবে কেমন করে নাটকের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, আর এটাই হবে তাদের পেশা। এমন কথা এর আগে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ভাবেনি। ভাবল রবীন্দ্রভারতী। নাটক বিভাগের তত্ত্বাবধানে রেপার্টরির মুখ্য উপদেশক হয়ে এসেছেন স্বয়ং বিভাস চক্রবর্তী। প্রথম প্রযোজনাটি তাঁর হাত দিয়েই হবে। শুধু নির্দিষ্ট মঞ্চেই নয়, এই রেপার্টরি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে দেশের নানা কোণে। যে কোনও পরিসর হয়ে উঠতে পারবে তাদের অভিনয়ের জায়গা। তার বাইরে, শহরে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে থিয়েটারের প্রশিক্ষণ দেওয়াও হবে তাদের কাজ। থিয়েটার কেমন করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তার পরীক্ষায় নামতে চলেছে রবীন্দ্রভারতী। ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেল এই পরিকল্পনার কথা।
দীপাবলি
মরিশাস থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে রিইউনিয়ন দ্বীপ অনেক দিন ধরেই ফ্রান্সের অধীনে। কালক্রমে সেখানে গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি। নানা ধর্মের মিলন ঘটে। তাই সেখানে এখন প্রতি বছর পালিত হয় সারা পৃথিবীর নানা ধর্মের উত্সব। এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের আলোর উত্সব দীপাবলি। এ বারে রিইউনিয়নের দীপাবলি উত্সবে ডাক পেয়েছে কলকাতার দল সহজিয়া। এই দলের পক্ষ থেকে ওখানে পাড়ি জমিয়েছেন গায়ক দেব চৌধুরী, বাপ্পা সেনগুপ্ত এবং বীরভূমের লক্ষ্মণ দাস ও রিনা দাসী। বাংলা তথা ভারতের নানা প্রান্তের লোকসংগীতের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছেন ওঁরা। রিইউনিয়ন ছাড়াও ফ্রান্সের কয়েকটি শহরে আছে গান নিয়ে কর্মশালা ও অনুষ্ঠান।
বাদল-প্রয়াস

বাদল সরকার প্রয়াত হন ২০১১-য়। এখনও তাঁর নাটকগুলি সমাজ ও জীবনের নানা অলিতে-গলিতে বাতিদান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা আলোকিত হচ্ছি। ১৯৬৪-তে লিখেছিলেন ‘কবিকাহিনী’। আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভোটকে কেন্দ্র করে যে রঙ্গ তৈরি হয় তারই একটি রসআখ্যান। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার জানিয়েছেন, ‘হাসি যদি সুস্থ হয়, নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে যদি হাসানো যায়, তবে সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে আমার মনে হয় না।’ ‘কবিকাহিনী’ সে উদ্দেশ্যে স্থির থেকে হিউমার ও স্যাটায়ার-এর ঠোকাঠুকিতে, বিষয়গত কারণেও দর্শকদের কাছে চিরআদৃত। ২১ অক্টোবর মধুসূদন মঞ্চে ও ২৭ অক্টোবর তপন থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬-৩০-য় সন্দর্ভ মঞ্চস্থ করতে চলেছে নাটকটি। নাটকটির সম্পাদনা ও নির্দেশনায় সীমা মুখোপাধ্যায়। মঞ্চনির্মাণ ত্রিগুণাশঙ্কর মান্নার, আবহসংগীত তড়িত্ ভট্টাচার্যের, আলোক পরিকল্পনায় উত্তীয় জানা। ৩৮তম বর্ষে সন্দর্ভ-এর এই প্রয়াস বাদল সরকারের প্রতি শুধুই স্মৃতিতর্পণ নয়, আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টাও।
চলার পথে
‘এই শহরে ছিন্নমূল আগন্তুক হয়ে এলেও এখানেই আমার শেকড়, এখানেই কর্মজীবন, সুখ দুঃখ বিষাদ কিংবা নতুন সৃষ্টির প্রেরণার কেন্দ্রভূমি। আমাদের সমবায় আবাসনে প্রতিদিনের জীবনযাপন তাকে দিয়েছে প্রাণশক্তি।’ লিখেছেন কবি কৃষ্ণ ধর তাঁর গদ্য ‘আমাদের সমবায়িক সংসার’-এ। এ রকম আরও অনেক রচনার সমাহারে বেরিয়েছে চলার পথে একসাথে, সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাসনের (১৯৬৫-২০১৪) পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে। পিছনের প্রচ্ছদে ছবিও রয়েছে ২০১ ও ২৩৮ মানিকতলা মেন রোড-এর দু’টি আবাসনের। দু’টির আবাসিকদের রচনাদি সম্পর্কে সুবর্ণজয়ন্তী উত্সব স্মরণিকা উপসমিতি-র ‘নিবেদনে’ জানানো হয়েছে ‘লেখাগুলি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল লেখকরা যেন তাদের লেখায় পুরনো দিনের স্মৃতির মধ্যে অনাগত ভবিষ্যত্কে দেখতে চেয়েছেন।’ রয়েছে আবাসনের কড়চা, তার মহাফেজখানা থেকে তুলে-আনা লেখা। রয়েছে প্রতিবেশীর কলম-ও। নগরায়ণের একটা চেহারাছবি ফুটে উঠেছে পত্রটিতে।
সুরের টানে
বলিউডের ভিন্ন ভাবনার ছবিতে নিরীক্ষামূলক সঙ্গীত প্রয়োগে হাতযশ এখন অলকানন্দা দাশগুপ্তের। পশ্চিমি ধ্রুপদী সঙ্গীতের নাটকীয়তার সঙ্গে বলিউডি সরস উচ্ছ্বসিত আকস্মিকতায় ভরা সঙ্গীতের এক আশ্চর্য ভারসাম্য তাঁর আবহ আর সুর সৃষ্টিতে। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃত ভারতীয় সিনেমা... মরাঠি ছবি ‘ফন্ড্রি’, হিন্দি ছবি ‘বি এ পাস’, বা আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তের ছবি ‘আসা যাওয়ার মাঝে’।

রবীন্দ্রনাথের ‘সে’ অবলম্বনে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের হিন্দি ছবি, বা তাঁর সাম্প্রতিকতম হিন্দি ছবি ‘আনোয়ার কা আজব কিস্সা’রও সঙ্গীত পরিচালক অলকানন্দা। পেয়েছেন প্রভাত পুরস্কার। ওড়িশি নৃত্যে তালিম নেন ছোটবেলায়, সে ‘প্যাশন’ অটুট রেখেই তুখোড় হয়ে ওঠেন পিয়ানো-য়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক হওয়ার পর ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতে স্নাতক। এই বঙ্গতনয়ার নিবাস এখন মুম্বই। অমিত ত্রিবেদীর সহযোগী হিসেবে বলিউডের ছবি ‘উড়ান’ আর ‘নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা’য় সঙ্গীত পরিচালনায় হাতেখড়ি। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, তথ্যচিত্রেও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। জন্ম কলকাতায়, চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ কন্যা হওয়ায় সাহিত্য-চিত্রকলা-সিনেমার প্রতি আসক্তি নিয়েই বড় হয়ে ওঠা। ‘সৃষ্টিশীল নিরীক্ষাতেই আমার কাজের দিগন্তকে প্রসারিত করব,’ প্রত্যয় তাঁর স্বরে। পুজোর মরসুমে ঘুরে গেলেন শহরে।
শ্রদ্ধার্ঘ্য
ম্যাডানদের থিয়েটারে দেখতে গেলুম শিশিরকুমারের আলমগীর ভূমিকা।’—এই ভাবেই হেমেন্দ্রকুমার রায় শুরু করেছেন তাঁর বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার বইটির (১৩৬১) চতুর্থ অধ্যায়। লিখছেন, আলমগীরের ভূমিকায় ‘শিশিরকুমার এমন অবলীলাক্রমে অভিনয় করেন যে, তাঁর শক্তির বিশালতা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।... অধিকাংশ সময়টাই থাকেন উপবিষ্ট অবস্থায়, অথচ এতখানি সময় দর্শকরা প্রায় শ্বাসরোধ ক’রে মাত্র তাঁর ভাষণের ইন্দ্রজালেই একেবারে অভিভূত হয়ে থাকে এবং তাঁর মুখের কথাগুলিই বারংবার সৃষ্টি করে বিচিত্র নাট্যক্রিয়া। আর কোন বাংলা নাট্যাভিনয়ে শিল্পীর সৃষ্ট এমন দীর্ঘকালব্যাপী কুহকের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করছে সূত্রধর, মলয় রক্ষিতের সম্পাদনায়। ৬ নভেম্বর সন্ধে ৬টায় ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়িতে (৬৭ই বিডন স্ট্রিট)। সম্পাদকের কথায় ‘এ-বই বাজার চলতি আর পাঁচটা বই-এর থেকে স্বভাবে-চরিত্রে অনেকখানিই আলাদা। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর এক আশ্চর্য মানুষ। কলাবিদ্যার নানা দিকেই ছিল তাঁর অনায়াস গতায়াত।’ সূত্রধর-সংস্করণে তাই সম্পাদক শুধু হেমেন্দ্রকুমারের মূল লেখাটিই রেখেছেন, অন্যদের লেখা বাদ দিয়েছেন। তাতেও তিনি প্রথম সংস্করণটিকেই মূল ধরেছেন, কারণ দ্বিতীয় (১৯৮৬) ও নবায়িত (১৯৯১) সংস্করণে মূল গ্রন্থটির ‘অনেক কিছুই নিঃশব্দে বদলে ফেলা হয়েছে...’। বইটি প্রকাশ করবেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ‘বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী’ নিয়ে বলবেন অনিল মুখোপাধ্যায় দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশিরকুমার অভিনীত নাট্যাংশ ও কবিতাপাঠ তাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াসে। ছবিটি পরিমল গোস্বামীর তোলা।