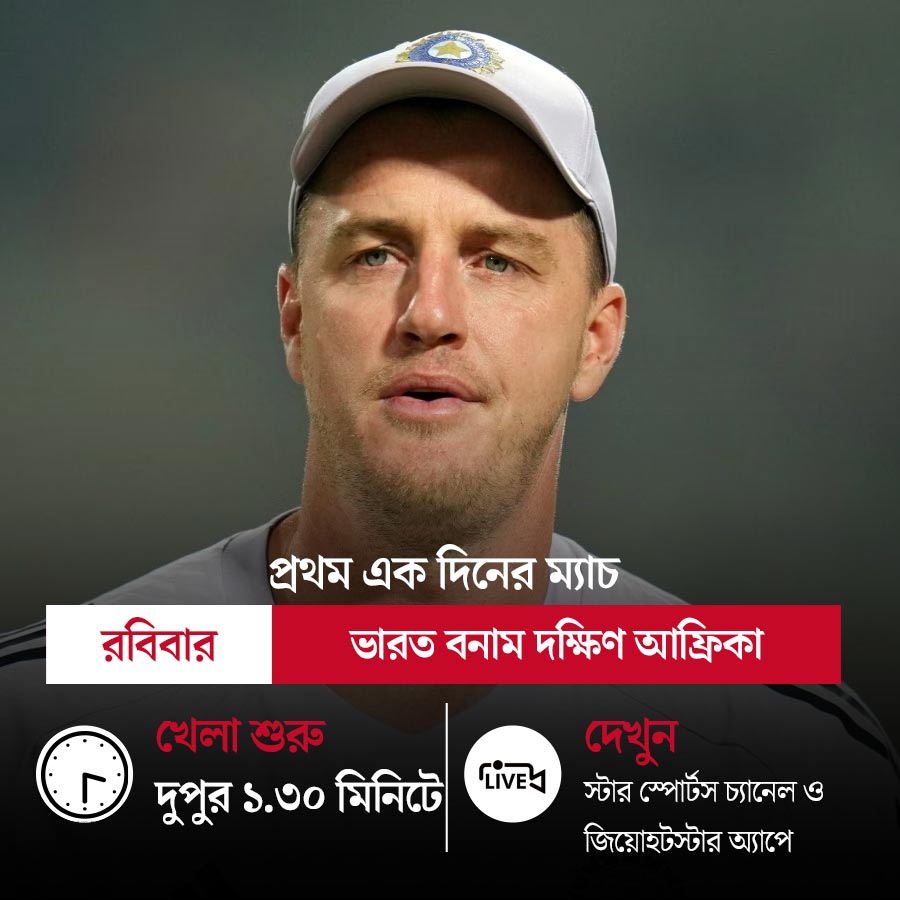অনেকের কাছেই বাঁচার অর্ধেকটাই চা। ভাবগত অর্থে তো বটেই, আক্ষরিক অর্থেও (বাঁ+চা= বাঁচা)। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চিনে গিয়ে চায়ের স্বাদ পেলেও, তাকে বাণিজ্যের চেহারা দিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা স্কটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রবার্ট ফরচুনকে ভার দিল গোপনে চিন থেকে ভারতে চা গাছ নিয়ে আসার জন্যে, যা ক্রমে বিরাট শিল্পের চেহারা নিল। চায়ের উৎস চিন। কিন্তু চায়ের কাপে তুফান শুধু বাঙালিরাই তোলে এবং জগতের মধ্যে তারাই একমাত্র চায়ের নেশায় ‘চাতাল’ হতে পারে। জাপানের চা পান নিয়ে যতই চাপানউতোর চলুক, বস্টন বন্দরে চায়ের পেটি ফেলে যতই আমেরিকান বিপ্লব হোক, জীবনের প্রেম-অপ্রেম, ক্ষোভ-যন্ত্রণা, তুচ্ছতা-অপারগতাকে দু’টি পাতা একটি কুঁড়িতে এমন ফুটিয়ে তুলতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আর তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে।
‘স্বয়ম্বরা’ গল্পে পরশুরাম বলেছেন চায়ের গুণের কথা। চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলিগোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালি তেমন চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় তারিফ করে চা খেতে শেখেননি, সর্দি হলে আদা-নুন দিয়ে খেতেন। তাতেই লিখতে পেরেছেন— বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশে ভাবের বন্যা এসেছে— ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম।
বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে শহুরে ছেলে গ্রামের দিদিমা বা মাসিমার কাছে চা চেয়ে, বদলে পেয়েছে হয়তো বেলের পানা। সেই সময় গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে, চায়ের প্রায় চল ছিল না। কোথাও বা প্রত্যুৎপন্নমতি নারীটি গ্রামের একমাত্র চা-পায়ী বাড়ি থেকে চা পাতা চেয়ে এনে অবাক করে দিয়েছেন। যেমন দিয়েছিল অনঙ্গ-বৌ দীনু ভট্চাজকে অশনি সংকেত-এ। ছেলেকে পাঠিয়ে কাপাসীর মা, শিবু ঘোষের বাড়ি থেকে চা জোগাড় করে বৃদ্ধের সামনে চায়ের গেলাস ধরে হাসি হাসি মুখে বলেছিল, দেখুন তো কেমন হয়েচে? চায়ের পাটাপাটি তেমন তো নেই এ বাড়িতে। ‘উন্নতি’ গল্পে চায়ে গুড়ের অভাব নিয়ে অনুযোগ করায় ছেলেকে শুনতে হয়েছে, ওইটুকু গুড় সারা বছরের পুজো আর রান্নাবান্নার জন্য তোলা আছে, চায়ে দিয়ে বাজে খরচ করা যাবে না। অর্থাৎ, চা পাতা জোগাড় হলেও চিনি, গুড় বা দুধের জোগান কঠিন ছিল।
তাই এই চা-কে বাঙালি জীবনের অসংযম মনে করেছেন জীবনানন্দ দাশ। অনটনের মধ্যেও এর আকর্ষণ বাঙালি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। শুকনো করমচা পাতার গুঁড়োর মতো চা, জলের মতো দুধ আর আখিগুড়ে যা তৈরি হয়।
কোথাও চা চিনি দুধ নিজেদেরই কিনে নিয়ে যেতে হয়, গৃহস্থ শুধু উনুনের আঁচটুকু দেন, তাই সই। সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পে আছে— উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। আমাদের চায়ের জন্যে এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে রেখেই হরিদা ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।
...এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর; আর আমাদের চার জনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।—চায়ের নেশা ধরানোর ছবি মণীন্দ্র গুপ্তর আত্মকথা অক্ষয় মালবেরি-তে। হাটে খানিকটা জায়গা নিয়ে বড় বড় কেরোসিন স্টোভে বিশাল বিশাল হাঁড়িতে চায়ের পাতা, দুধ আর আখের গুড় পাঁচনের মতো জ্বাল দেওয়া হত, হাটে আসা মানুষজনকে ডেকে সেই চা ঘটি ঘটি গেলাস গেলাস বিনিপয়সায় খাওয়ানো হত। সারা দিনই চা সেদ্ধ হচ্ছে— একই লোক কত বার এসে খেল। লোকেরা যত চা খায়, টি বোর্ডের ভদ্রলোকও তত খুশি।
হাটে চা বিক্রি হওয়ার চমৎকার ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মড়িঘাটের মেলা’ গল্পে। তত দিনে নেশা ধরে গেছে। আর বিনিপয়সায় নয়, চা খেতে হচ্ছে কিনে। পাড়াগাঁয়ে চায়ের দোকানে ভিড় বেশি হয়। এখানে যারা এসেছে, এদের মধ্যে চা অনেকেই বাপের জন্মে খায়নি। শৌখিন জিনিস হিসেবে অনেকেই এক পেয়ালা কিনে চেখে দেকচে। সেখানে মা নিজে চা খাচ্ছে, ছেলেকেও প্ররোচিত করছে চা খেতে। অনিচ্ছুক ছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলছে— ...এরে বলে চা— ভারী মিষ্টি— দ্যাখ খেয়ে— ...জ্বর আর হবে না— আ মো লো যা ছেলে। চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি ফেলে দেব কনে? মুই তো দু ভাঁড় খ্যালাম দেখলি নে?
তবে মেয়েদের চা খাওয়ার চল (বলা ভাল অনুমতি) ছিল না অনেক দিন পর্যন্ত। বিলেতি কলের চিনির মতো বিলেতি চা পান মানা ছিল মেয়েদের। মনে পড়ে ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি সিনেমায় রাজলক্ষ্মীর চা পানের সেই দৃশ্য। পরে মেয়েরা চায়ের এই ‘ট্যাবু’ নিজেরাই ভেঙেছেন। আমার দিদা বলেই দিয়েছিলেন চা খেয়ে উপোসে বাধা নেই। কিছু মন্দিরে তো ঠাকুরের বৈকালিক প্রসাদে চা নিবেদন করা হয়। দেহরাদূনের পথে এক ঠান্ডা কনকনে গোধূলিতে প্রকাশেশ্বর শিবমন্দিরের প্রসাদে পুরি-লাড্ডুর সঙ্গে এক গেলাস চা কী যে উত্তাপ দিয়েছিল! অত ঠান্ডায় গরম চা ছাড়া শিবঠাকুরেরও চলে নাকি?
চায়ের আর একটা গুণ আছে, খিদে মেরে দেয়। বুদ্ধদেব বসুর ‘একটি জীবন’ গল্পে পাই, ভোরের আলো ফোটামাত্র ছোট দাওয়ায় এসে বসেন, ভবানী তাঁর সামনে এনে রাখে গরম এক পেয়ালা চা, আর এক মুঠো মুড়ি। এই চা জিনিসটাকে গুরুদাস আবিষ্কার করেছিলেন যুদ্ধের শেষের দিকে— সত্যি এত উদ্যম দেয় আর খিদেটাকেও দমিয়ে রাখে খুব।
তাই বোধ হয় কাগজকুড়ানি মায়েরা কাকভোরে কাজে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের চা খাইয়ে রেখে যান, এই চায়ে মেশানো থাকে আফিম। যাতে বাচ্চারা আর খিদের জ্বালায় না কাঁদে।
সবচেয়ে আগে সব খবর, ঠিক খবর, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদের Google News, Twitter এবং Instagram পেজ।